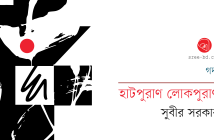বাবা ও আমাদের রবীন্দ্রজয়ন্তী
বৈশাখ এলে ধান-পান আম-কাঁঠাল বাঙ্গি-তরমুজ গরম কালবৈশাখী ইত্যাদি নিয়ে স্বস্তি-অস্বস্তিতে যেমন ভোগে বাঙালি, ঠিক তেমনি ২৫শে বৈশাখ যত এগিয়ে আসে মনটা ‘রবীন্দ্রনাথ’ ‘রবীন্দ্রনাথ’ করে ওঠে। ২৫শে বৈশাখের আগের দু-একদিন তো কথাই নেই। তার ওপর এরশাদ সরকারের কল্যাণে পহেলা বৈশাখের মতো বাংলাদেশে আবার ২৫শে বৈশাখও দুদিন।
রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের ঘটা এখন আর তেমন দেখা যায় না বাহ্যত। কিন্তু সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরলেও প্রকৃত বাঙালির কণ্ঠ এবং হৃদয় কখনো রবীন্দ্রবিমুখ হবে না। সাড়ম্বরে পালিত না হলেও ২৫ বৈশাখ পালিত হয় বাঙালির হৃদয়গৃহে আগের মতো একই তালে, একই ছন্দে একইরকম আনন্দের সাথে।
আমার জীবনে ২৫ বৈশাখ আনন্দমাখা শৈশবস্মৃতি, ২৫ বৈশাখ মানেই আমার বাবার মুখ, বাবার কণ্ঠ।
কেউ না শেখালেও ছোটোবেলা থেকে ঠাকুর-দেবতায় আমার বড়ো আগ্রহ। ইট দিয়ে ঠাকুরঘর বানিয়ে পুজো পুজো খেলাটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। আমার নাস্তিক বাবা একদিন চালনা থেকে সাদা রঙের একটা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি এনে হারমোনিয়ামের ওপর রেখে বললেন, ‘এঁও ঠাকুর। এখন থেকে এই ঠাকুরের পুজোও করবে।’
তখন থেকে রবি ঠাকুর আমারও ঠাকুর।
বাবা যে শুধু রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তা নয়—এটা ছিল তাঁর সাধনা। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-মধ্যরাত—দালানের দরজা বন্ধ করে তিনি গান তুলতেন। সময় অনুযায়ী নানা রাগ-রাগিণীর চর্চা করতেন। আমরা বিরক্ত হতাম। পিসি মাঝে মাঝে রাগ করতেন। পুরো গীতবিতান মুখস্থ ছিল বাবার। এখনকার শিল্পীরা যেমন যেকোনো গান যখন তখন গেয়ে ফেলেন, বাবা কিন্তু তা করতেন না। যে গানটি তাঁর স্বরলিপি দিয়ে তোলা নেই, সে গান কখনো উচ্চারণ করতে তাঁকে শুনিনি। আমি সবাইকে গর্ব করে বলতাম, ‘আমার বাবা দুশো গান জানেন।’ আমি যখন বাংলা নিয়ে পড়া শুরু করলাম, বাবা উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘গীতবিতান তোমাদের পড়ানো হবে?’
বাবা যে শুধু রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তা নয়—এটা ছিল তাঁর সাধনা। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-মধ্যরাত—দালানের দরজা বন্ধ করে তিনি গান তুলতেন। সময় অনুযায়ী নানা রাগ-রাগিণীর চর্চা করতেন। আমরা বিরক্ত হতাম। পিসি মাঝে মাঝে রাগ করতেন। পুরো গীতবিতান মুখস্থ ছিল বাবার।
যখন বাবা গান শেখাতেন, প্রতিটি গানের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতেন। গানের পেছনকার একেকটা গল্প আমাদের আগ্রহী করে তুলত। আমি ওই গল্পগুলো দ্বারাই আকৃষ্ট হতাম।
রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বাবা আমাদেরও কম জ্বালাননি। ঠাকুরদা শিল্পী ছিলেন বলেই আমাদের পরিবারের সবাই কমবেশি গান গাইতে পারেন কিন্তু আমার কোনো আগ্রহ ছিল না সংগীতে। বাবার কাছে পড়াশোনার চেয়ে গানের গুরুত্ব বেশি। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন দিদিকে আর আমাকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতে। কাকাতো দিদিরাও শিখত। কিন্তু হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেই জ্বর আসত আমার। কত মার! কত পরোটা-সন্দেশ খেলাম কিন্তু গান শেখা আমার হলো না।
একবার সিন্ধু বুড়ি দালালকে দিয়ে বাবা কলেজস্ট্রিট থেকে আসল বিশ্বভারতীর অনেকগুলো বই আনালেন। ‘তাসের দেশ’ গীতিনাট্যটি তোলাবেন আমাদের দিয়ে। বারান্দায় দিনরাত মহড়া চলে।’ শেষে দিদি আর আমি পালিয়ে চলে এলাম মামাবাড়ি।
ছোটোবেলায় আমাদের এলাকায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হতো খুব ঘটা করে। বৈশাখের মাঝামাঝি থেকেই নানা আয়োজন। বাবার আমন্ত্রণ আসত অনেক জায়গা থেকে। রবীন্দ্রজয়ন্তী মাঝেই তখন ছিল মানুষের ভরপুর আবেগ। খুব সাজসজ্জা হতো। মৌসুমি ফল দিয়ে আপ্যায়িত হতেন আমন্ত্রিতরা। বাবার সাথে গিয়ে আমিও চেয়ারে বসে তরমুজ, জামরুল খেতাম। বাবার গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে কলাপুরি স্যান্ডেল। হাতের সমস্যাটা তখন সদ্য দেখা দিয়েছিল বলে একটা চাদর ভাজ করে কাঁধে রাখতেন গরমেও। সবাই খাতির করত বাবাকে। অন্য সময়ে মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা থাকলেও এই সময়ে বাবাকে আমার ভীষণ ভালো লাগত।
একবার অনেক সন্দেশ-পরোটা বুন্দিয়া গ্লাসের দই পদ্মগজা (অধীর ময়রার দোকানে এর চেয়ে ভালো খাবার আর ছিল না) খাইয়ে, অনেক গল্প শুনিয়ে, এমনকি প্রহারের ভয় দেখিয়ে বাবা আমাকে দিয়ে ‘আয় তবে সহচরী’ এবং ‘খরবায়ু বয় বেগে’ গান দুটি তোলালেন। পরে শুনি আমি রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান গাইব শিশুশিল্পী হিসেবে। শুধু আমি নই, দিদিও গাইবে। ‘খোলো খোলো দ্বার’ গানটি দিদি ভালোভাবে শিখল। আমি দিদি এবং বাবা তিন জনে মিলে ‘আমরা সবাই রাজা’ গানও গাওয়া হবে। উৎসাহ-উত্তেজনায় আমার চোখে ঘুম নেই। বুকের ভেতর ধুকপুক করছে সব সময়। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি যে এবার গোনাবেলাই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আমি গান গাইব।
সেসময় এই ধরনের অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ থাকত বাবার গান। একটানা চার-পাঁচটি রবীন্দ্রসংগীত বাবা গাইতেন শেষে। সেবার আয়োজক কমিটিকে বাবা বললেন প্রথমেই যেন আমাদের দুই বোনকে গান গাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। দিদি প্রথমে গাইবে, তারপর আমি। কমিটি সানন্দে রাজি। আমাদের নতুন জামা-জুতো এলো। কয়েক দিন ধরে হারমোনিয়াম বাজানোর প্রাকটিস ভালোমতো হলো। আমি ব্লো টানতে পারি না। বাবা টেনে দেবেন কিন্তু আমি বাজিয়ে গাইব। তখন ছোটো বাচ্চাদের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে পারাটা খুব গর্বের বিষয় ছিল।
সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান। আমরা সেজেগুজে রওনা হলাম হেঁটে। তিন কিলোমিটার রাস্তা। ওই গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার। তার ওপর দুপুরে খাইনি ভাত। সেদিন শুক্রবার। আলিফ লায়লা হতো। মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে, আলিফ লায়লা দেখা হবে না বলে। সন্ধ্যাপিসি তো চাঁদা তুলে ব্যাটারি চার্জ দিয়ে এনেছেন বুধবারেই।
গোনাবেলাইতে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। কী চমৎকার করে সাজিয়েছে! আমার মামাবাড়ির আশপাশ থেকেও লোকজন এসেছে। আমাদের খুব খাতির করা হলো। তরমুজ, বাঙ্গি, আম, লিচু। দুবোন চেয়ারে বসে আছি। বাবা ঘুরছেন ফিরছেন আর আমাদের কাছে এসে খোঁজ নিচ্ছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হচ্ছে। বাবা ঘন ঘন চা খাচ্ছেন আর আমাদের এসে বলে যাচ্ছেন, ‘এই তো এক্ষুনি শুরু হবে। তুমি প্রথমে গাইবে। ভুল হয় না যেন।’
আমার বয়স তখন ছয় কিংবা সাত। প্রথম মঞ্চে গাইব। গলা শুকিয়ে আসছে।
অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে আমাকে ডাকার কথা। কিন্তু একজন এসে খুব ভয়ে ভয়ে বাবাকে বললেন, ‘খুলনা থেকে একজন অতিথি এসেছেন। ফিরে যাবেন। তাকে আগে গাইতে দিলে ভালো হয়। ওনার পরেই আপনার মেয়েরা গাইবে।’
বাবা হুংকার দিয়ে উঠলেন। দিদি তো ভয়ে কেঁদেই ফেলল। বাবা বললেন, ‘মেয়েদের রাত পর্যন্ত বসিয়ে রেখে এখন অতিথি দিয়ে গাওয়াবা? গাওয়াও। আমিও গাইব না আজ।’
বলেই আমাদের নিয়ে হাঁটা। অনুষ্ঠান পণ্ডপ্রায় কারণ বাবা না থাকলে তখন রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান পূর্ণ হতো না।’
কমিটির লোক এসে হাত-পা ধরতে লাগলেন, ‘অমলদা, তুমি না থাকলে সব পণ্ড। তোমার মেয়েরা আগে গাইবে। রাগ করো না… ইত্যাদি ইত্যাদি।
বাবা তো ন য়ে কারে ‘না’। গাইলেনই না গান। বাবাকে রাগানোর পরিণতি ভেবে কেউ কেউ একটু ভীত হয়ে উঠল।
আমরা ফিরে আসছি। বেশ রাত হয়েছে। খুব ক্লান্ত। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চকগোনার সাঁকো পার হব কেমনে তাই ভাবছি। সর্দার বাড়ির কাছে এসে শুনি শব্দ ভেসে আসছে ‘আলিফ লায়লা… আলিফ লায়লা… আলিফ লায়ায়ায়লা…’
আমি বলে উঠলাম, ‘আরেকটু জোরে চল দিদি। তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে একটুখানি দেখতে পাব।’
রাগ-দুঃখ খিদে-তেষ্টা সব ভুলে গেলাম। বাবার রাগে রক্ত মুখচোখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পদক্ষেপ শুধু দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। আলিফ লায়লার একটা পর্ব অন্তত দেখতে হবে…
‘আমরা সবাই রাজা’ গানটি বাবার সাথে আমরা গেয়েছিলাম আরও অনেক পরে। চকগোনার কোনো একটা অনুষ্ঠানে।
হারাওনি তো তবু
আমার জীবনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী মানুষটির নাম গৌরপদ মণ্ডল—আমার প্রিয় গৌরদাদু। গৌরদাদুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছে বহুদিন পূর্বে, কিন্তু আমার উপলব্ধিতে এখনো তিনি সজীব। এখনো আমি যখন শৈশবে ফিরি, গৌরদাদুর পিছে পিছে ইছামতী আর পশুরের তীর ধরে হাঁটি। পাকা ওড়া আর কেওড়া ফলের গন্ধে মাতাল হয় মন। দাদু আমায় এখনো ঠিক তেমনি কণ্ঠে বলেন, ‘বৈঠা ছাইড়ে দিলি কিন্তু আমরা আর কূলি যাতি পারব না। বৈঠা যেন না খসে।’
শৈশবে দেখতাম বাড়ির সকলে, গ্রামের সকলে এমনকি এলাকার মানুষও বাবাকে ভয় এবং সমীহ করতেন। কিন্তু বাবা শ্রদ্ধা করতেন গৌরদাদুকে। গৌরদাদুরা আমাদের রায়ত বলে জীবনভর আমাদেরই অনুগত। কিন্তু আমাদের প্রতি গৌরদাদুর স্নেহ আনুগত্য থেকে নয়—কোথা থেকে যে এসেছিল সেই স্নেহ, পরকে আপন করার অমন সর্বগ্রাসী শক্তি, আমি আজও তার কূলকিনারা পাই না। ঠাকুমা প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় শুয়ে কান পেতে থাকতেন, কখন আমি কেঁদে উঠি তাই শোনার জন্য। কাঁদলেই সন্ধ্যা পিসি অথবা দাদু ছুটে আসতেন। আমাদের বাড়ির পূর্বপাশে হওয়ায় দাদুদের বাড়িকে আমরা বলতাম ‘পুবের বাড়ি’। এই পুবের বাড়ি এবং সেই বাড়ির তিন জন মানুষ আমার শৈশবকে মধুময় করে রেখেছিলেন।…
তাঁর গল্পগুলো শুনেছিলাম বলেই আমি এখনো কিছু কল্পনা করতে পারি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, মলন ঘোরাতে ঘোরাতে, জাল বুনতে বুনতে, টিপটিপ বর্ষায় কিংবা রাতের অন্ধকারে তিনি আমার মনের হাত ধরে যে রহস্যের জগতে নিয়ে যেতেন, সে জগতের মূল্য বড়ো হয়ে বুঝেছি। কত গল্প যে তাঁর ঝুলিতে ছিল! একেকটি গল্প দশবার করে শুনতাম। কখনো দেখিনি তাঁকে বিরক্ত হতে।
গৌরদাদু! আমার গৌরদাদু! আমার পুরো শৈশবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর গল্পগুলো শুনেছিলাম বলেই আমি এখনো কিছু কল্পনা করতে পারি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, মলন ঘোরাতে ঘোরাতে, জাল বুনতে বুনতে, টিপটিপ বর্ষায় কিংবা রাতের অন্ধকারে তিনি আমার মনের হাত ধরে যে রহস্যের জগতে নিয়ে যেতেন, সে জগতের মূল্য বড়ো হয়ে বুঝেছি। কত গল্প যে তাঁর ঝুলিতে ছিল! একেকটি গল্প দশবার করে শুনতাম। কখনো দেখিনি তাঁকে বিরক্ত হতে। বাবা চাইতেন ছোটোবেলায় আমি বৃদ্ধ মানুষের সাথে মিশি যাতে আমার মনে কলুষতা প্রবেশ না করে আর বড়ো হয়ে শিশুদের সাথে মিশি যাতে আমার পোক্ত মন ওদের মনের পবিত্রতার ছোঁয়া পায়। আর কিছু না পারলেও বাবার এই চাওয়া আমি পূরণ করেছি।
দাদু নদীতে মাছ ধরতে গেলে আমি লুকিয়ে গিয়ে থলেটা ধরে রাখতাম। ইছামতীতে কত দিন স্নান করেছি! চকগোনায় নতুন হাট বসলে আমি দাদুর সাথে হাটে যেতাম। দাদু খেজুর গাছ কাটতেন আর আমরা চুমরির জন্য তাঁর পিছে পিছে ঘুরতাম। দাদু কয়েকটা চুমরি আমার জন্য আলাদা করে রাখতেন। দাদু যে আমার নিজের দাদু নয়, এটা বুঝেছি অনেক পরে। এমনকি একদিন দাদু তাঁর নাতিকে কোলে নিয়ে বসলে আমার দিদি তাকে হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়েছিল দাদুর কোলে।
দাদুর স্নেহ আমি কোনো দিন ভুলব না, দাদুর স্মৃতিও না। আমি যখনই কিছু লিখতে যাই, সেখানে হুড়মুড় করে প্রবেশ করেন গৌরদাদু। আমার প্রথম উপন্যাস ‘ময়নাঢিপির কথকতা’র হরনাথ বাড়ুই গৌরদাদু ছাড়া আর কেউ নয়। দাদু আমার এত প্রিয় ছিলেন যে, আমি তাঁকে অনুকরণ করতাম। দাদু পায়ে নাগরা জুতো দেন বলে বাবাকে নাগরা জুতো কিনতে হয়েছিল আমার জন্যও।
গোয়ালঘরে দেওয়াল থেকে মাছরাঙা পাখির বাচ্চা বের করতে গিয়ে একবার আমার পায়ে পেরেক বেঁধে। পেকেটেকে ভয়ংকর অবস্থা। মা ছিলেন না তখন। দাদুই আমায় কোলে নিয়ে ঘুরতেন।
সহস্র স্মৃতির মধ্যে দুএকটি খুব স্পষ্ট ছবির মতো ভাসে।
…বিশাল এক মালবাহী কার্গো আমাদের ইছামতীর মোহনায় ডুবে গেছে। লোকজন ইচ্ছেমতো স্রোতে ভাসা জিনিসপত্র তুলে নদীর তীরে শুকাচ্ছে। গৌরদাদু কার কাছ থেকে দুটো কমলা নিয়ে ছুটছেন আমার দিকে। তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।…
…ইছামতীতে রাস উপলক্ষ্যে নৌকা বাইচ। শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় জমিয়েছে নদীর তীরে। আমি নৌকা দেখতে পাচ্ছি না। দাদু দৌড়ে এসে আমায় কাঁধে তুলে নিলেন। ‘ওই তো দীন মোহম্মদের নৌকো আসতিছে। দেখতি পাচ্ছ? মাথাডা আরেকটু সোজা রাখো…’
…দাদু আমায় যেসব গল্প বলতেন, তার মধ্যে ভূত আর বাঁদার গল্প বেশি। আমাদের বিদ্যার বাহনের দেওয়ান ভিটেয় থাকত তখনকার নামজাদা সব ভূত। ভূত চতুর্দশীতে সেখানে ভূতের ভোগ হতো। দাদুর মুখে সেসব শুনে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম ভূত চতুর্দশীর জন্য। কার্তিক মাস এলো। ঠিলার ভেতর একটা শোলমাছও জিইয়ে রেখেছি ভূতের জন্য নিয়ে যাব বলে। তারপর দাদুর কাছে বায়না। ভূতের ভিটেয় আমাকে নিতেই হবে। যেভাবে হোক আমি যাব। দাদু বললেন, বাবা পিটিয়ে চামড়া তুলবেন। আমি নাছোড়বান্দা। বাবাকেও বললাম। বাবা অরাজি নন। দাদুর সাথে কয়েক দিন ধরে চলল পরিকল্পনা। তারপর এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। সন্ধ্যা থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আমি দাদুদের বাড়ি বসে আছি। পিসি গালাগালি করছেন। আমি দাদুর সাথে যাচ্ছি দেওয়ান ভিটেয়। বড়ো গাঙের পাশ দিয়ে যাব। রাঙামার বাড়ির সামনে গেলেই কয়েকটি কুকুর ডেকে উঠল। আমি ভয়ে দাদুর হাত আঁকড়ে ধরলাম। দাদু বললেন, ‘চলো তাড়াতাড়ি।’ আমি বললাম, ‘যাব না। গেলে ছুটদি সমস্ত চৌদ্দশাক খেয়ে নেবে।’ বাবা আমাকে অবশ্য মারধর করেননি। আমি যে ওই বয়সে দেওয়ান ভিটেয় যাওয়ার সাহস দেখিয়েছি। তাতেই বাবা খুশি।…
…বৈশাখে ইছামতীর জল শুকিয়ে এলে আমরা নদীতে নামতাম। একবার দাদুর সাথে নদীতে নামলাম। মাঝনদীতে আমারই কোমরজল। লাবনীরাও ছিল। আমি বারবার জলে ডুব দিচ্ছি। দাদু জাল নিয়ে এগিয়ে গেছেন। শুনি ওদিক থেকে সবাই চেঁচাচ্ছে। দাদুর জালে কচ্ছপ পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি এগোচ্ছি। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দাদু জাল টেনে তুলছেন সন্তর্পণে। কচ্ছপটা কত বড়ো হবে, কে কাটবে ইত্যাদি নিয়ে কথা হচ্ছে। জাল টেনে তোলা হলো। দেখি কচ্ছপের বদলে একখানা সিন্দুর কাঠের মুড়ো। দাদুকে অমন আশাহত হতে আমি আর দেখিনি কখনো।…
…আমাদের গ্রামে খাবার জলের কল ছিল না। চকগোনা থেকে জল আনা হতো। দাদুরা দীন মোহম্মদ জেলের নৌকা নিয়ে মাঝে মাঝে জল আনতে যেতেন। একবার আমিও গেলাম। ফেরার পথে বায়না ধরলাম আমি বৈঠা বাইবো। দাদু শেষমেশ আমার ছোট্ট হাতে বৈঠা ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন। বললেন, ‘দীন মোহম্মদের মুখ ভালো না। বৈঠা হারালে যা না তাই বলবে। ছেড়ে দিয়ো না কিন্তু।’ আমি একটু পরেই বৈঠা ছেড়ে দিলাম। দাদু হতাশ হয়ে বসে বসে বৈঠা ভেসে যাওয়া দেখলেন। দীন মোহম্মদ হয়তো দাদুকে বকেছিলেন কিন্তু আমরা কীভাবে বাড়ি পৌঁছেছিলাম তা স্মৃতিতে নেই।…
…আমাদের ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের সমস্ত পূর্বগৌরবের কথা, পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্য, বদান্যতা এবং ঠাকুরদাদের অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডের গল্প দাদু আমাকে শোনাতেন।’ শোনাতেন ফসলের ইতিবৃত্ত। বংশগৌরবে চোখমুখ আমার উজ্জ্বল হয়ে উঠত। দাদুর কারণেই আমি নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করেছিলাম।…
…দাদুকে নিয়ে কত কথা যে বলা যায়! কত স্মৃতি যে এখনো জাগরূক আছে, আমি যে তাকে কতখানি ধারণ করি, তা কেবল আমিই বুঝি। ছোটোবেলায় দাদুর সাহচর্য পেয়েছিলাম বলেই আজও আমি সবার এমন কাছাকাছি যেতে পারি। আজও কেউ কেউ আমায় মাটির মানুষ বলেন, সেই মাটি দাদু তাঁর স্নেহরসে ভিজিয়ে দিয়ে গেছেন বলে আজও আমি কঠিন আর অহংকারী হতে পারিনি।…
…আমি পড়াশোনার জন্য মামাবাড়িতে চলে আসার পর দাদু মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আসতেন। সাদা পাঞ্জাবি পরা কাউকে বাড়ির ভেতর আসতে দেখলে আমি আনন্দে নাচতে শুরু করতাম। বাড়ি এসে সবচেয়ে আগে ছুটে যেতাম তাঁর কাছে।… বড়ো কষ্ট পেয়েছেন দাদু জীবনে। সন্ধ্যা পিসির বিয়ে সময়মতো দিতে না পারার যন্ত্রণায় তিনি সব সময় পীড়িত হতেন। ঠাকুমা বিছানায় ভুগে মারা গেলেন। ছেলে-ছেলেবউ ভালো ব্যবহার করত না। দাদু একসময় ভারতে চলে গেলেন ছোটো ছেলের কাছে। আমি জানতাম না তাঁর চলে যাওয়ার কথা। শুনেছি আমায় দেখতে চেয়েছিলেন যাওয়ার আগে।… তারপর একদিন সংবাদ পেলাম দাদু আর নেই। ওদেশেও অযত্ন পেয়েছেন। ইলেকট্রিক চুল্লিতে মুহূর্তের মধ্যে দাদুর পাঞ্চভৌতিক দেহ কীভাবে ভস্মীভূত হয়েছিল সেকথা আমি পিসির মুখে শুনেছিলাম। অথচ আমার মতো দাদুও চেয়েছিলেন তাঁর দেহ ইছামতীর তীরে পলিমাটিতে মিশুক।…
দাদু নেই, কিন্তু দাদুর উত্তরাধিকার আমি বহন করছি মননে, মস্তিষ্কে। যদি আরও কিছু কথা আমার কলম দিয়ে বের হয় সেখানেও গৌরদাদুর প্রভাব জ্বলন্ত হয়ে থাকবে। আমি চলে যাব কিন্তু আমার গল্পে থেকে যাবেন গৌরদাদু। কারণ মৈদাড়া গ্রামের অখ্যাত দুঃখী গৌরপদ মণ্ডলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমি।…
…আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কাছের মানুষ সুচিন্তক ও সুলেখক সাইফুল ইসলাম ভাইয়া সম্প্রতি একটা বই লিখেছেন ‘কৃতজ্ঞতার মহাবয়ান’ নামে, যেখানে তিনি মা-বাবা, ঈশ্বরসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ডিম, মুরগি, মাছও তাঁর কৃতজ্ঞতা পেয়েছে। আমি তাঁর লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি। ভাবলাম আমারও তো অনেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আছে। দাদুর কথা লিখতেও বসেছি সর্বপ্রথম। কিন্তু যে মানুষটা আমার অস্তিত্বে মিশে আছে, তাঁর প্রতি কী কৃতজ্ঞতা জানাব? আমি শুধু দাদুকে উপলব্ধি করি আর মনে মনে বলি, ইলেকট্রিক চুল্লি তোমার দেহ ভস্মীভূত করেছে দাদু, কিন্তু তুমি তো কোনো দিনও হারাবে না। তুমি বেঁচে থাকবে। তোমার দেহ হারিয়েছে কিন্তু তুমি হারাওনি। হারাবেও না কখনো। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তোমার কণ্ঠ আমায় প্রেরণা দেবে—‘বৈঠা ছেড়ো না। তাহলে আমরা কূলে পৌঁছাতে পারব না।’
বৈঠা আমি ছাড়িনি দাদু। তুমি তো দেখছ, এত ঝড়ের মাঝেও আমি কেমন করে বৈঠা ধরে আছি।
দিদিমার হাত
শৈশবে একবার সুন্দরবনের কাছে জয়মনি গ্রামে গিয়েছিলাম দাদু-দিদিমার সাথে। অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ। দাদু পৌরোহিত্য করবেন। সাথে দাদুর কয়েকজন শিষ্য।
আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো যজ্ঞস্থলের পাশেই এক বাড়ি। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া মেটে মেঝের ঘর, কাঠের বেশ মজবুত বেড়া। শোনা গেল জয়মনি গ্রামে নাকি প্রায়ই রাতে বাঘ আসে নদী পার হয়ে। কয়েক দিন আগে এক গৃহস্থের গরু নিয়ে গেছে। দিদিমা তো ভয়ে জড়সড়। কেন আমায় নিয়ে আসলেন—এই বোকামির জন্য আফসোস করতে লাগলেন।
মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আমি দেখি দিদিমা তাঁর দুই হাত অদ্ভুতভাবে আমার মাথার ওপরে রেখে শুয়ে আছেন এবং এর জন্য তাঁর ভীষণ কষ্টও হচ্ছে। আমি বললাম, ‘ওভাবে হাত রেখেছ কেন?’ দিদিমা বললেন, ‘বাঘ যদি আসে তাহলে আগে আমার হাতের ওপর দিয়ে যাবে।
রাতে আমাদের ঘুমোতে দিলো বারান্দায়। বাড়িভর্তি আরও অনেক লোক। গরমকাল বলে উঠোনেও মশারি পড়েছে। আমাকে ভেতরপাশে দিয়ে দিদিমা বাইরের পাশে শুয়ে পড়লেন। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আমি দেখি দিদিমা তাঁর দুই হাত অদ্ভুতভাবে আমার মাথার ওপরে রেখে শুয়ে আছেন এবং এর জন্য তাঁর ভীষণ কষ্টও হচ্ছে। আমি বললাম, ‘ওভাবে হাত রেখেছ কেন?’ দিদিমা বললেন, ‘বাঘ যদি আসে তাহলে আগে আমার হাতের ওপর দিয়ে যাবে। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।’ আমি বিষয়টা সত্যি ভেবে নিলাম। পরে বাড়ি এলে এটা শুনে সবাই হাসাহাসি করল। ছোটো মামা আর মা তো দিদিমাকে নিয়ে টিটকারি শুরু করলেন, ‘মা নাকি হাত দিয়ে বাঘের থাবা আটকাবে!’
দিদিমা নীরবে সেই ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করতেন।…
পরে বুঝেছিলাম তাঁর সেই দুটি দুর্বল হাতের মহিমা, বুঝেছিলাম কীভাবে ওই হাতদুটি আমায় জগতের সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে এসেছে।… এখনো বুঝি। হাতদুটি আজ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু আমি এখনো সেই শীর্ণ, শাঁখা-পলা পরা হাতদুটিকে দেখছি আমার মাথার ওপর বরাভয় মুদ্রা নিয়ে দুলছে।
‘ভয় কী দাদা! আমি আছি।’
পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে আপন নেই কে বলে এমন কথা?
বাবা ও মৌচাক
আমাদের বাড়িতে মৌমাছিতে চাক বাঁধত যেখানে সেখানে। তেঁতুলগাছে, আতার ডালে, জামের ডালে। তবে সবচেয়ে বেশি মৌচাক দেখেছি আমি দালানের কড়ি-বরগাতে। বাবা একটা কাগজ ফুলেরগাছ লাগিয়েছিলেন। বিশাল সেই গাছটি এখনো আছে। ওই গাছে স্থায়ী মৌচাক ছিল যারা কিছু দিন পরপর মধু খেয়ে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত। বাবা আমায় চাক ভাঙার আশ্বাস দিলেও দিনক্ষণ দেখে আর ভাঙা হয়ে উঠত না।
একবার মৌচাক হলো আমাদের মাঝখানের বড়ো ঘরের (এই ঘরটা এত বড়ো যে শীতকালে বৃষ্টি এসে গেলে এখানে মহিষ দিয়ে মলন ঘোরানো যেত। এখানেই আমার জন্ম হয়েছিল বলে, এটা ছিল আমার ঘর।) কড়িতে। মেঝে থেকে প্রায় বাইশ ফুট উঁচু কড়ি। দেওয়াল ঘেঁষে চাক। আমি জোর বায়না শুরু করলাম বাবার কাছে, ‘ওই চাক ভাঙতেই হবে।’ বাবা বললেল, ‘চাক ভাঙার লোক আছে, ওদের খবর দিই।’ আমি নাছোড়বান্দা। চাক আজকেই ভাঙা চাই।
ছোটোবেলায় আমি পা দাপিয়ে কাঁদতাম। শুরু হলো কান্না। খাওয়া বন্ধ। ঘেরের কিষাণ রাজি নয়। পিন্টুদা বলল, পারবে না। শেষমেশ বাবা-ই উঠবেন চাক ভাঙতে। আমার উৎসাহের শেষ নেই। গৌরদাদুকে ডেকে আনলাম দৌড়ে গিয়ে।
দাদুকে নিয়ে বাবা দুটো মই জোড়া দিলেন। পিসি তুলসী পাতার রস মেখে দিলেন বাবার মুখে, হাতে। কুটোর বিড়েয় আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি করা হলো। এবার মৌচাক ভাঙা হবে। বাবা গায়ে মাথায় বস্তা জড়িয়ে প্রস্তুত। বাবার বাম হাতে সমস্যা। একহাতে মই বেয়ে অত উঁচুতে উঠবেন কীভাবে ভেবে এবার আমি ভীত হলাম। বাবাকে যারা জানেন তারাই বুঝবেন সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাঁর কেমন আগ্রহ ছিল।
কোমরে কাঁচি গুঁজে বাবা তরতর করে উঠে যাচ্ছেন ওপরে। গৌরদাদু নিচে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া দিচ্ছেন।
একটি দুটি করে মৌমাছি উড়তে উড়তে ঘর ভরে গেল। বাবার গায়ে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে তারা। গৌরদাদুও কামড় খেলেন। চাকে মধু আছে প্রচুর। বাবা চাক কেটে নিচে ফেলে দিয়ে চিৎকার করছে—মানি, ঘর থেকে বের হও। এক্ষুনি বের হও।
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি বাবার আতঙ্কিত মুখ। নিজের শরীরে বিষজ্বালা অথচ, আমার শরীরে যাতে হুল না বসে তার জন্য বিকট চিৎকারে সমস্ত বাড়িকে সন্ত্রস্ত করে তুললেন।
একমাত্র বাবারাই বুঝি পারেন সন্তানের আনন্দ বিধানের জন্য এভাবে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতে।
কবিগান
কবিগান আসলে কী এটা বুঝে ওঠার অনেক আগের থেকেই আমি কবিগান শুনতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। কবিগানের সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা পারিবারিক। মতুয়াগুরু ভেকটমারির বাকসিদ্ধ অনন্ত পাগল আমার মায়ের দাদু। পাগলকে আমি দেখিনি কিন্তু দেখেছি তাঁর প্রভাব। ওবাড়ি কবিগান হতো প্রায়ই। দিদিমা বলতেন, বিজয় সরকার, অনাদি সরকার, রাজেন সরকার থেকে শুরু করে বিখ্যাত বিখ্যাত কবিয়াল সকলেই ওবাড়ি এসে জিরোন দিতেন আর এক আসর করে গান গাইতেন। পাগলের বড়ো ছেলেও কবিগান গাইত টুকটাক। আমি দেখেছি নারায়ণ সরকারকে অনেকবার। তাঁর কাছে মজার মজার গল্পও শুনেছি। দিগিন্দ্র সরকার আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মাঝে মাঝে আসতেন মামাবাড়ি। তাঁর মুখে গান শুনেছি, আর গল্পও। ছোটোবেলায় দেখতাম কোনো একটা উপলক্ষ্য পেলেই এলাকার মানুষ কবিগানের আয়োজন করছে। দিদিমা খুব কবির ভক্ত। তাঁর সাথে আমিও গিয়ে বসে বসে বুট বাদাম খেতাম।
মানুষের মুখে মুখে কেবল কবিগানের কথা। আমাদের ঘরবাড়ি, আনাচ-কানাচ সব পরিষ্কার করা হলো। প্রচণ্ড গরম তখন। গোলপাতা দিয়ে পাতলা ছাউনি তোলা হলো আমাদের রান্নাঘরের পেছনে। ওদের বাড়ি তো বিশাল আয়োজন।
আমার বয়স তখন এত অল্প যে মনে থাকার কথা নয়, তবু স্পষ্ট মনে আছে। পাগলের আশ্রমে একবার অনাদিজ্ঞান সরকার এলেন। সম্ভবত মৃত্যু/ দেশত্যাগের আগে এটাই তাঁর শেষ আসা। সে কী বিপুল আয়োজন! মানুষের মুখে মুখে কেবল কবিগানের কথা। আমাদের ঘরবাড়ি, আনাচ-কানাচ সব পরিষ্কার করা হলো। প্রচণ্ড গরম তখন। গোলপাতা দিয়ে পাতলা ছাউনি তোলা হলো আমাদের রান্নাঘরের পেছনে। ওদের বাড়ি তো বিশাল আয়োজন। কবিগানের দিন পিঁপড়ের মতো লোকজন আসতে লাগল। স্থানের সংকুলান হয় না শেষে। আমি দিদিমার কোলে বসে বসে মানুষ দেখছিলাম আর মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঘষা বরফ খেয়ে আসছিলাম কাচের গ্লাসে করে। উনি যে বিখ্যাত অনাদি বাবু, তা পরে জেনেছি। এই গানটা গেয়েছিলেন সেদিনও- ‘ওপার হতে যারা, সাথে এসেছিল তারা, পার হয়ে গেল আগে। আমি একা বসে আছি ঘাটে।’
কবিগানের সাথে আমাদের দক্ষিণের মানুষের বেশ আবেগ জড়িয়ে আছে। আমার ঠাকুরদা সংগীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কীর্তনের দল ছিল তাঁর। আমাদের বাড়ি নাকি বিজয় সরকার অনেকবার গিয়েছেন কবি গাইতে।
কবিগান পরে শুনেছি আর ভালো করে জেনেছি বাংলা সাহিত্য পড়তে এসে। ক্লাসে যখন স্যার কবিগানের ইতিহাস পড়াতেন, আমি খুব গর্বিতমনে ভাবতাম, এমন জীবন তো আমি নিজেই যাপন করেছি। কবিগানের মাঝে বড়ো হয়েছি।
কয়েক বছর আগে আমাদের বিদ্যারবাহনের বিখ্যাত ভূতের আবাস দেওয়ান ভিটার কাছে অসীম সরকার এসেছিলেন কবি গাইতে। আসলে অসীম বাবু একটু বেশি আধুনিক যা কবিগানের সাথে মানায় না। একটু বেশি ভাবুকও তিনি। আমি তাই শুনতে গেলাম না। মা গেলেন। কবির আসর যেখানে বসেছিল তার কয়েক গজ দূরেই পশুর নদী। তখন ভরা দুপুর। উতলা হাওয়া বইছে ফাল্গুন মাসের। পশুরের জোয়ার ফুলে ফেঁপে একেবারে কানা ছুঁয়ে উপচে পড়ার মতো। মাথার ওপরের বাদাম বাতাসে ছিঁড়ে যায় যায় ভাব। ঠিক তেমন মুহূর্তে অসীম বাবু উদাত্ত কণ্ঠে গাইছেন অনাদি বাবুর এই বিখ্যাত ধুয়া—ওপার হতে যারা, সাথে এসেছিল তারা, পার হয়ে গেছে আগে। আমি একা বসে আছি ঘাটে।
ভাবুন তো একবার চোখ বুজে। মায়ের মুখে শুনে আমি আফসোস করেছিলাম এমন ধন থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে।

জন্ম ১৯৯৩ সালের ১২ অক্টোবর বাগেরহাটের মোংলায়। পড়াশোনো করেছেন ভেকটমারী বেলাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুন্দরবন ডিগ্রি মহিলা কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বাংলার প্রভাষক হিসেবে কাজ করছেন ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রকাশিত গ্রন্থ; প্রবন্ধ: ‘বৈষ্ণব পদাবলী: নারীবাদী বীক্ষণ’, ‘বাউলপদাবলীতে চৈতন্যপ্রভাব’, উপন্যাস: ‘ময়নাঢিপির কথকতা’।