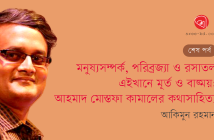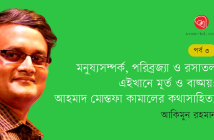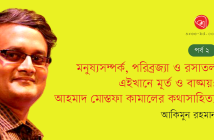যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতায় প্রবেশ করার আগে আমরা ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে দু-একটা কথা মনে করতে চাইব। কিন্তু যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতাসংগ্রহ-এর ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন? এই সংগ্রহের কবি একজন মানিক-গবেষক ছিলেন সেই কারণে?
যুগান্তর চক্রবর্তী নিছক একজন মানিক-গবেষক ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষেই তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনে অবগাহন করেছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকট ও সংকল্প। তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য জীবনের দ্বন্দ্বময় ভাষ্য।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা ৩৭টি উপন্যাস ও দুই শতাধিক গল্পের প্রায় কোনোটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করে যাননি। এমনকি কোনো রচনারই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রথম পাঠও তিনি সংগ্রহ করে রাখেননি। নেই পাঠান্তরের কপিও। শুধু ছিল মরচেধরা, তোবড়ানো তিন চারটি টিনের ট্রাঙ্ক। কী ছিল তাতে? ছিল অজস্র ছিন্নভিন্ন পাতা। কয়েকটি খাতা। আর নানা মাপের বারোটি ডায়েরি। ডায়েরিগুলোর সময়কাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬। এইসব ডায়েরিগুলোও আবার সাল তারিখ মেনে লেখা নয়। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা অনিয়মিত ও পারম্পর্যহীন। একজন লেখকের ডায়েরি বলতে যা বোঝায়, এই ডায়েরিগুলো তেমন নয়। তাহলে কেমন? একজন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মানুষের মন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে এইসব ডায়েরির পাতায় পাতায়। এইসব ডায়েরি, চিঠিপত্র দিনের পর দিন নিবিড়ভাবে পাঠ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন যুগান্তর চক্রবর্তী। কীভাবে? কাজটা ১৯৫৯ সাল থেকে শুরু করলেও তাঁর সম্পাদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর দু-দশক পর প্রকাশিত হয় অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রামান্য সংকলন। ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ডায়েরি ও চিঠিপত্র’। কিন্তু শুধু এটুকুই? তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আরও দুটি বই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৫) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)। লেখকের জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধগ্রন্থ ‘সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: দ্বন্দ্বের দুই মুখ’ (২০০৮)। এ ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন বই প্রকাশ করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় একটা জীবন তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য উৎসর্গ করেছেন।
কিন্তু আবারও ওই একই প্রশ্ন। যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতাসংগ্রহর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গ কেন?
কারণ অন্য কিছু নয়, কবির সম্পাদকসত্তা। ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ডায়েরি ও চিঠিপত্র’ গ্রন্থের সম্পাদকের ভেতর যে সম্পাদকসত্তা গড়ে উঠছিল, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তা, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যুগান্তর চক্রবর্তীকে সাহায্য করেছে। কীভাবে? যুগান্তর চক্রবর্তীকে তাঁর সম্পাদকসত্তা কবিতায় শুধু মিতবাক সাহায্য করেছে, তা নয়, তিনি আর পাঁচজন বাঙালি কবির মতো একই কবিতা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পুনরাবৃত্ত করেননি। ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’র মতো একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ লেখার পর কবি হিসেবে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পান কিন্তু তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে তখন তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। কবিতা লেখার পরিবর্তে তিনি আরও গভীরভাবে মানিক-গবেষণায় ডুব দেন। এই রকম সংযম বাংলা কবিতার জগতে বিরল। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে একজনের, তিনি সমর সেন।
এই যে একটা উচ্চতায় পৌঁছেও তিনি থেমে গেলেন এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ভেতরে একজন কবির পাশাপাশি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল সম্পাদকসত্তা। যিনি জানতেন, কোথায় তাঁকে থামতে হবে।
এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ১৯৬৮ সালে একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে যিনি নিজেই লেখা প্রায় ছেড়ে দিলেন কেনই-বা তাঁর কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল? সত্যই কি এর প্রয়োজন ছিল? আছে?
২.
‘তিমির সীমান্ত’। যুগান্তর চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। কবির বয়স তখন উনিশ। কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থটিকে পরবর্তীকালে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু কেন? গান্ধার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে যুগান্তর চক্রবর্তী বলেছিলেন, ‘…বইটাকে আমি অস্বীকার করি আর কোনও কারণে নয়, বইটা ঠিক কোনো চরিত্র পায়নি। মানে পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা যদি থাকত, একটা ব্যাপার হত। বা সেইসময় অন্য রাজনীতি-বর্জিত কবিতাগুলো থাকত, তাহলেও অন্যরকম একটা চরিত্র পেত। কোনোটাই না করার ফলে না-এদিক না-ওদিক কিছুই দাঁড়াইনি।’ কিন্তু সত্যই কি দাঁড়ায়নি? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো আজ আর সম্ভব নয়। কারণ এ-বইটি কারো কাছেই নেই। এমনকি যুগান্তর চক্রবর্তীর নিজের বাড়িতেও নেই। তাহলে? আদিপর্বের কোনো লেখার সঙ্গেই কি পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়?
বার্মা থেকে ফিরে মালদায় বাস শুরু করেন চক্রবর্তী পরিবার। যুগান্তর যখন দশম শ্রেণির ছাত্র তখন সরোজ রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক বর্তমান পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি কেমন? ২০০৪ সালে কবিসম্মেলন পত্রিকায় চৈতালী চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে স্মৃতি থেকে ওই কবিতার তিন পঙ্ক্তি বলেছিলেন। যুগান্তর চক্রবর্তী রচিত পঙ্ক্তি তিনটি এই রকম:
আজও আমি চেয়েছি তোমাকে
আজও দেখি চাঁদ ওঠে বাদামি পাতার ফাঁকে ফাঁকে
যদিও গলির মোড়ে ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল করে ভিড়
একজন দশম শ্রেণির ছাত্র, কতই বা তাঁর বয়স, বড়োজোর ১৬, তাঁর পক্ষে এর থেকে পরিণত লেখা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যুগান্তর চক্রবর্তী ছাত্রাবস্থা থেকে বামপন্থি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে বামপন্থি সাহিত্যের সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। কিন্তু একটা সময়ের পর তিনি সাহিত্যে বামপন্থি অনুশাসন মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ বামপন্থি সাহিত্যে রোমান্টিসিজম পরিত্যাজ্য। একটি সাক্ষাৎকারে যুগান্তর বলছেন, ‘প্রেম তো সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। বাদ দিয়ে নয়। আন্দোলন তো তোমাকে নিয়েই।’
তিনি যখন মালদা থেকে পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় চলে এলেন সে সময় তাঁর বন্ধুবৃত্তে অনেকেই ছিলেন, অনেক সাহিত্যপ্রয়াসী। রাম বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, দীপক মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে। তবে কৃত্তিবাসীদের রাজনীতিবিমুখ স্বীকারোক্তিমূলক লেখা যুগান্তরকে আকর্ষণ করতে পারেনি।
তিনি যখন মালদা থেকে পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় চলে এলেন সে সময় তাঁর বন্ধুবৃত্তে অনেকেই ছিলেন, অনেক সাহিত্যপ্রয়াসী। রাম বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, দীপক মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে। তবে কৃত্তিবাসীদের রাজনীতিবিমুখ স্বীকারোক্তিমূলক লেখা যুগান্তরকে আকর্ষণ করতে পারেনি। নিজে কমিউনিস্ট হলেও বামপন্থি ঘরানার কবিতার ব্যাপারেও তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল। তাই তাঁর কবিতায় সময়ের প্রহার খুব একটা দেখা যায় না। নেই সোশ্যাল কমিটমেন্ট। ধ্রুপদি ঘরানা থেকে খুব দূরে অবস্থান না করলেও তাঁর কবিতায় সেভাবে ধ্রুপদি উচ্চারণও দেখা যায় না। তাহলে কী আছে তাঁর কবিতায়? কাব্যগ্রন্থটিতে?
৩.
১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’। প্রকাশমাত্রই দীক্ষিত পাঠকের বিপুল সমাদর পায় এ বই। অন্বিষ্ট পত্রিকায় বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে একটি গদ্য লেখেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত আসামের একটি কাগজে দীর্ঘ একটি গদ্য লেখেন। আরও কিছু লেখা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। এখনও হয়।
ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, যুগান্তরের কবিতার পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ভাষার সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। সহজ ও চেনাজানা শব্দের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন মনের গহন ভাব। বিমূর্ততা। তাঁর কবিতায় খুব সহজেই মিশে যায় চেতন ও অবচেতন। লৌকিক ও অলৌকিক। তাঁর কবিতায় অকারণ যেমন জটিলতা নেই তেমনি তা একমাত্রিকও নয়। অর্থাৎ ভঙ্গিমার দিক থেকে একটা মধ্যপন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ছন্দের ভেতরে থেকেও তিনি কবিতার ভেতর প্রবাহিত করতে পেরেছেন মুক্তির বাতাস। কী রকম সেই বাতাস, আসুন, এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে লক্ষ করি:
আমাকে জাগাবে বলে একি গান ঘুমভাঙানিয়া।
সারারাত জেগে-জেগে অমন বালিকাবেলাগুলি
হঠাৎ ভাসালে আজ, এ-কার উদাস ভীরু হিয়া
ঘুমের বাগান যেন—আমি সাজি হাতে ফুল তুলি।
এ-আনন্দে সব বুঝি ভেসে যায়, ভেসে যেতে পারে।
প্রতিটি দিনের দৈন্য ধুয়ে ধুয়ে ধারায় ধারায়
সংগীত, সংগীত শুধু—প্রভাতফেরির পারাপারে
তমসা-আকুল মুখ অবগুণ্ঠনের মুক্তি চায়।
এই তো জীবন, আহা, এরই টানে বালকের মতো
একবার বাহিরে এসে ঘরে ফেরা আবার, আবার
মনে হয় কী সহজ, কী সহজ এই ভিক্ষারত
পৃথিবীর অধিবাস, দেয়া-নেয়া মুগ্ধ উপহার
আমাকে জাগাবে বলে এ-পথের বাসরের কাছে
সারারাত জেগে-জেগে সেও বুঝি অপেক্ষায় আছে।
কবিতাটি যে খুব দুরূহ বা রহস্যময়, তা নয়। কিন্তু পুরো আবহটা যে চেনা, তাও নয়। তবে ঘুমভাঙানিয়া শব্দটি মনে পড়ায় রবীন্দ্রনাথকে। কীভাবে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ/ ওগো ঘুমভাঙানিয়া।’ আর যুগান্তর? রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে তিনি লিখলেন আমাকে জাগাবে বলে একি ঘুমভাঙানিয়া। এইখানে এসে প্রশ্ন এসে যায় কথক কি তাহলে ঘুমিয়ে ছিলেন? আর সে জন্যই কি গান ঘুমভাঙানিয়া? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন এসেই যায়, এই ঘুমভাঙানিয়া গান কে গাইছেন? প্রকৃতি? নাকি প্রেয়সী? নাকি ঈশ্বর? ঈশ্বর যে নন, তা ‘বালিকাবেলা’তে পৌঁছে বোঝা যায়। কবি এখানে অসাধারণ একটা ইমেজ রচনা করেছেন। ‘বালিকাবেলাগুলি হঠাৎ ভাসালে আজ।’ এ রকম হয় নাকি? বালিকাবেলাগুলি ভাসে? ভাসে তো বটেই। আর ভাসে বলেই পৃথিবীকে মনে হয়, ‘ঘুমের বাগান যেন’। কিন্তু এই বাগানে কবি কী করছেন? কথক নিজেই বলছেন, ‘আমি সাজি হাতে ফুল তুলি।’ এখন মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, কার জন্য তিনি সাজি হাতে ফুল তুলছেন? প্রেয়সীর জন্য? নাকি ঈশ্বরের জন্য? এর কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। থাকার কি খুব প্রয়োজন আছে? এই কবিতা খুব একটা যুক্তির ধার ধারে না। ‘তাই এ আনন্দে বুঝি সব ভেসে যায়, ভেসে যেতে পারে’/ আর প্রতিটি দিনের দৈন্য ধুয়ে ধুয়ে যায় ধারায়।’ কীসের ধারায়? সংগীতের ধারায়, যে ধারা শুরু হয়েছিল ঘুমভাঙানিয়া গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর? ‘প্রভাতফেরির পারাপারে তমসা-আকুল মৃগ অবগুণ্ঠনের মুক্তি চায়’। এখানে লক্ষণীয়, শুরুতে প্রভাতের পারাপারের কথা বলা হলো না। যুগান্তর লিখলেন ‘প্রভাতফেরির পারাপারে’। এখন দেখার, আশ্চর্য সেই স্থানে কী হচ্ছে? সেখানে ‘তমসা-আকুল মৃগ অবগুণ্ঠনের মুক্তি চায়’। এই যে ‘তমসা-আকুল মৃগ’—এ কীসের সংকেত? ‘তমসা-আকুল মৃগ’ হলো আমাদের চেতন ও অবচেতন মনের গহন অভীপ্সা। এই অভীপ্সা সমস্ত ধরনের বন্ধন অতিক্রম করে মুক্তি চায়। জীবন তো এ রকমই। তার জন্য একবার বাইরে এসে আবার ঘরে ফেরা। এই যে ঘরে ফেরা—এ তো মৃত্যুর পরের জীবনের কথা। তাই নয় কি? কিন্তু ভিক্ষারত পৃথিবীর অধিবাস—এর মানে কী? এটি একটি ধূসর অঞ্চল। কিন্তু সত্যই কি ধূসর? দুষ্প্রবেশ্য? পৃথিবীকে তো জীব হিসেবেও কল্পনা করা যেতে পারে, আর জীব হলে তার সঙ্গে তো উপহার দেওয়া-নেওয়া করাই যেতে পারে। যায়ও। এর পরেই, আমরা দেখব, একটা স্পেস। যেন কিছু মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আবার কথক বলছেন, ‘আমাকে জাগাবে বলে এ পথের বাসরের কাছে/সারারাত জেগে-জেগে সেও বুঝি অপেক্ষায় আছে।’ এই পঙ্ক্তি দুটিতে অনেকগুলো মাত্রা লুকিয়ে আছে। প্রথমত এইখানে এসে নিশ্চিতভাবে মনে হয় কথক তথা কবি জেগে নেই। তাঁকে জাগাবে বলে সারা রাত জেগে জেগে সেও বুঝি অপেক্ষায় আছে। এখন এই সে যে কবির প্রেয়সী এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এও বলা যায় অপেক্ষাই আসলে প্রেম। তার জন্য পথের বাসরের কাছে সারা রাত জেগে কাটিয়ে দেওয়া যায়।
অপেক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেমকে দেখলাম এবার দেখব শরীরের ভেতর দিয়ে। শারীরিক মিলন। সংগম। আসুন এই কবিতাটি পাঠ করি:
বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে রাত্রি এক মাঠের কাহিনি।
শিকড়ে আসক্ত জ্যোৎস্না, সিক্ত চাঁদ নক্ষত্রনিকরে।
আচম্বিতে দুঃখ জাগে, দুঃখ ঘোর পায়ে পায়ে ঘোরে।
জলের শিয়রে মৌন বৃক্ষ, তুমি কার কাছে ঋণী।
জলের শরীর বৃক্ষ, ছায়া ধরো জলের শিয়রে।
তোমার শরীর বৃক্ষ, স্রোতায়িত নীরব প্রস্তর।
কেউ অস্ত্র গড়েছিল, কেউ তুলেছিল শান্ত ঘর।
প্রবাহ ফেরাতে থাকো উভয়ে জলের বক্ষোপরে।
প্রবাহ ফেরাতে থাকে বক্ষোমাঝে নিদ্রিতাসুন্দরী।
থাকে অন্তঃপুরে নগ্নঅস্ত্ররেখা সুন্দরী আমার।
কিছুবা প্রস্তর বুঝি, কিছুবা সচ্ছল স্রোতোধার।
শিকড়ে আসক্ত জ্যোৎস্না, সিক্ত চাঁদ কাঁপে বক্ষোপরি।
বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে রাত্রি এক মাঠের কাহিনি।
আচম্বিতে দুঃখ জাগে, তুমি কার কাছে ঋণী।
পুরো কবিতাটিতে একটিও যৌন শব্দ নেই। কিন্ত কবিতাটি একটি সার্থক সংগমের চিত্র। প্রথম পঙ্ক্তিতেই তা পরিষ্কার। বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে রাত্রি এক মাঠের কাহিনি। সত্যই তো তাই। সংগমশেষে রাতকে আর মাঠ নয়, মনে হয় মাঠের কাহিনি। এর পরের যে পঙ্ক্তিগুলো এসেছে তা বৃষ্টিপাত হওয়ার আগের মুহূর্তের কিছু ছবি। ‘শিকড়ে আসক্ত চাঁদ,’ জলের, শরীর বৃক্ষ, ছায়া ধরো জলের শরীরে’, ‘প্রবাহ ফেরাতে থাকো উভয়ে জলের বক্ষোপরে’ কিংবা ‘অন্তঃপুরে নগ্নঅস্ত্ররেখা সুন্দরী আমার’। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এইসব রূপক একটা সংগমের আয়োজনকে পূর্ণতা দিচ্ছে।
এখন একটা প্রশ্ন মনে আসতেই পারে, কে স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি? কবিতা? নাকি ঈশ্বর? এগুলো যে নয়, অন্তত ‘পূর্ণিমা ১৯৬৭’ কবিতায় স্মৃতি বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি হল কবির প্রেয়সী তা একবার পাঠ করলেই বোঝা যায়।
আসুন, পাঠ করি কবিতাটি।
পূর্ণিমা, তোমার গায়ে গতবছরের গঙ্গাজল
লেগে আছে। তুমি সমসাময়িক হতে শেখ নাই।
তোমাকে যেতেছে আজও স্পষ্ট দেখা,
তুমি আজও গত বছরের
ফেরিঘাট ব্রিজ, ট্রামলাইন ট্রাফিক সংকেত
পার হয়ে দেখা করো, কাছে এসো,
বসে থাকো পাশাপাশি, গত বছরের কাছাকাছি।
তুমি স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি।
তুমি নগ্ন করো নীল পান্থশালা।
তুমি পরিপ্রেক্ষিতের অর্থ চাও,—তোমার বিছানা
এইখানে পাতা হবে, তুমি বলো।
পূর্ণিমা, তোমার বুকে গত বছরের প্রাচীনতা।
তুমি রেখেছিলে হাতে, মনে হয়,
চিরজীবনের মুখভার।
একটা আদ্যন্ত প্রেমের কবিতা এটি। কিন্তু প্রেয়সীকে কোনোভাবেই মহিমান্বিত করা হয়নি। এমনকি প্রেয়সীর নামটাও অত্যন্ত সাদামাটা, পূর্ণিমা। তাকে ঘিরে যে কল্পনার আয়োজন সেখানেও খুব একটা আধুনিকতা নেই। তাহলে কী আছে? ‘তোমার গায়ে গতবছরের গঙ্গাজল লেগে আছে।’ গঙ্গাজল একটা পবিত্র জিনিস, সেই পবিত্রতার কারণেই কি প্রেয়সীর গায়ে তা লেগে থাকার কথা বলা হয়েছে? নাকি গঙ্গাজলের মধ্য দিয়ে যৌবনকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে? উত্তর যায় হোক, একটা প্রশ্ন কিন্তু এসে যায়। সেটা হল গতবছরের কেন? গতবছরের গঙ্গাজল কি একবছর ধরে কারো শরীরে লেগে থাকতে পারে? থাকে? একজন কবি একজন দ্রষ্টা, তাঁর দৃষ্টিতে তা হতেই পারে। হয়ও। প্রেয়সীর গায়ে, তিনি দেখতেই পারেন, লেগে আছে গতবছরের গঙ্গাজল। বা জলের ঘ্রাণ। আসলে শুরু থেকেই প্রেয়সীর একটা আবছা অবয়ব আঁকার চেষ্টা করছেন কবি। সে জন্যই হয়ত তিনি লিখছেন ‘তুমি সমসাময়িক হতে শেখো নাই’। কিন্তু পরক্ষণেই কেউ যাতে তাকে আবছা না ভাবেন সে জন্য লিখছেন ‘তোমাকে যেতেছে আজও স্পষ্ট দেখা।’ এখানে, এই পঙ্ক্তিটিতে লক্ষণীয়, তিনি লিখছেন আজ নয়, আজও। অর্থাৎ এই ব্যাধিগ্রস্ত পৃথিবীতে একজন প্রেয়সীর সঙ্গে থাকা ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাকে যে শুধু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তা তো নয়, গত বছরের ফেরিঘাট স্ট্র্যান্ড রোড ট্রামলাইন ট্রাফিক সংকেত পার হয়ে সে তার সঙ্গে দেখা করছে, বসেও থেকেছে পাশাপাশি। পাশাপাশি কেন? কারণ, তুমি স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি। তবে, আমার মতে এ কবিতার শ্রেষ্ঠ পঙ্ক্তি পরের পঙ্ক্তি। ‘তুমি নগ্ন করো নীল পান্থশালা’। একজন জাত কবি ছাড়া এই রকম উচ্চতার বহুস্তরীয় পঙ্ক্তি লেখা সম্ভব নয়। এই পঙ্ক্তিটির অনেকগুলো মাত্রা থাকতে পারে। আছেও।
কিন্তু তাকে যে শুধু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তা তো নয়, গত বছরের ফেরিঘাট স্ট্র্যান্ড রোড ট্রামলাইন ট্রাফিক সংকেত পার হয়ে সে তার সঙ্গে দেখা করছে, বসেও থেকেছে পাশাপাশি। পাশাপাশি কেন? কারণ, তুমি স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি। তবে, আমার মতে এ কবিতার শ্রেষ্ঠ পঙ্ক্তি পরের পঙ্ক্তি। ‘তুমি নগ্ন করো নীল পান্থশালা’। একজন জাত কবি ছাড়া এই রকম উচ্চতার বহুস্তরীয় পঙ্ক্তি লেখা সম্ভব নয়।
পান্থশালা পথিকের কাছে একটা আশ্রয়। এখন এই পান্থশালা নিছক পান্থশালা নয়, ‘নীল পান্থশালা’। নীল এই শব্দের মধ্য দিয়ে একটা স্বপ্নের আবহ তৈরি হচ্ছে। আর পূর্ণিমা? সে কী করছে? ‘তুমি নগ্ন করো নীল পান্থশালা’। অর্থাৎ পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো স্বপ্নের এক-একটা স্তর উন্মোচন করে চলেছে। কিন্তু শুধু এ-টুকুই? এই পঙ্ক্তির ভেতর নীল পান্থশালার মধ্য দিয়ে কি আমরা প্রেয়সীর শরীরও কি দেখতে পাই না? না যদি পাই, তাহলে কেন এক পঙ্ক্তি পরে লেখা হলো ‘তোমার বিছানা এইখানে পাতা হবে, তুমি বলো।’
যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতার প্রেরণা, আমার মনে হয় আবেগ। কিন্তু তাঁর কবিতা আবেগের স্ফুরণ নয়, তিনি আবেগ থেকে প্রজ্ঞার দিকে যাত্রা করেছেন। রচনা করেছেন ধীকে। তাই একটা শান্ত ও নাটকীয়তাবর্জিত মেধাবী উচ্চারণ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় আর যা থাকে তা হলো নিরাভরণ সৌন্দর্য। কেমন সেই সৌন্দর্য, আসুন দেখি।
তোমাকে গানের দেবী মনে হয়, কিন্তু কই তোমার নগ্নতা,
যা ছাড়া পায়ের কাছে বসা ভার, ঊরুর উপর ন্যস্ত মাথা
রাখা ভার।
তুমি তো গানের দেবী,
কিন্তু এনেছিলে কোন গান
সে কি রেখেছিলে মনে? কিছু তার জানে কি স্তব্ধতা?
তোমার বিস্তৃতি—সে কি তোমার শান্তির পরিমাণ?
তুমি কি গানের দেবী?
কেন পাশে রয়েছ শয়ান?
তোমার মাথার কাঁটা বুকে বেঁধে, দেখি না যে ডানার যুগ্মতা।
আমাকে শোনাতে হবে বলে তুমি শেখো নাই
কোনো প্রিয় গান।
কত সহজ এই উচ্চারণ অথচ কী গভীর! প্রথম পঙ্ক্তিতেই রয়েছে দর্শনসিক্ত উপলব্ধি। তোমাকে গানের দেবী মনে হয় কিন্তু কই তোমার নগ্নতা। যেন নগ্নতা ছাড়া দেবী হওয়া সম্ভব নয়। নগ্নতাই সভ্যতার প্রথম ধাপ। সিঁড়িও। তাই তা ছাড়া ‘পায়ের কাছে বসা ভার’। ‘ঊরুর ওপর ন্যস্ত মাথা রাখাও ভার’। প্রথম পঙ্ক্তিতে প্রেয়সীকে গানের দেবী মনে হয়েছিল, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে এসে সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া গেল। কীভাবে? কবি বলছেন, তুমি তো গানের দেবী। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংশয়। কিন্তু ‘এনেছিলে কোন গান/ সে কি রেখেছিলে মনে?’ এরপর একটা আশ্চর্য পঙ্ক্তি। কিছু তার জানে কি স্তব্ধতা? এর মানে? স্তব্ধতা কি গানের শেষ কথা? শেষ কথা তো বটেই। কবিতার মতো গানও আসলে এক ধরনের স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতার ভাষা যুগান্তর চক্রবর্তী জানতেন বলেই লিখতে পেরেছেন, ‘তোমার বিস্তৃতি—সে কি তোমার শান্তির পরিমাণ?’ এর পরক্ষণেই আবার সংশয়। ‘তুমি কি গানের দেবী?’ না হলে কেন তবে ‘তোমার মাথার কাঁটা বুকে বেঁধে, দেখি না যে ডানার যুগ্মতা।’ এখানে ডানার যুগ্মতা দিয়ে কি উড্ডীন অবস্থাকে বলতে চাওয়া হলো? নাকি ডানার যুগ্মতা আসলে প্রেয়সীর ভীরু দুই স্তন? একটা স্পেসের পর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরেক বিস্ময়। যাকে এতক্ষণ গানের দেবী বলা হচ্ছিল তাঁর সম্পর্কে কবি লিখছেন, ‘আমাকে শোনাতে হবে বলে তুমি শেখো নাই কোনো প্রিয় গান।’ এই কবিতায় একটিই ভাবনা জলের মতো বারবার বিভিন্ন রূপে ঘুরে এসেছে।
আরেকটা তীব্র সংরাগের কবিতা পাঠ করব।
তোমার বুকের জামা তুমি খুলে দেবে নিজ হাতে,
আমি চাই। আমার নশ্বর হাত অন্যত্র রয়েছে।
আমি চাই উৎসর্গবিহীন
সব লেখা, সব প্রেরণার আগে তুমি।
তোমার বুকের পরে আজ কোনো অপর কবির
দাবি নাই। সমস্ত নশ্বর হাত অন্যত্র রয়েছে।
আমাদেরও মুখোমুখি শুতে হবে,
ওরা কি বোঝে না।
এ হলো প্রেয়সীর প্রতি তীব্র অধিকারের কবিতা। এমনই অধিকার যে, বুকের জামার ভেতর যে দুটি স্তন থাকে তা কবির জন্য উন্মুক্ত করতে বলা হচ্ছে। যদিও, কী আশ্চর্য, কথকের নশ্বর হাত অন্যত্র আছে। অন্যত্র সেটির ভূমিকা কী, সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। আমরা অবলোকন করছি দুই পঙ্ক্তি পর প্রেয়সীর প্রতি কথক ফতোয়া জারি করছেন। কী রকম সেটি? তিনি বলছেন, ‘তোমার বুকের পরে আজ অপর কবির দাবি নেই’। খুবই সঙ্গত দাবি। প্রেয়সীর প্রতি যেকোনো প্রেমিকের তো এই রকম দাবি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।
এবার আরেকটা চমৎকার কবিতা পাঠ করব। ‘স্বগত’।
নীহারিকাপুঞ্জে আমি সুপ্ত আছি, হে কবিকুমার
জাগরণে চাই নদী, চাই জলধারা পায়ে পায়ে,
নিকটে নিকটে চাই বৃক্ষ এক, সিক্ত ছায়ে ছায়ে
আমি যার কাছে যাব তার মুখ সদা উপহার।
কে দুঃখ জাগায় দূরে, কার হাত বাগানে বাগানে
বিষাদে পেয়েছে এক ব্যক্তিসত্তা—খুঁজে ফেরে স্মৃতি,
চন্দনের গন্ধবনে কার দীর্ঘরেখা গানে
রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায় পোড়ে—আমি চাই তাহার প্রতীতি।
জ্বালো অগ্নিশিখা। আমি এতকাল গঠিত চরিত্র
একা একা ভাঙব বলো, হানো অন্ধতম বৃষ্টিপাত,
বিনষ্ট আলোর নীচে শায়িত যে শরীর পবিত্র
আমি তার নিপাতিত দৃশ্যে হব জলের প্রপাত।
নীহারিকাপুঞ্জে আমি সুপ্ত আছি, হে কবিকুমার
আমি চাই উভয়ের প্রবেশের একটি দুয়ার।
কবিতাটি শুরু হয়েছে মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এই কবিতাটি খুব ব্যাখ্যাযোগ্য কবিতা নয়। তাহলে? কবিতাটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে অসাধারণ বিমূর্ততা। বোধ। কেমন সেই বোধ? বিমূর্ততা? দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তি হলো, ‘চন্দনের গন্ধবনে কার রূপ দীর্ঘরেখা গানে/ রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায় পোড়ে—আমি চাই তাহার প্রতীতি।’ এইখানে রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায় যা পোড়ে তা কি পার্থিব কিছু? সম্ভবত নয়। একটা সৌন্দর্যের ধারণা দিচ্ছে এই পঙ্ক্তি। শেষে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বোধ। ‘আমি চাই তাহার প্রতীতি’। এইখানে একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, কেন তাহার প্রতীতি? তার প্রতীতি নয়? সৌন্দর্যের যে ধারণা তার প্রতি দূরত্ব আরোপ করার জন্যই সম্ভবত তাহার শব্দের প্রয়োগ। তৃতীয় স্তবকটি পুরোটাই চমৎকার। কিন্তু শেষ স্তবকের অন্তিম পঙ্ক্তিটি কি দুষ্প্রবেশ্য? ‘আমি চাই উভয়ের প্রবেশের একটি দুয়ার।’ এখানে যে উভয়ের কথা বলা হচ্ছে এই উভয়ে কারা? কবি ও তার প্রেমিকা? সম্ভবত নয়। তাহলে কবিতার নাম ‘স্বগত’ হতো না। তাহলে? এই দুজন হলো ব্যক্তি-আমি ও কবি-আমি। এই দুই আমির ভেতর কবি চাইছেন যোগাযোগ। ‘প্রবেশের দুয়ার’।
এবার আমরা একটু অন্য ধরনের দুটি কবিতা পাঠ করব। গভীর দর্শন কাজ করছে কবিতা দুটির ভেতর। কিন্তু কবিতা দুটি কোনোভাবেই দর্শনের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। আলোচ্য কবিতা দুটি হলো ‘অর্জুনবিষাদ’, এবং ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুন’। ‘অর্জুনবিষাদ’ কবিতা সম্পর্কে ‘তিরপূর্ণি’ পত্রিকার বইমেলা ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে যুগান্তর চক্রবর্তী বলছেন, ‘কবিতাটির প্রথম ৪ লাইন লিখেছিলাম—প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ১৯৪৯ সালে। তারপর আটকে যায়। শেষ করতে পারি ৭ বছর পরে ১৯৫৬তে। এই ৭ বছর এই একটা কবিতা লেখারই চেষ্টা করেছি।’ ৭ বছরে বাকি কবিতা অর্থাৎ ৭ বছরে বাকি ১০টি পঙ্ক্তি রচনা করেছেন। ভাবা যায়!
পুরো কবিতা পড়ার পরিবর্তে কবিতাটির শেষ দুটি স্তবক, আসুন, আরেকবার পাঠ করি, যেখানে অর্জুনের বিষাদ ঘন হয়ে উঠেছে।
তোমার নিয়ত বাঁশি বেজে যায়, কিন্তু সে নিঃস্বর
ক্ষমাহীনতারে ভুলে থাকা জানি আরও ক্ষমাহীন।
কোথা তব শূন্যতার সাদা ক্রোধ, পরিণামহীন
কেন নাম, কোথা নামহীন কবি, প্রেরণা অক্ষর।
তোমার শৃঙ্খল ওই পড়ে আছে, ওই অভিজ্ঞতা
আজও নাম ধরে ডাকে। মাথা তোলে দিব্য অক্ষমতা।
এ হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের অভিমান। শুধু অভিমান নয়, বিষাদ। দিব্য অক্ষমতা।
এবার পাঠ করব ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুন’ শীর্ষক কবিতাটি।
উত্তর তোমার সব জানা আছে, দিয়েছ উত্তর
কিন্তু জিজ্ঞাসাই যার জীবন, অব্যক্ত হতে যারে
অব্যক্তে পৌঁছাতে ফের ব্যক্ত হতে হয় বারে বারে
সেই জানে কুরুক্ষেত্র, —তাই প্রশ্ন, অতঃপর
বিপন্নতা আমারই তো, পরাজয়, সেও তো আমার
জানি তুমি রাখো নাই আমার ধ্বংসের কোনো সীমা।
চতুর্দিক জুড়ে দেখি জল মাটি পাতাল নীলিমা
এবং তোমার মুখ—তাই প্রশ্ন, অশ্রুধার…
অগ্রসর হতে হবে আরও দূর, কিন্তু কত দূর?
শিল্পের আক্রোশ থেকে চৈতন্যের দূরত্ব যতটা?
ব্যবহৃত হতে হবে, তবু যার শেষ বিরুদ্ধতা
ভাঙে সব অভিজ্ঞান, গর্ভের বিশাল অন্তঃপুর
দীর্ণ করে। শুরু হল নশ্বর অলীক যাতায়াত।
তাই প্রশ্ন অরুন্তুদ, ধর্মহীন, তাই, রক্তপাত
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের দৃষ্টিতে কবিতাটি লেখা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্যতম নায়ক এই অর্জুন। চোখের সামনে তিনি দেখেছেন যাঁদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন তাঁরা সবাই আত্মীয়স্বজন। অর্জুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে না চাইলে শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার গুরুত্ব বোঝান। তিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। কিন্তু শুধুই ভগবান? কৃষ্ণ অর্জুনের সখাও। তাই তিনি জানেন, উত্তর সব জানা আছে তাঁর। তাঁর অর্থাৎ কৃষ্ণের। কিন্তু জিজ্ঞাসাই যাঁর জীবন, তাঁর কী হবে? অব্যক্ত থেকে অব্যক্তে পৌঁছাতে যাঁকে ব্যক্ত হতে হয় সে কি জানে কুরুক্ষেত্রের অবশ্যম্ভাবীতা?
কিন্তু তিনি তো তাঁকে দিয়ে এসব না-ই করাতে পারতেন। তিনি তো বিষ্ণুর অবতার। ভগবান। জল মাটি পাতাল নীলিমার পাশে তিনি দেখেন তাঁর মুখ। কিন্তু সেই মুখ তাকে শান্তি দেয় না, বারংবার প্রশ্ন করায়। কেমন সেই প্রশ্ন? `অগ্রসর হতে হবে আরও দূর, কিন্তু কত দূর?/ শিল্পের আক্রোশ থেকে চৈতন্যের দূরত্ব যতটা?’ শুধু প্রশ্ন নয়, তিনি জানেন তাঁকে ব্যবহৃত হতে হবে। এই তাঁর নিয়তি।
এই যে তাঁর বিপন্নতা সেটা তাঁরই ঠিক কিন্তু তিনি জানেন সেটাও তাঁর সখা কৃষ্ণের রচনা। তাঁকে ঘিরে ধ্বংসের যে আবহ তারও কোনো সীমা তিনি রাখেননি। কিন্তু তিনি তো তাঁকে দিয়ে এসব না-ই করাতে পারতেন। তিনি তো বিষ্ণুর অবতার। ভগবান। জল মাটি পাতাল নীলিমার পাশে তিনি দেখেন তাঁর মুখ। কিন্তু সেই মুখ তাকে শান্তি দেয় না, বারংবার প্রশ্ন করায়। কেমন সেই প্রশ্ন? `অগ্রসর হতে হবে আরও দূর, কিন্তু কত দূর?/ শিল্পের আক্রোশ থেকে চৈতন্যের দূরত্ব যতটা?’ শুধু প্রশ্ন নয়, তিনি জানেন তাঁকে ব্যবহৃত হতে হবে। এই তাঁর নিয়তি। কিন্তু পরের পঙ্ক্তিতে যে রয়েছে ‘তবু যার শেষ বিরুদ্ধতা ভাঙে সব অভিজ্ঞান’ এখানে শেষ বিরুদ্ধতাটা কার? শ্রীকৃষ্ণের কি? কিন্তু এই বিরুদ্ধতা কার প্রতি? অর্জুনের প্রতি কি? এর জন্যই কি গর্ভের বিশাল অন্তঃপুর দীর্ণ করে ভাঙে সব অভিজ্ঞান? আর শুরু হয় ‘নশ্বর অলীক যাতায়াত’। কিন্তু নশ্বর অলীক যাতায়াত এর দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে? অর্জুনের রথে করে যদ্ধে নেমে পড়া? কিন্তু তাহলে সেটা অলীক হবে কেন? এর উত্তর স্পষ্ট না হলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে রক্তপাত হয়েছে। তা হবেও। আর এ কারণেই প্রশ্ন অরুন্তুদ থেকে যাবে।
এটুকুই কবিতাটির সারকথা।
‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতা আলাদাভাবে আলোচনা করার দাবি রাখে। আলোচনা করতামও কিন্তু স্থানাভাবের কথা ভেবে তা করা থেকে বিরত থাকলাম। বিরত থাকার আরেকটা কারণ, এটি একটি গ্রন্থের ভূমিকা, আলোচনামূলক সন্দর্ভ নয়।
৪.
বিপুলভাবে আদৃত হওয়ার পরেও যুগান্তর চক্রবর্তী কবিতা লিখলেন না। ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কেন? ১৯৯৮ সালে গান্ধার পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, ‘সেটা যেত। অনেকে তা করেও থাকেন। অনেক কবি আছেন যাঁরা এটা করেন। কিন্তু আমি কবিতা দিয়ে কিছু একটা করতে চাই বা আমার কবিতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে তাহলে কিছু না কিছু পরীক্ষা-টরীক্ষা করার ব্যাপার থাকে বা করা যায়। কিন্তু করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়াই যায় বা পড়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, আমি যা চাই কবিতাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাই, সেখানে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতারই অভাব, আমি বলব। সে ক্ষমতা আমার নেই। কতকগুলো বাস্তব অসুবিধা বা বাধাও ছিল। আর বাকিটা; পুরোটাই শেষ পর্যন্ত অক্ষমতা। ফলে আমি থেমে গিয়েছিলাম।’
কিন্তু থেমে যাওয়ার কারণ কি শুধুই ‘অক্ষমতা?’ ওই সাক্ষাৎকারে আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, ‘এর জন্য অনেক কিছু দরকার। কবিতার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা জীবনযাপনের দরকার। একধরনের মানে পারিবারিক দায়- দায়িত্ব অমুক তমুকের ভেতরে আমি এত বেশি জড়িত ছিলাম… কবিতা লেখার জন্য একধরনের স্বার্থপরতা দরকার, যাতে এসব কিছুকে দূরে রাখা যায়। এটা মহত্ত্বের কোনো ব্যাপার নয়; নিরুপায়ভাবেই, স্বার্থপর হওয়ার উপায় আমার ছিল না। ফলে আমাকে কবিতাকেই ত্যাগ করতে হয়েছিল।’
এই যে ত্যাগস্বীকার এর কারণ কি শুধুই পারিবারিক দায় দায়িত্ব? সম্ভবত নয়। আমারা শুরুতেই বলতে চেয়েছিলাম, যুগান্তর চক্রবর্তী তাঁর জীবনটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা যে খুব ভুল কিছু বলিনি তা আরেকটা সাক্ষাৎকারে যুগান্তর চক্রবর্তী নিজেই বলেছিলেন। কবিসম্মেলন পত্রিকায় প্রকাশিত চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘তুমি তখন জানতে চাইছিলে না, কবিতা কম লিখি কেন, নানা কারণের মধ্যে এটাও কিন্তু একটা, যে, মানিকবাবুর কাজ নিয়ে মগ্ন হয়ে গেলাম। না খেয়ে পয়সা বাঁচিয়ে কলেজ স্ট্রিটে ওঁর প্রকাশকদের কাছে যেতাম। কাগজপত্র, পাণ্ডুলিপি, সব একটা টিনের বাক্সে রাখা ছিল। তাই নিয়ে মেতে রইলাম।নিজের লেখা চুলোয় গেল। আমি যদি আরও তিনটি বই লিখি, ৫০-১০০ বছর পর নাম থাকবে না, কিন্তু মানিকবাবুর তো থাকবে, এই থিয়োরিটাই আমাকে পেয়ে বসল।’
এখন প্রশ্ন কোন থিয়োরিটা ঠিক? গান্ধার পত্রিকাকে দেওয়া অক্ষমতার থিয়োরি না কবিসম্মেলন পত্রিকায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সংযোগের থিয়োরি।
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাপত্র যথাযথভাবে প্রকাশকে তিনি একটা ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখালেখি থেকে দূরে সরে যাওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু অক্ষমতার তত্ত্ব যেটা তিনি খাড়া করতে চাইছেন সেটা কি ঠিক? তা যদি হবে তাহলে জীবনের উপান্তে কেন তিনি প্রকাশ করলেন তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ? ‘ইষ্টিপত্র এবং অন্যান্য’? কাব্যগ্রন্থ হিসেবে এটি কতটা প্রাতিস্বিক? গুরুত্বপূর্ণ?
৫.
২০০৬ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ‘ইষ্টিপত্র এবং অন্যান্য’। এই গ্রন্থটি চারটি পর্বের সমন্বয়ে সংকলিত। প্রথম পর্বের নাম ‘আঘাটার গান’। এই পর্বের কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৫৩-১৯৫৫। অনুমান করা যায়, এই পর্বের কবিতাগুলো কবি ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ গ্রন্থে ইচ্ছে করেই সংকলিত করেননি। কিন্তু কেন? ‘তিরপূর্ণি’ পত্রিকার বইমেলা ১৯৯৮ সংখ্যায় একটি প্রবেশক গদ্যে উল্লেখ করেন, ‘এই চারটি কবিতা স্মৃতিবিস্মৃতির চূড়ান্ত প্রেস কপিতে ছিল। কিন্তু ছাপা শুরু হওয়ার, শেষ মুহূর্তে, আমি কবিতাগুলি তুলে আনি। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল, গোটা বইটির কিছুমাত্র চারিত্রিক ঐক্য যদি থেকে থাকে, এই চারটি কবিতার জন্যেই তা নষ্ট হচ্ছে।’
অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ওই চারটি কবিতার মধ্যে, ‘পদাবলি’, ‘যখনি তোমাকে টানি’ এবং ‘একটি সূর্যাস্ত’ ‘আঘাটার গান’ পর্বে অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ‘আমার প্রতীক্ষা’ কবিতাটি পরের পর্বে সংকলিত।
‘আঘাটার গান’-এ ওপরে উল্লেখিত তিনটি কবিতা ছাড়াও রয়েছে আরও দুটি কবিতা। ‘আঘাটার গান’ ও ‘নাম ধরে ডাকি না’। এ কবিতা দুটিরও অবশ্য রচনাকাল ১৯৫৪। প্রথম কবিতার প্রথম দুটি পঙ্ক্তিতে পাই যুগান্তর চক্রবর্তী সেই ম্যাজিক উচ্চারণ:
অঙ্গে যে তরঙ্গ দোলে, নিঃশ্বাসের স্পর্শে ফোটে ফুল।
আঙুলে আঙুল লেগে রক্তে বাজে কীর্তনের তালি।
কবিতাটির নিশ্বাসের স্পর্শে শুধু যে ফুল ফুটতে দেখছি, তা নয়, আঙুলে আঙুল লেগে অর্থাৎ সেই স্পর্শে দেখছি রক্তে বাজে কীর্তনের তালি। কিন্তু কীর্তন কেন? তাহলে কি এখানে প্রেমিকা ও ঈশ্বর একাকার হয়ে যাচ্ছে? প্রেমের ভেতর দেখা যাচ্ছে আস্তিক্য। কবিতাটির শেষ স্তবক পড়া যাক:
…নীলিমা তো তোমারই গুণ্ঠন
উদয়াস্ত কাঁপে রোজ। পীতাম্বর পৃথিবী তো নীল।
তাই মুগ্ধ অভিসারে খুঁজি দোঁহে নিঃশেষিত মিল।
যদি মত্ত টানে যমুনার দুরন্ত প্লাবন
সমুদ্রতরঙ্গতটে মুক্ত করে সমস্ত নিখিল।
যদি মৃদঙ্গের বোলে চৌদিক পাঠায় আলিঙ্গন।
এখানেও প্রেম ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখছি কবি বলছেন ‘নীলিমা তো তোমারই গুণ্ঠন/ উদয়াস্ত কাঁপে রোজ’। এইখানে এসে একটা প্রশ্ন এসেই যায়। সেটি হলো নীলিমা উদয়াস্ত কেন রোজ কাঁপে? এর উত্তরও আমরা পেয়ে যাব কবিতাটিতেই। এক পঙ্ক্তি পরেই তিনি বলছেন ‘যমুনার দুরন্ত প্লাবন’। এ কীসের ইঙ্গিত? যৌবনের নয় কি? তা যদি না হয় তাহলে কেন তিনি লিখলেন, যদি মত্ত টানে যমুনার দুরন্ত প্লাবন/ সমুদ্রতরঙ্গতটে মুক্ত করে সমস্ত নিখিল?’
‘আমার প্রতীক্ষা’। আলোচ্য বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম। এই শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট ৭টি কবিতা। এর মধ্যে ‘আমার প্রতীক্ষা’ ও ‘ছিন্নপত্র ১৯৬৭’—এই কবিতা দুটি ১৯৬৭ সালে লেখা। অর্থাৎ এ কবিতা দুটিকেও তিনি বাতিল করেছিলেন। ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। আর বাকি ৫টি কবিতা? এগুলোর সবকটিই ১৯৭৮ সালে লেখা। অর্থাৎ মাঝের দশ বছর তিনি কবিতা লেখেননি বা লিখলেও সেগুলোকে মুদ্রিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন, খুব স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগে ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ পর্বের পরবর্তী পর্যায়ে কেমন ছিল তাঁর কবিতা। আসুন, একটি কবিতা পাঠ করি:
আসলে লাগছে না কিছু ভালো
এই সেই প্রাচীন বিরক্তি
মন চাইছে একটা কিছু হোক
কতকাল বন্ধ রক্তারক্তি
যতই লন্ঠন কেন জ্বালো
আসলে তো বুকেরও ভিতর
লোডশেডিং, মাথার ভিতরও
লোডশেডিং রাত্রি-দ্বিপ্রহর
আজ সর্বাত্মক বিবমিষা
বিবমিষা বাহিরে ও ঘরে
বিবমিষা বইয়ের আলমারি
বিবমিষা মুদ্রিত অক্ষরে
বিপ্লবও কি চরিত্র বদলাল
—ভ্রান্তিবিলাস
কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় কবি রহস্যম্যতা, ইশারা ও সংকেতের পথ পরিত্যাগ করে সরাসরি কথা বলতে চাইছেন। কবিতাতে আসছে সময়ের চিহ্নও। এই যে সরাসরি কথা বলা—এই প্রবণতা শুধু যে এ কবিতাতে দেখব, তা নয়, ‘স্মৃতি বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে অল্পবিস্তর তিনি যে লেখালেখি করেছেন তার সিংহভাগ কবিতাতেই দেখা যায় এই গুণ।
‘আরোগ্যের দিকে যাত্রা’। ‘ইষ্টিপত্র এবং অন্যান্য’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট ৫টি কবিতা। কবিতাগুলি ২০০৪-এর মার্চ ১৫-২৬-এর মধ্যে লেখা। ওই সময় যুগান্তর চক্রবর্তী ভিআইপি অ্যাপেক্স নার্সিং হোমে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি ছিলেন। কবিতাগুলো তিনি বলে গেছিলেন এবং এগুলো অনুলিখন করেছিলেন কবির সহধর্মিণী শিপ্রা চক্রবর্তী।
এক্ষণ-সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যকে নিয়ে তিনি একটি এলিজি লিখেছেন। ‘নির্মাল্য এলিজি’। এই ছড়াধর্মী কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে তিনি তাঁর সেই অক্ষমতার থিয়োরির কথা লিখেছেন।
না, নির্মাল্য, বিপন্নতা নয়
আমার লেখা ও না লেখার
সমূহ কারণ অক্ষমতা—
কিন্তু এই আত্মকথা থাক।
এই কবিতাগুলো তিনি যখন লিখছেন তখন তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হোমে ভর্তি। এ অবস্থায় লেখা কবিতার মধ্যে অসুস্থতার কথা থাকবে না, মৃত্যুর অনুষঙ্গ থাকবে না, তা তো হতে পারে না। হয়ওনি। প্রথম কবিতাটিতেই মৃত্যুচেতনার কথা আছে কিন্তু তা খুব সরাসরি নয়। কীভাবে? আসুন প্রথম স্তবকটি দেখি।
এভাবে দূরত্ব শুরু হয়
এভাবে দূরত্ব বাড়ে দ্রুত
জানি এ-তো কাঞ্চন-প্রসূত
তিনি শুধু একাই অক্ষয়
এরই মধ্যে গুপ্ত সরীসৃপ
অমঙ্গল ডেকেছে টিকটিকি
এরই মধ্যে তবু ময়নাদ্বীপ
হোসেনের গান আছে ঠিকই
কাজ আর দায়িত্বে ভরপুর
আজও চলে শশীর সংগ্রাম
এসব কি কিছু ছাপা নাম
জেগে ওঠে ছোটবকুলপুর
যাত্রী শুধু নেই একজন
নেই? আছে ক্ষমাহীন নাম
স্বতাধীকারীরা পায় দাম
যা হারায়—মানিক্য-রতন
মূল্য পায় পাঠক খানিক
আর পায় গুপ্ত আন্দোলন
অন্তঃস্রোত-বাহিত জীবন
বিদ্যুৎ চমকায় দিকবিদিক
তিনি ছাড়া আজও বৃথা জয়
একা তিনি এখনো অক্ষয়
কবিতাটিতে এই যে বলা হলো ‘একা তিনি এখনও অক্ষয়’—এই ‘একা তিনি’ কে? তিনি কি ঈশ্বর? নাকি মৃত্যু? নাকি সুন্দর? খুব স্পষ্ট নয়। তবে এই কবিতাটি কোনোভাবেই একমাত্রিক নয়। এমনও হতেই পারে এই ‘একা তিনি’ একইসঙ্গে ঈশ্বর ও মৃত্যু।
মৃত্যুর যে একটা ইঙ্গিত আছে তা কবিতাটিতে ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলো অনুষঙ্গ থেকে স্পষ্ট। ‘এভাবে দূরত্ব শুরু হয়/ দূরত্ব বাড়ে দ্রুত’, ‘গুপ্ত সরীসৃপ’, ‘অমঙ্গল ডেকেছে সরীসৃপ’, ‘যাত্রী শুধু নেই একজন নেই?’, ‘বিদ্যুৎ চমকায় দিগ্বিদিক’, ‘একা তিনি এখনও অক্ষয়।’ —এইসব শব্দচিত্র থেকে অনুমান করা যায় এ কবিতা মৃত্যুচেতনা থেকে লেখা।
এই পর্বের আরেকটি কবিতার কিছু অংশ পড়ব, যেখানে অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে। কবির কাছে অসুস্থতা আরোগ্য দর্শন হিসেবে এসেছে। কবিতাটির নামও ‘আরোগ্য দর্শন’।
অসুস্থ থাকলেই ভালো থাকি
আমার অসুস্থ থাকা চাই।
কষ্টে শ্বাস টেনে বুঝি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস
রীতিমতো এখনও চলছেই
শ্বাসকষ্ট ছাড়া তবে কীভাবে বুঝব?
শরীরে অঙ্গার বাড়ছে, অঙ্গারের গাঢ় অন্ধকার
সে কি শুধু আমার একার?
ঘরে-বাইরে পৃথিবীর সর্বত্র অঙ্গার, জমছে ছাই—
অম্লজান চাই!
সেও নয় আমার একার
পৃথিবীর চাই অম্লজান।
অম্লজান অর্থাৎ অক্সিজেন একজন সিওপিডি পেশেন্টর অত্যন্ত জরুরি একটি পদার্থ। কিন্তু তা কি শুধুই কবির প্রয়োজন? পৃথিবীর নয়? ‘ঘরে-বাইরে পৃথিবীর তো সর্বত্র অঙ্গার, জমছে ছাইও’। আর তা ছাড়া কবির শরীরে যে অঙ্গার বাড়ছে, অঙ্গারের গাঢ অন্ধকার সে কি শুধু কবির একার?
‘ইষ্টিপত্র’। এই শেষ পর্বে রয়েছে মোট ১১টি কবিতা। কবিতাগুলির রচনাকাল ২০০৪-২০০৫। এই পর্বের অধিকাংশ কবিতাই সরাসরি লেখা। কবি কোনো কুহক বা রহস্যময়তার ভেতর লুকোচুরি খেলেননি। ইচ্ছাপত্রে যেমন ঘোষণা থাকে তেমন কিছু ঘোষণা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:
‘দীর্ঘ হোক ক্ষুধার বিরুদ্ধে/ মানুষের আজন্ম সংগ্রাম কিংবা আমাদের জন্মদিন নেই/ আমাদের মৃত্যুদিন আছে/ আমাদের মৃত্যুর খবর/ ছাপা হয় না দৈনিক কাগজে।’
কিন্তু ‘ইষ্টিপত্র’ নামের যে কবিতা সেটি পড়ে মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। নিজের বিরুদ্ধে এতখানি ক্ষোভ ও ঘৃণা সচরাচর একজন কবির ভেতর দেখা যায় না। আসুন, দেখি তা কেমন।
ভালবাসার চেয়েও অধিক ঘৃণায়
এখন আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি মুখ
ও মুখ আমি দেখব না আর, না
এই যে ও মুখ-এর কথা বলা হলো এই মুখ কার? শত্রুর কি? কবিতাটি আর কিছুটা এগোলে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায়, এই মুখ, অন্য আর কারোর নয়, কবির নিজের। এত দিন ধরে তিলে তিলে যে মুখ গড়ে উঠেছে, যে অর্জন তিনি করেছেন, তার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ, তাই তিনি অতীতের মুখ আর দেখতে চান না। এখানে লক্ষণীয়, ‘ও মুখ আমি আর দেখব না’ বলে কবি বাক্যটি শেষ করছেন না। কমা দিয়ে যোগ করছেন আরেকটি শব্দ। ‘না’। অর্থাৎ দেখব না ভাবটিকে তীব্রতর করা হলো। এবার কবিতাটির শেষ তিনটি বাক্য পাঠ করি।
চূর্ণবুক আমার এ-আয়না
আমার থাক আমার যত ঘৃণা
আমার থাক আমারই কান্না।
কবিতাটিতে বারবার নিজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার পাশাপাশি শেষ বাক্যে আমরা দেখলাম ‘আমার থাক আমারই কান্না’। এখন প্রশ্ন, কেন এই কান্না? আমার ধারণা সম্ভবত কবি মনে করছেন একজন কবি হিসেবে, একজন স্বামী হিসেবে, একজন বাবা হিসেবে, সর্বোপরি একজন নাগরিক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার জন্যই নিজের প্রতি ঘৃণা। আর কান্নাও ওই একই কারণে।
‘এপিটাফ’। এ-বইয়ের শেষ কবিতা। তবে কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৯৭৯ সালে, ‘স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি’ গ্রন্থটি বের হওয়ার কিছু পড়ে। আসুন, কবিতাটি পাঠ করি:
সমস্ত লেখার পরও বাকি থেকে যায় শেষ লেখা
যা লেখে সকলে, তাই কিছু পৃষ্ঠা থেকে যায় বাকি—
শিরোনামহীন কিছু সাদা পাতা,
…………………..স্বাক্ষরবিহীন।
সব কবিতারও পর বাকি থাকে একটি কবিতা
যা লেখে অজ্ঞাতনামা কবি এক—
অগ্নি
…….জ্বলে
………..বল্কলে
…………….শিলায়।
যেকোনো কবিরই কি এপিটাফ নয় এই কবিতাটি? প্রকৃত কবির পক্ষে শেষ লেখা বলে কিছু হয় না, তাই সব লেখার পরও বাকি থেকে যায় শেষ লেখা। এই লেখা লেখেন কে? কবি নিজে? না, তাঁর সে ক্ষমতা নেই। তাহলে? কে লেখেন সেই শেষ লেখা? লেখেন সকলে। অর্থাৎ পাঠকেরা। আর সব কবিতার পর বাকি থাকে যে একটি কবিতা সেটা লেখেন কে? সেটি লেখেন অজ্ঞাতনামা কবি। অজ্ঞাতনামা কেন? প্রকৃত কবিরা ছাপাছাপির জগৎকে বিশ্বাস করেন না তাই চিরকাল তাঁরা থেকে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু একমাত্র তাঁদের পক্ষেই শেষ কবিতাটি লেখা সম্ভব। আর তা হলেই ‘অগ্নি জ্বলে বল্কলে ও শিলায়’। এইখানে বলা বাহুল্য অগ্নিতে যেমন সবকিছু ধ্বংস হয় তেমনি অগ্নিতে পরিশুদ্ধও হয় সবকিছু।
যুগান্তর চক্রবর্তীর ‘কবিতাসংগ্রহ’ গ্রন্থে একটিই সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করেছি। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৭। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন গৌতম বসু ও সুদেব বকসী। সাক্ষাৎকারটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন যুগান্তর চক্রবর্তীর স্ত্রী শিপ্রা চক্রবর্তীও। যাঁর আরেকটি পরিচয় তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো মেয়ে। এই খোলামেলা ও দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘তিরপূর্ণি’ পত্রিকার বইমেলা ১৯৯৮ সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র যুগান্তর চক্রবর্তীর অনেক অজানা দিগন্ত জানা যাবে, তা নয়, তাঁর কবিতার বিস্তৃতি ও ব্যাকরণ অনুধাবন করতেও সুবিধা হবে ভেবে গ্রন্থিত করা হয়েছে।
৬.
যেহেতু যুগান্তর চক্রবর্তী লিখেছেন কম, ভেবেছেন অনেক বেশি, সেহেতু তাঁর ভাবনার সব স্তর লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেইসব অজানা ভাবনার স্তরকে কি কোনো দিন উদ্ঘাটন করা সম্ভব? যেহেতু যুগান্তর চক্রবর্তী প্রয়াত সেহেতু তাঁর লেখা কবিতা ছাড়া তাঁর চিন্তা-চেতনাকে জানার একটিই রাস্তা খোলা আছে। সেটা কী? সেটা হলো, বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার। অনেকগুলো সাক্ষাৎকারই তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত যুগান্তর চক্রবর্তীর ‘কবিতাসংগ্রহ’ গ্রন্থে একটিই সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করেছি। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৭। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন গৌতম বসু ও সুদেব বকসী। সাক্ষাৎকারটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন যুগান্তর চক্রবর্তীর স্ত্রী শিপ্রা চক্রবর্তীও। যাঁর আরেকটি পরিচয় তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো মেয়ে। এই খোলামেলা ও দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘তিরপূর্ণি’ পত্রিকার বইমেলা ১৯৯৮ সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র যুগান্তর চক্রবর্তীর অনেক অজানা দিগন্ত জানা যাবে, তা নয়, তাঁর কবিতার বিস্তৃতি ও ব্যাকরণ অনুধাবন করতেও সুবিধা হবে ভেবে গ্রন্থিত করা হয়েছে।
‘তিরপূর্ণি’ পত্রিকার ওই সংখ্যাটি দিয়ে সাহায্য করেছেন সুদেব বকসী। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অপর দুটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল ‘কবিসম্মেলন’ ও ‘গান্ধার’ পত্রিকায়—সে দুটিও এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে কিছুটা সাহায্য করেছে। সাক্ষাৎকার দুটি জোগাড় করে দিয়েছেন যথাক্রমে শংকর চক্রবর্তী ও তরুণ কবি পৃথ্বী বসু। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটি করার ব্যাপারে এককথায় অনুমতি দিয়েছেন কবিপুত্র ঋজুরেখ চক্রবর্তী। ঋজুরেখ নিজেও একজন কবি, আমাদের বন্ধুজন, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোটো করব না।
বাংলা কবিতার নিবিষ্ট পাঠকেরা যুগান্তর চক্রবর্তীর ‘কবিতাসংগ্রহ’ বইটি গ্রহণ করলে আনন্দ পাব।

জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। পেশা শিক্ষক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : ‘উজাগর আঁখি’ (১৯৯৪), ‘রাত ও রাতের বিভা’ (১৯৯৫), ‘কন্দমূলের আকাশ’ (১৯৯৯), ‘কালপুরুষ’ (২০০০), ‘ভূপাখি ভস্মপাখি’ (২০০৫), ‘দুর্লভ শিখরদেশ’ (২০০৯), ‘অলসরঙের টিলা’ (২০১২), ‘বিবাহের মন্থর আয়োজন’ (২০১৬), ‘অরচিত অন্ধকার’ ( ২০১৯)। সম্পাদিত পত্রিকা : ‘আদম’। সম্পাদিত গ্রন্থ : ‘কমলকুমার মজুমদারের চিঠি’, ‘আমার স্বামী কমলকুমার : দয়াময়ী মজুমদার’, ‘গদ্যসংগ্রহ : গীতা চট্টোপাধ্যায়’, ‘কবিতাসংগ্রহ : সুধীর দত্ত’, ‘কবিতাসংগ্রহ : সমীরণ ঘোষ’। প্রাপ্ত পুরস্কার : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, অহর্নিশ সম্মাননা, ঐহিক সম্মাননা প্রভৃতি।