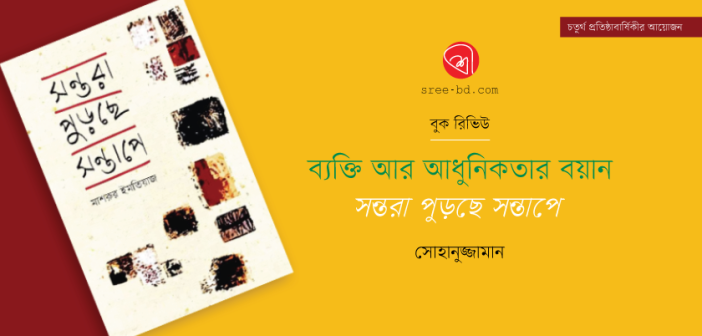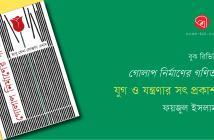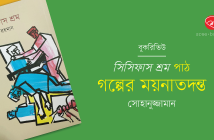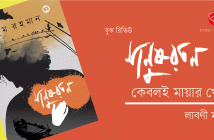আলাপ শুরু করব ‘সন্তরা পুড়ছে সন্তাপে’ (২০২৪) কাব্যের শেষ কবিতা দিয়ে। এটিই সমীচীন হবে, আমার মতে। কারণ এই কাব্যের যে মৌল আকাঙ্ক্ষা আর প্রবণতাসমূহ লুকিয়ে আছে—তা অনেকাংশে নিহিত আছে এই কবিতার ভেতরেই, লুকিয়ে কিংবা বেশখানিক ছাপিয়ে; যেন অপ্রকাশের ভেতরে আরও বেশি প্রকাশিত হয়ে। এই কাব্যের শেষ কবিতাটির শিরোনাম: ‘সন্তরা পুড়ছে সন্তাপে’। এই কবিতাটি এই কাব্যের নামকবিতাও বটে। এই কাব্যের অন্যান্য কবিতার আকার-আকৃতির বিবেচনা-হিসেবে এটি তুলনামূলকভাবে ছোটো কবিতাই বলতে হবে। কবিতা শুরু হচ্ছে কাউকে সম্বোধন করে, ‘প্রিয় মেষ’—এই বাক্যের এক সূচনামূলক অনুকৃতির অসীম ব্যঞ্জনায়। কে এই মেষ? আমি, আপনি, তুমি বা আরও কেউ? না, তার প্রস্তাব পাড়েননি মাশরুর ইমতিয়াজ (জ. ১৯৮৮)। কিন্তু কোনো প্রেমের চেয়ে বিরহের সন্তাপই কি কেবল এই মেষ-সম্বোধনকারীকে বহন করতে হয়? হ্যাঁ। তা কিছুটা করতে হয়। কিন্তু এই কাজটি করা হয় ব্যক্তি-বেদনার ভারবাহী এক চমৎকার রোজনামচায়। এই রোজনামচা কি কাগুজে? না। তারও তো কোনো নির্দেশক তথ্য আমাদের কাছে পেশ করেন না মাশরুর, কবিতায়।
এরপরের স্তবকেই মাশরুর এই ভাব-ভাবনা থেকে বের হয়ে বলেন, ‘পুরাণের দিনে পুণ্য হবে’—মানে নতুন এক লোভের জগতে বিচরণের পূর্ব প্রস্তুতি মাশরুর বেছে নেন। কিন্তু আধুনিক মানুষের মনের আর শরীরে এই সুযোগ কি আর থাকে, শেষমেশ। ধাক্কা একটু পরে তাঁকে খেতেই হয়, পাঠকও খাবেন নিশ্চয়। শুনতে পাই সেই লাগাতার ধ্বনি সুষমার চিৎকার, সৌন্দর্যের মুকুটে হৃদয়ের ক্ষতস্থান ধৌত না করার মতো জটিল আবেশীয় বিষয়। অর্থাৎ আরেহী-পদ্ধতি আনয়ন করে সেই বাস্তবতা, যেখানে মাশরুর বলতে বাধ্য হন, ‘আরোহী বিরহের দিন,/সন্তরা পুড়ছে সন্তাপে…’। কিন্তু ব্যাপারটি একটু গোলেমেলে নয় কি! যে সন্ত, তার আবার থাকছে সন্তাপ! তাহলে তার সন্তাপ কোথায় থাকে? তার পরিচয়ও পাই আমরা। পরিশেষে সমস্ত সন্তাপ রেখে ধুয়ে-মুছে সন্ত উঠে পড়ে এক নতুন ঘরে।

সন্তরা পুড়ছে সন্তাপে
তাহলে এই সন্ত কে? বহুবচনে কারা এই সন্তের দল; যাদেরকে পুড়ে চলতে হয় সন্তাপে? প্রশ্নের পেছনে ভাষিক বাস্তবতার সাথে সাথে একটি পরিপ্রেক্ষিতগত বাস্তবতাও তো থাকে। কবিতা তো নাজেল হয় না আকাশ থেকে, দূর আকাশের মেঘের ভেতরকার বুড়িমার ঘরদোর থেকে। কিংবা কবিতা তো নাজেল হয় না কোনো কস্তুরী কিংখাবের ঝালরের ভেতর থেকে। কবিতা তৈয়ার হয় এই দুনিয়ার ভেতর থেকেই। এবং কবিতার নাজেল হওয়ার বিষয় কস্তুরী কিংখাবের ভেতরে না হলেও কস্তুরী কিংখাবের প্রসঙ্গ কবিতায় আসবে প্রাসঙ্গিকভাবেই। না এসে আর কই যাবে ও? এখন দেখেন, যে প্রস্তাব হাজির করেছি, শিরোনামে, সেই প্রস্তাবের বিচার না করে সামনে এগোনো বেশ দুষ্কর হয়ে ওঠে। ধরুন আমি ‘ব্যক্তি’ ও ‘আধুনিকতা’—এই দুটো শব্দ ব্যবহার করেছি। এই দুটি শব্দ বাংলা কবিতার বিবেচনায় বেশ পুরোনো।
উনিশ শতকে বিহারীলালের কবিতা কিংবা মাইকেলের কবিতাকেও আধুনিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তেমনি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারপরে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের আলোচনায়ও এই কথাই বলা হলো: এঁরা সব আধুনিক! আলোচনার এই আলাপ বেশ গোলমেলে আর বিস্ময়কর তো বটেই! তাহলে কে আধুনিক আর কে ক্ল্যাসিক কিংবা রোমান্টিক তার ধার কেন ধরা হলো না? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া বেশ ভারের মতো ভারবাহী হয়ে উঠবে ক্রমাগত। এছাড়া বাংলাদেশের কবিতায়ও চল্লিশের দশক থেকেই আধুনিক-আধুনিক করে কবিতা-পাড়া মাত করে তোলা হলো। এবং এই আধুনিকতার পাল্টা বয়ানকল্প হিসেবে আনা হলো উত্তরাধুনিকতা পর্যন্ত! কিন্তু এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি চলে গেলরে ভাই! মাশরুর কি এই ধারণাটি বুঝে-শুনেই সামনে এগিয়েছেন। তার আধুনিক আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবিতা নির্মাণের বেলায়?
এটি বোঝাশোনার চেয়ে জরুরি যে, যে বাস্তব প্রেক্ষিত বিবেচনায় তিনি কবিতা রচনা করেছেন, সেই প্রেক্ষিতে তিনি এমন কবিতা লিখবেন, যা হয়ে উঠবে প্রকৃত প্রস্তাবে পরিপার্শ্বের বাস্তবতা। তিনি, বলব, তাঁর সময়, মানুষ, মানুষের সমাজ আর রাষ্ট্রের কবিতা লিখেছেন। তিনি আধুনিক আর তাঁর কবিতা হয়েছে ব্যক্তিক। ব্যক্তিকতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে হয়ে উঠেছে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। আর এই ধারক-বাহক বিষয়ই ব্যক্তিকতার চরমে পৌঁছেছে। হয়ে উঠেছে ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যে ভারাতুর। এই দ্বৈততায় তিনি লিখেছেন এমন কবিতা, ‘সন্তরা পুড়ছে সন্তাপে’। এই সন্তরা কারা? এই একটি শব্দ ‘সন্ত’, যার ভেতর থেকে যে ভাবাদর্শ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভাবাদর্শ চারপাশের বাস্তবতারই চরম আর বাস্তব রোশনাই। জ্বাজল্যমান। প্রকাশিত। বিবেচনাপ্রসূত। যৌক্তিক। ভালো-মন্দের হিসেবে দুটোই। ফলে এই সন্ত কেবল একটি চরিত্র নয়, এ যেন আমাদের চারপাশের লোকজনের মূর্ত বাস্তবতা নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত। এবং এই সন্তু এমন এক সমাজ-রাষ্ট্রে বেড়ে ওঠে আর বড়ো হয়—সেই সমাজ-রাষ্ট্রের অন্দরেই এই সন্তের জন্ম আর বিকাশও সম্পাদিত হয়।
ফলে এই একটি সন্তের ‘সন্তেরা’ হওয়া ব্যক্তি থেকে সামষ্টিকে পৌঁছানোর এক দুর্মর শিকারি-আকাঙ্ক্ষা, এবং লক্ষ্য শিকারি-আকাঙ্ক্ষার শিকারে কামেল। এই সন্তের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই প্রকৃত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় সৃষ্ট বর্তমানের আধুনিকতার বর্তমানময়তায় উৎপন্ন বাস্তবতা। ফলে পূবর্তন সন্ত শব্দের ধ্রুপদী চিহ্নের আর রূপের বিপরীতে বর্তমানময়তায় অভিষিক্ত হওয়া এবং সন্তের ধ্রুপদী অর্থের বিপরীতে বর্তমান বাস্তবতায় ক্রমাগত বিভিন্ন অর্থ তৈয়ারের বিষয়টি একার্থে চমৎকার। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক সমন্বিত সুর বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই প্রকাশিত।
এবার এই কাব্যের প্রথম কবিতার আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। এই কাব্যের প্রথম কবিতার শিরোনাম: ‘পথে’। ক্ষুদ্র একটি কবিতা। তেমন আলাপের বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু একটি নৈরাশ্যবাদী আর শূন্যবাদী ধারণায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে এই কবিতা। যেন কোথাও কিছু নেই, আবার সব আছে কিন্তু যেন আর কিছুই থাকবে না—এমন এক ধাঁধার জগতে থেকে মাশরুর কবিতার আলাপ সারছেন। ঐ যে আগেই বললাম, যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দবাদী বিষয়-আশয় আছে, ‘রঙিন জিপসিরা গান জুড়েছে’ও, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ‘ধুলোহীনতার এলিজিতে’ পরিগণন করতে হয় পাঠকের। কিন্তু এই যে সব পথ শেষ পর্যন্ত ধুলো হয়, এই ধুলোর ঠিকানা নির্মাণের পেছনে কারা কারা আর কী কী থাকে—তাও কিন্তু পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। পাঠক ভাবতে বাধ্য হবেন নিজের সাথে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে। কারণ পাঠক যেকোনো সাহিত্য পাঠের বেলায় নিজের সমান্তরালে মিলিয়ে পাঠ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
মাশরুরের কবিতায় এমন জগৎ আছে, যা পুরোদমে পাশ্চাত্যময়তায় ঠাসা। যেমন দ্বিতীয় কবিতা ‘ডুয়েল’-এ মাশরুর এই কাজ করেন। এমন কাজ তিনি এই কাব্যের আরও কিছু কবিতায় করেন। এই কবিতা ব্যক্তির, যা একরকম মাশরুরের, সিনেমা দেখার ফসল কি? এমন প্রশ্ন চতুর পাঠক করবেন। উচ্চ মাত্রায় ওয়েস্টার্ন-ঘরানার উপন্যাস কিংবা ঝকমারি ওয়েস্টার্ন সিনেমার বাস্তব ছবি এই কবিতায় দৃশ্যত দৃশ্যায়িত হয়েছে। তবে ভাষার নিখুঁত ব্যবহার মাশরুর জানেন। জানেন বলেই এই প্রসঙ্গ ভাষার ভেতর দিয়ে কবিতায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে। এবং সিনেমা কিংবা উপন্যাসের জনারের থেকে বের হয়ে একটি কবিতা হয়ে উঠেছে।
দ্বৈত ধারণার ভেতর দিয়েও মানুষের জীবনের এই অসহায়ত্ব নির্মিত হয়। কবিতা যে ব্যঞ্জনায় কথা বলে, তা তো এখানে বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেটা বলে নিলাম। এই কবিতায় ব্যক্তির সামূহিক অসহায়ত্বের ভার বহনের বর্ণনা যে পদ্ধতি মাশরুর কবিতার জমিনে চালান করেন, সেই ভার বহন করানোর বিষয়টি মাশরুর বহির্জগতের সীমনার ব্যবহারের মাধ্যমেই করেন।
মানুষের অসহায়ত্বের কি কোনো কূল-কিনারা আছে? কোন সময়কালে ব্যক্তি-মানুষ অসহায় ছিল না? মানুষ মাত্রই অসহায়। সেই অসহায়ত্বের জানান সে জন্মের পর থেকেই দিতে থাকে, চিৎকারের ভেতর দিয়ে। এবং এই যে চিৎকারে ভুবন কাঁপানো বিষয়—তা নেহাতই কোনো ঠুনকো বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু জন্মের পর থেকেই মানুষ আশ্রয় খোঁজে। আশ্রয়ের সাথে সাথে সে হয়তো বা আরও কিছু খোঁজে। সময়ের বিবেচনায় এই আশ্রয়ের নানারূপ রূপকল্প থাকে। এক এক সময় মানুষের সহায় হয় এক একজন। তা মানুষ না হয়ে প্রকৃতিও হতে পারে। কিন্তু মানুষ আর প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়েই এই বিষয়টি হয়। তাই মানুষ শত্রু কি মানুষের, নাকি শত্রু প্রকৃতি মানুষের—এই দ্বৈত ধারণার ভেতর দিয়েও মানুষের জীবনের এই অসহায়ত্ব নির্মিত হয়। কবিতা যে ব্যঞ্জনায় কথা বলে, তা তো এখানে বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেটা বলে নিলাম। এই কবিতায় ব্যক্তির সামূহিক অসহায়ত্বের ভার বহনের বর্ণনা যে পদ্ধতি মাশরুর কবিতার জমিনে চালান করেন, সেই ভার বহন করানোর বিষয়টি মাশরুর বহির্জগতের সীমনার ব্যবহারের মাধ্যমেই করেন।
এই কবিতার শুরুতেই ব্যক্তি বলে উঠছে, ‘ডুবে যাচ্ছি চন্দ্রবিন্দু!’—এতোটুকু বলে গেলে তো সমস্যা মিটেই যেত। কিন্তু বাক্য সমাপ্তে পূর্ণচ্ছেদ হিসেবে ব্যবহার করছেন বিস্ময় চিহ্ন দিয়ে! আমরাও বিস্মিত হই? এই বিস্ময়ের বিষয়টি নিয়েই আলাপ করা যাক। দুনিয়ার বেঁচে থাকা আর না থাকার সহায়ের রূপকল্প হিসেবে তিনি ‘অক্সিজেন’ এনে কবিতা সাজান। অক্সিজেন দুনিয়ার উপরিতলে মানুষ সহজেই পায়। কিন্তু জলের নিচে তা সহজলভ্য নয়। তাই এই মানুষ ডুবসাঁতারে নামে অক্সিজেন নিয়ে। কিন্তু সমস্যা হয় পথিমধ্যে, ‘অক্সিজেন সিলিন্ডার আচমকা ফুটো হুট!’ এই সমস্যাটি ডুবসাঁতার আর অক্সিজেন-এর বাইনারিতে ফেললে যে অর্থ তৈরি হয় তা হলো, অসহায়ত্বের সক্রিয়তায় নির্মিত বিপন্নতা। এবং কবিতার শিরোনাম পূর্বোক্ত দুটি প্রত্যয়কে আরও বেশি দৃঢ় করে। ফলে কবিতার শিরোনাম মাশরুর দিলেন: ‘গ্রাস’। যথার্থই হলো।
ভাষা তো ইথারে হারায়। ভাষা জমা থাকে কোনখানে? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। উত্তরের বিষয়টিও খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। কিন্তু ব্যক্তির ক্রমাগত মনোলগের এক দারুণ ঝলমলে প্রকাশ পাওয়া যায় ‘নিছক ভাঁড়ের মতোন’ কবিতায়। প্রকৃতিতে ঋতুর ব্যবহারের বেলায় বাংলা সাহিত্যে কবিতা-জগৎ বেশ রোশনাই ছড়িয়েছে, যেকোনো অঞ্চলের কবিতার বিবেচনায়। কীভাবে? পশ্চিমের ঋতুর যে ঝিম মেরে থাকার প্রবণতা, সেই প্রবণতার বিষয় নানাভাবে এড়িয়ে গিয়ে বিচিত্রতায় ঋতুকে কবিতার পরাণে সিঁধিয়ে দেওয়ার, এবং সিঁধিয়ে দেওয়ার পরেও প্রাণ ফিরে থাকার বিষয়টি কিন্তু জরুরি। বাংলা কবিতার জগতে বিষয়টি করা গেছে। ‘বারমাইস্যার’ মতো ঘটনা অহরহ ঘটেছে। আরও আগে মেঘদূত কাব্যের উদহারণ দেওয়া যেতে পারে। আর বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ—এঁরা এই ব্যাপারে গুরু হয়ে বসে তো আছেনই। তারপরও কেন মাশরুরকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি এক্ষেত্রে?
কারণ মাশরুর সেই ধারাটা রক্ষা করেছেন। কিন্তু কীভাবে? দেখেন শীত তো বাংলাদেশের আবহাওয়া আর প্রকৃতিতে এক দারুণ আমোদপূর্ণ ঋতু। শত রকমের ফুল, মাঠে বিচিত্র ফসলের ঘ্রাণ আর ঘরে পিঠা-পুলির জম্পেশ আয়োজন হয় এই ঋতুতে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে নাগরিকতা, মেট্রোপলিটনের চাপ, কসমোপলিটন যতটুকু হয়েছে তা—এইসব মিলে শীত আর সেই ‘শীত’ নাই। অর্থাৎ পুরোনো শীত নাই হয়ে গেছে। আর আধুনিকতার একটা জোয়ারও বয়ে চলেছে এখনকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রে, বেশ ভালোভাবেই, তা যদিও বিচ্ছিন্নতায়। লোকজন সুইসাইড করছে ধুমধাম; ভুগছে একাকীত্ব আর বিষণ্নতায়—এইসব চিহ্ন আমাদের জানাচ্ছে বিশ-ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ইউরোপের দিকে এক পা হলেও আমরা বাড়িয়েছি। তাই এই বিচার-বিবেচনায় পুরোনো জমানার শীতকে যেভাবে কবিতায় ব্যবহার করা যাবে, সেই বিবেচনায় এই সময়ের বিবেচনায় ব্যবহার সম্ভব নয়। মাশরুর তাই এই কবিতার প্রথমে বলে নেন, ‘শীতরাতে শীত আসে আবেগপ্রবণে,’ এবং একই লাইনের কমার পরে দ্বিতীয় অংশে বলেন, ‘শবাগারে ঘ্রাণ নেই মোটে।’ অর্থাৎ পশ্চিমের ব্যক্তির বিকাশ আর প্রকাশকে ঘিরে ‘আধুনিকতাবাদী’ কবিদের যে আবেগহীন আর জঙ্গমতায় ভরা কবিতার মতোও এই কবিতা হয়ে ওঠে। আর এই যে ঘটনা ঘটল ব্যক্তির অন্তর্জগতের ভাবনা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তার বিষয়ও স্পষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কবিতার বিষয় নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। শিরোনাম: ‘নরসুন্দর’। এই কবিতা তো আমাদের কবিতার মূর্ত আর বিমূর্ততা সম্পর্কে ধারণা দেয়। দৃশ্যের বাস্তবতা কোনো নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নয়। দৃশ্য কবিতার বেশ জুতসই বিষয় হিসেবেই ধরা দেয়। এবং মূর্ত আর বিমূর্ততার ভেতরেই নির্মিত হয় ব্যক্তি ধারণাটি।
আধুনিক সময় বা যুগ ব্যক্তি নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বশীল জায়গা ধরে রাখে। ব্যক্তি আধুনিক সময়কালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও হবে। এই ব্যক্তিকে আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিবেচনায় আমাদের পাঠ করতে হবে, তা কবিতা কিংবা অন্য যেকোনো বিবেচনার বেলায়ও। ব্যক্তি যদিও আত্মানুভূতির বিবেচনায় নির্মিত হয়। ভাববাদের খণ্ডন বিষয়ে যুক্তিবাদের উদ্ভব-বিকাশের আলাপ জরুরি হয়ে পড়বে এক্ষেত্রে। ব্যক্তি যে নিজে নিজের আলাপ করে, এটি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচিত হতে পারে। মানে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক বিষয় আরকি। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি যে নিজের মতো করে ভাববাদী আলাপ তোলে, সেটি আবার নির্মাণের জন্য ব্যক্তির যে অন্তর্জগৎ প্রয়োজন, তা সৃষ্টির পশ্চাতে বহির্জগৎও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যে কারণে ভাববাদ আর বস্তুবাদ—এই দুই ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়েই ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। ফলে আমাদের বলতে বাধ্য হতে হয় যে, ভাববাদী আর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়গত ধারণায়, কিংবা আলাদা আলাদাভাবেও ব্যক্তির বিকাশের পেছনে সমাজ একটি বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। ‘বায়োপিক’ এই ধারণায় পড়া যেতে পারে। এই কবিতা আমাদের এই বিবেচনায়ই পড়তেও হবে। ব্যক্তিকে এই কবিতায় ‘জাদুকর’ কিংবা ‘জুয়াড়ি’ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। যে জুয়াড়ি কিংবা জাদুকর তার নিজস্ব কর্মকৌশলের ভেতর দিয়েই তার সমস্ত কর্মকাণ্ড সমাধা করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু অন্তর্জগতের নির্মাণে বহির্জগতের যে চাপ, সেই চাপের বিষয়টি নানা কারণেই আটকে থাকে অন্তর্জগতের নির্মাণ-অনুষঙ্গে।
কিন্তু তারপরও ‘ইন্ডিভিজ্যুয়াল আইডিয়োলজির’ সমর্থনে ক্রমশই এক ব্যক্তিই যেন আমার দু’চোখের সামনে স্পষ্ট হয়। এইটাই ব্যক্তির বায়োপিক, মতান্তরে মাশরুরের বায়োপিক; আর আরও বৃহৎ অর্থে এই সময়-সমাজের বায়োপিক।
ফলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এমন সব আশ্রয়ীর ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, সেই আশ্রয়ী আবার নির্দিষ্ট সমাজ-রাষ্ট্রের ‘আমজনতার’ ক্ষেত্রে একটি সমস্যামূলক বা অপরিচিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। ফলে আমরা ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও অসমর্থ হই। কবি হিসেবে মাশরুর এই অসমর্থতাকে সমর্থতায় পর্যবসিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, ‘সুপেয় জলসহ ব্ল্যাকগ্রেপ জ্যুসে মিশে যায়,/বরফ টুকরো আর লঘু অপলাপ।/সব মুছে যায়,/শুধু ফুটে ওঠা কোনো মানুষের মুখ—/অ্যান্টিক টাইপরাইটারের লেখা পরিচয়পত্র এক।’ এই পরিচয়পত্র যে ব্যক্তির জন্য নির্মিত হলো, তা কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তি তৈরি করে দিল? এমন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বেশ দুষ্কর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপরও ‘ইন্ডিভিজ্যুয়াল আইডিয়োলজির’ সমর্থনে ক্রমশই এক ব্যক্তিই যেন আমার দু’চোখের সামনে স্পষ্ট হয়। এইটাই ব্যক্তির বায়োপিক, মতান্তরে মাশরুরের বায়োপিক; আর আরও বৃহৎ অর্থে এই সময়-সমাজের বায়োপিক।
এই বায়োপিক থেকে মানুষের মুখ খুঁজতে গিয়ে মাশরুর তাঁর পরবর্তী কবিতা ‘নদীমুখে বসে’ কবিতায় মানুষের সমান্তরালে প্রকৃতিকে হাজির করেন। কিন্তু পুরো কাব্যেই দেখা যাচ্ছে যে, পাঠক দেখবেন, মাশরুরের কবিতা অতিমাত্রায় যান্ত্রিক। তাঁর কবিতার ভাষায় আবেগ-অনুভূতির বিপরীতে এই যান্ত্রিক প্রণোদনা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যেন। এবং কবিতার যে অন্যতম উপাদান প্রকৃতি, একার্থে মাশরুরের কবিতায় তা খারিজ হয়ে যায়। মাশরুর কেন এই কাজ করেন? ব্যক্তিজীবনের প্রভাব বোধহয় মাশরুরের এই প্রক্রিয়ায় অন্তঃস্থত করতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও, আমি বলছি, নেতিয়ে-চুরিয়ে হলেও মাশরুর তাঁর কবিতায় দুই-একবার হলেও প্রকৃতির শরণাপন্ন হয়েছেন। নদী আর মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণ এবং এই সম্পর্ক জায়েজ করার জন্য হলেও তিনি তা ব্যবহার করেছেন। উপরিউক্ত ধারণায় ‘আমাকে বলছি’ কবিতাটিও ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে পাঠ করা সম্ভব। এবং ব্যক্তির সাথে প্রেম ওতোপ্রোত সম্পৃক্ত বিষয়—এই হলো এই কবিতার বিষয় আর সুর। ‘আঠারোর পরে’ শিরোনামের কবিতা ব্যক্তি ও আধুনিকতার সমন্বয়ে নির্মিত প্রেমভাবনা বিষয়ক কবিতা। এই ব্যক্তিগততা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে এমন আরও কিছু কবিতা হলো: ‘যা কিছু আছে, ছিলো, অথবা নেই’, ‘ফেরারি ফুলের মতোন’, ‘বড়ো হয়ে’।
নিহিলিজমের জনক হিসেবে বিবেচিত হন ফ্রেডরিখ নিৎসে। কিন্তু এর আগে পরে এই ধারণা নিয়ে আরও অনেকেই কাজ করেছেন। নিহিলিজমের কেন্দ্রীয় ধারণার মধ্যে অন্যতম হলো: জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণাকে প্রত্যাখ্যান, দুনিয়ার পরম সত্যের ধারণাকে খারিজকরণ, সমাজ-রাষ্ট্র থেকে পলায়নপর মনোভাব, অস্তিত্বহীনতায় নির্মিত দুঃখবাদ এবং এই সব ছাপিয়ে মানুষের চূড়ান্ত বেখেয়ালী স্বাধীনতা। এই ধারণা ভাববাদী না বন্তুবাদী—তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা কম হয়নি। এই নিহিলিজম-এর ধারণা এখনকার নতুন সময় ও সমাজের ধারণা হিসেবেও পাঠ করা সম্ভব। ‘তুচ্ছ এক সন্তান’ শিরোনামের এই কবিতায় প্রখর নিহিলিস্টিক ধারণার বাতাবরণ লক্ষণীয়। উদাহরণ: ‘এপ্রিল শেষে মে, জুনে ফুটন্ত ফুল কিংবা ঝরে যাবে কেউ/তুমি সময়ের পিছু আছো—শুধুই সপ্তাহান্তের ছুটির দিনে’। তবে শেষ পর্যায়ে রোমান্টিকদের মতো আশা জিইয়ে রাখার এক দারুণ ব্যর্থ কসরত মাশরুরকে করতে দেখা যায়। এই কাব্যের সামূহিক প্রবণতার বিবেচনায় বিষয়টি বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই হাস্যকর ঠেকবে। দেখুন উদাহরণে: ‘তুমি এইক্ষণে জানো, জেনে রাখো, জানবেই—/ব্রহ্মাণ্ডের তুচ্ছ এক সন্তান তুমি নও,’।
প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত এই যুগে বিজ্ঞান-টিজ্ঞান নিয়ে নানা রকম গল্প বার-বার বলা হচ্ছে মানুষের এই সমাজে। মানুষ দৌঁড়াচ্ছে শিংওয়ালা হরিণের মতো, কিন্তু কোথায় তার শেষ? মানুষ এতো দৌঁড়ে কোথায় যায় শেষ পর্যন্ত? বা মানুষের কীইবা হয় শেষ পর্যন্ত? পরিবার আর আরও আরও সমাজ সংস্থার যে নিয়মনীতিও তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুতে পৌঁছায়! কিংবা ব্যক্তির সবচেয়ে কাছের সম্বন্ধ পরিবারের বিষয়টিও এক পর্যায়ে ব্যক্তির কাছে বিচ্ছিন্নতার নাম হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই বিষয়ও ভার হিসেবে ব্যক্তিকে নিতে হয়। পরিবারে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মরে গিয়ে নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমে শেষ পরিণামে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বিষয় বেঁচে থাকা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির জন্য দুঃসহ স্মৃতি আর ট্রমার নির্মাণ করে দেয়। ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দুঃসহ স্মৃতি আর ট্রমা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ‘শিশুশিক্ষা’ এই ধারণাকে নিয়ে লিখিত কবিতা। এই কবিতার ‘মনোমুগ্ধকর বাক্য’ একটিই, ‘বড় হয়ে গেলে, মানুষ গলার কোমলতা হারায়,’—এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আধুনিক ব্যক্তি মানুষের নিয়তি সম্পর্কে আর কী হতে পারে!
মাশরুরের এই কাব্যে ম্যাক্সিম ঘরানার কিছু কবিতা আছে। ম্যাক্সিম কম কথা বলে একটি বৃহৎ অনুভূতি কিংবা ভাবনা প্রকাশের ভালো আর জুতসই কবিতা নির্মাণ-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি জারি থেকেছে ‘কুসংস্কারসমূহ’ শিরোনামের কবিতার ভেতরে। এই কবিতার ভেতরে আবার ছোটো-ছোটো ম্যাক্সিমের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। মানে বড়ো কবিতা নির্মিতি হয়েছে অনেকগুলো ম্যাক্সিমের মাধ্যমে। উদাহরণ: একটি ম্যাক্সিমের, ‘কালো বেড়াল দেখে বিপদ আসবে বলে, বেড়ালটা কী মারটাই না খেলো।’—এই এক লাইনকে দুনিয়ায় বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর নির্মমতার এক বিশদ বাণীরূপ হিসেবেই আমি বিবেচনা করব। বেড়াল কেবল বেড়াল নয়, কালো বেড়াল হয়েছে। এই কালো বেড়াল সম্বন্ধে সমাজের মানুষের যে ধারণা, সেই ধারণার ভেতর দিয়ে কালো বেড়ালের ভয় মূলত নিপীড়নের ভাবাদর্শিক পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি মানব সমাজের বিবেচনায়ও বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। রাষ্ট্রের নানারূপ নিয়মনীতি তো কালো বেড়াল দেখার মতো কুসংস্কার। ফলে কালো বেড়াল নিছক কুসংস্কারের কারণে মানুষের সমাজে পশু হিসেবে নিপীড়নের শিকার হয়। একইভাবে সমাজের ভেতরে নানা শ্রেণির মানুষকেও এই ধারণার ভেতরে অবস্থান করেই নিপীড়িত হতে হয়। কিন্তু কালো বেড়াল সম্পর্কিত কুসংস্কারের কারণে তাদের কিছুই করার থাকে না।
এই কাব্যের একটি দারুণ কবিতা হিসেবে আমি বিবেচনা করি ‘এটিএম বুথ’ নামের কবিতাকে। এই কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিতাও এটি, আমি মনে করি। এই কাব্যের অসংখ্য কবিতায় চরিত্র আছে। তা অবশ্যই কথাসাহিত্যের চরিত্রের মতো নয়। আর এক্ষেত্রে কবিতার চরিত্র যে একটু ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপিত হয়, সে কথা বাড়িয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়। চতুর পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারেন, আধুনিক কবিতায় চরিত্র মানেই কবি প্রায় একাই নিজের মতো করে প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই কবিতায় চরিত্র কোনো ব্যক্তি নয়। দুনিয়ার প্রাণহীন বস্তু হয়ে উঠেছে চরিত্র। প্রাণহীন বস্তু হিসেবে সমাজে সক্রিয়তায় ক্রীড়নকের ভূমিকায় টাকা উত্তোলনের আধুনিক যন্ত্র এটিএম বুথ। একটা মানুষ এটিএম বুথে টাকা তুলতে যাওয়ার মতো সামান্য মুহূর্ত এই কবিতার মূলাংশ। কিন্তু দেখুন, শব্দগুলো, ‘ওহী আসে’; কোথায় আসে? আসে ‘মুঠোফোনে’। কিসের ওহী? ওহী তো অলৌকিক বিষয়। কিন্তু ওহী শব্দের ব্যঞ্জনায় বর্তমান প্রযুক্তির বাড়-বাড়ন্ত বিষয়কে উপস্থাপন দারুণ বিষয়ই বটে। আর এই যে ব্যক্তি কচুরিপানা পেরিয়ে বুথে যায়, সেও এই রাষ্ট্রিক সিস্টেমের দাস। এক কথায় আধুনিক মানুষের দৈনন্দিনতা এবং এর সাথে প্রযুক্তির মিশেলে যে এক নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, তা পষ্ট করেন মাশরুর। কিন্তু ঘামে ভেজা জামা পরা রিকশাওয়ালার কী হবে এই রাষ্ট্রিক সিস্টেমে? মাশরুর এই প্রশ্ন তোলেন না। কিন্তু আবার তোলেন। তাহলে মেট্রোপলিটন, নাগরিকতা, আধুনিক, আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ আর কিছু পর্যায়ের হলেও কসমোপলিটন—এই সব মিলে যে পরিস্থিতি বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে, সেই প্রক্রিয়ায় কারা আছে আর কারা নেই, এই প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। এবং একটি বর্তমানময়তা আর সর্বমনস্কতার বিষয় আগাপাশতলা বিবৃত না হয়েও আরও বেশি ব্যঞ্জনার ঘনঘটায় বিবৃত হয়েছে।
ইতিহাসের যে সময়-পর্যায়ে রাষ্ট্র বিষয়টি নির্মাণের কাল্পনিক বাস্তবতা তৈরি হলো, সেই সময়ে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিষয়ের মতো অর্থ ও আর্থ-উৎপাদন বিষয়ক ধারণাও এক নতুন মাত্রা পেলো। ‘মুদ্রা’ শীর্ষক কবিতায় আর্থ-উৎপাদন ও আর্থ-উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নানা বিষয় একত্রিত হয়েছে। কিন্তু মাশরুরের এই কবিতায় অর্থ বিষয়ে মুদ্রা শব্দটি কোনো আর্থ-উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়ের সাথেই কেবল সংশ্লিষ্ট থাকেনি। বরঞ্চ মুদ্রার নিরিখে আধুনিক মানুষের জীবন আর জীবনের বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রা প্রসঙ্গ টেনে আধুনিক মানুষের নির্মম নিয়তি প্রসঙ্গই বিশেষ হয়েছে এই কবিতায়। মুদ্রার উল্টোপাশের নিয়মনীতি নানা কারণে মানুষের সাথেই স্পষ্ট করা হয়েছে। এবং মুদ্রার উল্টোপাল্টা হওয়ার রূপকল্পে মানুষের জীবনের পরিবর্তনের বিষয়ও স্পষ্ট হয়েছে।
আপনি আধুনিক হবেন আর সুইসাইড করতে চাইবেন না—এটি কেমন করে হবে! হ্যাঁ, মাশরুর এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিয়েছেন। আধুনিক সমাজের ব্যক্তি মানুষ তার বহির্জগতের চাপে তটস্থ থাকে সর্বদা। স্থিরতার মতো বিষয় কৃষি সমাজের মানুষ যেভাবে ভোগ করতে পেরেছিল—এই বিষয়টি আধুনিক সমাজের ব্যক্তি মানুষ একেবারেই করতে পারে না। ফলে আধুনিক মানুষের দুয়ারে ‘বর্ডার লাইন পরিস্থিতি’ উপস্থিত হয়। এবং এর ভেতর দিয়েই আধুনিক মানুষকে যেতে হয়, এই পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ই পরিস্থিতি যে কাউকে সুইসাইডাল করতে পারে। ঘটতে পারে সুইসাইডের মতো ঘটনা। এই কারণে আগের যে ব্যক্তি নির্মাণের প্রকল্প হিসেবে মাশরুর কিছু কবিতা আমাদের সামনে হাজির করেন, তদ্পরবর্তী কবিতা হিসেবেই এই কবিতাকে বিবেচনা করতে হবে। যেমন একাংশে কবি বলছেন, ‘আমি/ডানমুঠোয় রিভলবার নিয়ে, ডানমুখ বুজে—মাথার ভেতর পৃথিবী নামের/যন্ত্রটাকে দ্যুম শব্দটা শুনিয়ে দিলাম।’
এবার এই কাব্যের ভাষা বিষয়ে কিছু আলাপ করা যাক। কারণ মাশরুরের এই কাব্যের ভাষার বিষয় নিয়ে আলাপ না করলে এই কাব্যের আলাপ সমাপ্ত হয় না। মাশরুরের এই কাব্যের ভাষা প্রথমতই ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কাঠামোবাদী আর উত্তর কাঠামোবাদী—এই দুই ধারণাসমূহের ভেতরে একটি সমন্বয় সাধন করেই সামনে আগ বাড়িয়েছে। ধরুন এক্ষেত্রে একটু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রাচীন যুগের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম চর্যাপদ। কিন্তু চর্যাপদের ভাষা এখনকার মতো বাংলা নয়। কিন্তু সেই ভাষাকেও বাংলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আবার মধ্যযুগের বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। এবং উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের এই পর্যন্ত বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের বিবেচনার বেলায় দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা একই ধারায় পরিবর্তন হতে থেকেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের বিষয়টি ঘটেছে ক্রমাগত মানুষের সমাজের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু যে আলাপ করা হলো, সেই আলাপটি কেবল সাহিত্যের ভাষার আলাপ নয়। এর ভেতরে ভাষার কেজো বিষয় নিয়েও আলাপ করা হয়েছে। ফলে সাহিত্যের ভাষা, আর ভাষার কেজো রূপের জন্য ভাষা—এই দুটি ধারণার ভেতরে পার্থক্য রয়েছে।
মাশরুরের কবিতা আলোচনায় ভাষা বিবেচনায় আমাদের সাহিত্যের ভাষা বিষয়েই আলাপ করতে হবে। কিন্তু মাশরুর যে ভাষা তাঁর কাব্যের কবিতাসমূহে ব্যবহার করেন, সেই ভাষার নির্মাণে আবার সমাজের একটি বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে, সেটা স্বাভাবিকভাবেই থাকে আর থাকবেও। এই বিষয় এড়িয়ে চলার বিষয় হতেও পারে না। কিন্তু এই নতুন সমাজে মেট্রোপলিটন নির্মিত ভাষাবৈশিষ্ট্য বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আবার একটি কেন্দ্রীয় শাসানুবর্তী ভাষাও তাঁর কাব্যের ভাষা হয়েছে। পাঠক যদি মাশরুরের কবিতার ভাষা দেখেন, তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে, মাশরুর বাংলা ভাষার কাঠামোবাদী ভাষা ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন মাশরুর, যেমন: গিমিক—গিমিক শব্দের উৎপাদিত অর্থের ভেতর দিয়ে মানুষের সমাজে পণ্যায়নের এই যুগের যে বাস্তবতা মাশরুর পষ্ট করেন, তা এক কথায় দারুণ। আবার এই একই কবিতায়, ‘সমায়িক গিমিক’, ‘স্ট্রিপটিজ পোস্টার’ শব্দগুচ্ছ নারীবাদী জমানায় নারীবাদের প্রধানতম কার্ভগুলো ভেঙে যেন কীভাবে নারীকেই পণ্যায়িত করে ফেলে। আর মাশরুরের কাব্যের কবিতাসমূহে এমন নতুন নতুন শব্দের ঝকমারি প্রকাশ অহরহ ঘটছে। যেমন, ‘ডুয়েল’, ‘বিউটিবোন’, ‘ফেইডেড’, ‘স্ল্যাং’, ‘রিস্টার্ট’, ‘সিনেম্যাটিক’, ‘আমিউজিয়ামে’, ‘দ্য ডার্ক অ্যালি’, ‘পাঞ্চ’, এটিএম বুথ’, ‘স্টারি নাইট’, ‘সেরেনাটায়’—এমন আরও অনেক শব্দ তিনি তাঁর কবিতাসমূহে তিনি ব্যবহার করে চলেছেন। যে বিষয়টি কেবল ব্যাকরণিক দিক থেকে ভাষার প্রচলিত কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়ায়নি, বরঞ্চ অর্থের নতুন নতুন নির্মিতি আর তার সামাজিক ব্যকরণ নির্মাণের পেছনেও বড়ো ভূমিকা পালন করেছে।
এই ধরনের ভাষা-শব্দ ব্যববহারে বেলায়ও তিনি কেন যেন আগ্রহী নয়। তাহলে কি মাশরুরের ভাষা-জগতে কোনো নস্টালজিয়া-নির্ভর ভাষার ভান্ডার নেই? থাকলে কেন তিনি তা ব্যবহার করেননি? তা মাশরুরই বলতে পারবেন ভালো।
আবার সেই চর্যাপদের আমল থেকেই তিনি করেছেন তা বলব না, কিন্তু সেই ধারা আর ধারণা মেনে অসংখ্যা প্রচলিত শব্দ ব্যবহারও তিনি করেছেন। কিন্তু মাশরুরের কবিতায় আবেগ, আমেজ, রোমান্টিকতার অন্যতম গুণ নস্টালজিয়া নির্মিতির ভাষা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এর কোনো ধরনের প্রবণতাই যেন লক্ষ করা যায় না তাঁর কবিতায়। এই ধরনের ভাষা-শব্দ ব্যববহারে বেলায়ও তিনি কেন যেন আগ্রহী নয়। তাহলে কি মাশরুরের ভাষা-জগতে কোনো নস্টালজিয়া-নির্ভর ভাষার ভান্ডার নেই? থাকলে কেন তিনি তা ব্যবহার করেননি? তা মাশরুরই বলতে পারবেন ভালো। আর মাশরুরের সময়ে অন্যান্য কবিরা যেভাবে মুসলিম কমিউনিটির ভাষা ব্যবহারের দিকে পা বাড়িয়েছেন, সেই ব্যাপারেও তিনি কোনো প্রচেষ্টা চালাননি। বরঞ্চ তিনি এর বিপরীতেই থাকতে যেন পছন্দ করেছেন। আর নিজে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হওয়ার কারণেই কি বারবার কঠিন আর বেশি বেশি জটিল আর ব্যঞ্জনামণ্ডিত ভাষা ব্যবহার করলেন পুরো কাব্যে? এই প্রভাব হয়তো অবচেতনেই তিনি ধারণ করেছেন। তাতে অবশ্য কবিতার বেশি ক্ষতি হয়নি।
শেষ কথা। মাশরুরের এই কাব্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাক্রম, ধরা-ধারণা কিংবা বিষয় নির্ধারণ করে পড়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পড়তে কেউ পারেন, কিন্তু পড়লে মূল বিবেচ্য বিষয় স্থানচ্যুত হবে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, বলা একভাবে উচিতই হবে, মাশরুরের এই কাব্য এই সময়-সমাজের বিচিত্র ঘটনাক্রমকে পেছনে রেখে ব্যক্তি, আধুনিক ব্যক্তির, অন্তর্চেতানমূলকতায় নির্মিত। মিখাইল বাখতিনের ‘কার্নিভাল’ তত্ত্বের বিবেচনায় বহুস্বরের বিষয় একই কোটরে ধারণ করার মতো বিষয় এই কাব্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। আধুনিক মানুষ সমাজসত্যের বাইরে গিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিবাচক ধারণা কিংবা বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করতে পারে না। পারা সম্ভব হয় না। এই বিষয় মাশরুর বেশ দারুণভাবে নিজ সময়-সমাজের দৃঢ় বাস্তবতায় তৈরি করতে পেরেছেন, একথা আমি বলব। এবং তিনি যদি এই কাজ না করে তাঁর পূর্বসুরীদের মতো কবিতা লিখতেন, তো মাশরুরকে নিয়ে আলাপের কিছু থাকতো না। কিন্তু এখন এই আলাপটা করা গেল। কিন্তু কেউ কেউ তীব্র নস্টালজিয়া সহকারে এই সময়ে এসে কবিতা লিখে চলেছেন। মাশরুরের এই কাব্য-পাঠের পর এই ব্যাপারটি পাওয়া বেশ দুষ্কর হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আধুনিকতা ও ব্যক্তির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নস্টালজিয়া সহকারে রোমান্টিক অনুধ্যানে কবিতা নির্মাণের সময়ও বোধহয় এই অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার মতো বাস্তবতা পেতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক। জন্ম ১৮ মে ১৯৯৪ সালে, ঝিনাইদহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। নিয়মিত লিখছেন ও অনুবাদ করছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০-এর অধিক।