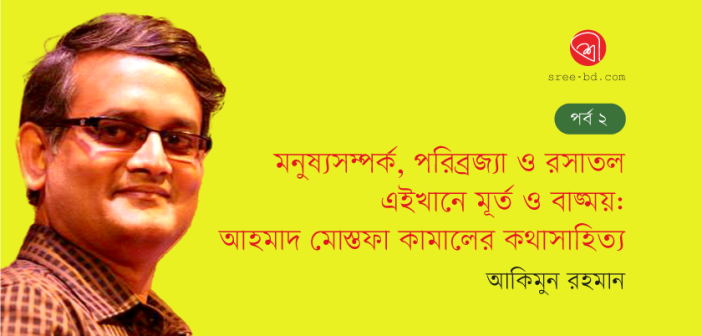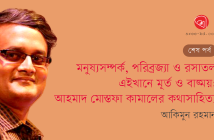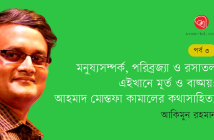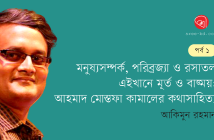পর্ব-২
তিন. বহিরিস্থিতদের গল্পগুলো এমন
আগন্তুক-এর নায়ক অঞ্জন হায়দার চৌধুরী। তরুণ অঞ্জন ‘দেখতে সুদর্শন, আবার মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল, রুচিশীল।’ স্ত্রীর কাছে সে ‘দেখতে-শুনতে যেমন সুন্দর, তেমনি কথাবার্তায়ও, গভীর অনুভূতিপ্রবণ, উদার, কনসিডারেট, আবার বেশ খানিকটা উদাসীন ও রহস্যময়।’
উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেই অঞ্জনকে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে হয়। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার জন্যই জীবনে প্রথম শহরে আসে সে, তার আগের ‘ষোল বছর’ কাটে তার উদাসপুরে, তাদের গ্রামের বাড়িতে, বাবা-মায়ের সাথে।
আমেরিকার দিকে উড়াল দেওয়ার জন্য অঞ্জনের নিজের ইচ্ছা কিছুমাত্র কাজ করেনি। বিদেশে যাওয়ার কোনো আগ্রহই বোধ করেনি সে তখন। বরং সে দেশেই রয়ে যেতে চেয়েছিলো। এখানেই পড়াশোনাটা করে উঠতে উঠতে, সে চিনে উঠতে চেয়েছিলো, তার দেশের রাজনীতিক ওঠাপড়াটার স্বরূপ। পরিষ্কার-রকমে সে জেনে উঠতে চেয়েছিলো, দেশ বা সমাজের জন্য তার প্রপিতামহ বা পিতামহ বা পিতার আত্মত্যাগের কারণগুলোকে। কিন্তু ওটি করার কোনো সুযোগ পায় না অঞ্জন। পরিবারের অন্যদের চাপে পড়ে তাকে বিদেশে যেতেই হয়।
তবে শুধুই পড়াশোনা করানোর তাগাদা থেকেই তার পরিবারের অন্যরা তাকে বিদেশে যেতে বাধ্য করে, বিষয়টা তেমন ছিলো না। দেশের রাজনীতির উথাল-পাথাল অনিশ্চিতির ঝাপটা থেকে নিজেদের পুত্রটিকে রক্ষা করার তাগাদা থেকেই মূলত অভিভাবকেরা তাকে পরবাসে পাঠায়। অঞ্জন বোঝে: ‘আমেরিকায় তাকে পাঠানো হয়েছিলো তার মতের বিরুদ্ধে, প্রায় জোর করেই—এদেশে কিছু হবে না, ছাত্ররা হরতাল, বোমাবাজি, মিছিলমিটিং করলে পড়াশোনা আর করবে কখন? অতএব এ দেশে কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এই অজুহাতে কলেজ পাশ করে বেরুনোর পরপরই তাকে বাইরে পাঠানোর জন্য তোড়জোর শুরু হলো।’ (পৃষ্ঠা ২৬)
অনিচ্ছুক মনপ্রাণ নিয়ে বিদেশে যায় সে, তারপর দিনে দিনে সেই পরদেশেই সে কাটিয়ে ফেলে ‘প্রায় ১২ বছর’। শেষে আবার সেই অভিভাবকদের চাপে পড়েই দেশে ফিরে আসতে হয় অঞ্জনকে। ‘দেশে ফিরে জায়গা তৈরি করে নিতে খুব বেশি সময় লাগে’ না তার, ‘ছ’মাসের মধ্যে চাকরি-বাকরি, বিয়ে করে রীতিমতো সংসারী’ও হয়ে ওঠে সে। দেশে ফেরার পরপরই চমৎকার এক মেয়ে, শান্তা যার নাম, তার সাথে বিয়ে হয়ে যায়। তারপর ওই দম্পতি রাজধানীর অভিজাত এক এলাকায় বসবাস শুরু করে। আর ‘একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অংশ’ হয়ে জীবন কাটানোও শুরু করে অঞ্জন। খুব দ্রুতই তার জীবনের ‘সবকিছুই ঠিকঠাক’ হয়ে আসে, ‘একটি হ্যাপি এন্ডিং ফিল্মের মতো প্রায়’। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অঞ্জনও প্রথমে ভাবে, সবই মসৃণ গতিতেই যাবে তার। কিন্তু ক্রমে ধীরে সে ‘টের পায় কোথায় যেন বিশাল একটা ফাঁক রয়ে গেছে।’
যে বয়সে প্রকৃতপক্ষে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সেই বন্ধুত্ব এতোই গভীর যে কখনো কখনো তা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে… এ শহরে যে আমার কিছু নেই। …আমি ভয়াবহ এক বহিরাগত। আমার সবকিছুই কেবল ওপর-ছোঁয়া।
সে অহর্নিশি বোধ করতে থাকে : ‘এই শহর আমি চিনি না, এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পরিচিত একটা কোনো মানুষও নেই। এইখানে আমি থেকেছি খুব সামান্য সময়—মাত্র তিন বছর—অন্তত কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এ সময় সামান্যই। …এই শহরে আমার কোনো শেকড় নেই। যে বয়সে প্রকৃতপক্ষে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সেই বন্ধুত্ব এতোই গভীর যে কখনো কখনো তা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে… এ শহরে যে আমার কিছু নেই। …আমি ভয়াবহ এক বহিরাগত। আমার সবকিছুই কেবল ওপর-ছোঁয়া। …কিছুই আমার নয়।’ (পৃষ্ঠা ২৮)
ওই অচিন শহরেই ক্রমে দিন যেতে থাকে অঞ্জনের, যতো দিন যেতে থাকে ততো সে একা হতে থাকে, ততো সে কাতর হতে থাকে তার গ্রামের জন্য। সেই গ্রাম, যেখানে সে বাবা-মায়ের সাথে কাটিয়ে এসেছিলো শৈশব ও কৈশোরের ষোলটা বছর। সেই গ্রাম, যার সবুজ-সৌন্দর্যের স্মৃতি, অঞ্জনকে এই মধ্য তারুণ্যেও অভিভূত করে রেখেছে। সেই গ্রাম, যার মানুষগুলোর জীবন-যাপনের ধরন দিয়ে চির মোহগ্রস্ত হয়ে আছে অঞ্জন। শহরে বাস করে যেতে যেতে, সেই গ্রামের শীত ও বর্ষাকে মনে করতে করতে, উদ্বেল হতে থাকে অঞ্জন। তার প্রাণ সর্বক্ষণ উথলে উঠতে থাকে। কিন্তু গ্রামের বাড়িটাকে এক নজর দেখতে যেতে সাহস হয় না তার। কী জানি, যদি সেই গ্রাম ইতোমধ্যে বদলে গিয়ে থাকে! যদি গ্রামের নদীরা বদলে ফেলে থাকে তাদের জোয়ানকি ও শোভা, যদি গাছেরা হারিয়ে ফেলে থাকে তাদের শ্যামশ্রী, সেই বিনষ্টির যন্ত্রণা অঞ্জন সহ্য করবে কীভাবে! সে তাই স্মৃতির গ্রামটাকে নিয়েই বিভোর হয়ে থাকে, সত্যকার গ্রামের দিকে পা বাড়াবার হিম্মত পায় না।
তারপরেও একদিন আচমকাই, শান্তাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে নিজ পিতৃভিটার দিকে। যেতে যেতে দেখে সে, সত্যই তার গ্রাম ইতোমধ্যে তার সকল মহিমাই খুইয়ে ফেলেছে। তার গ্রামের নদী হয়ে গেছে জীর্ণতাগ্রস্ত। হেঁটে যেতে যেতে সে দেখে ‘যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো প্রায় ভাঙাচোরা-জরাজীর্ণ। পশ্চিমে একটু দূরে খা খা শূন্যতা ও ইছামতী থাকার কথা, কিন্তু ওদিকেও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দরিদ্র ঘরদোর, ইছামতীর নামগন্ধ নেই।’ (পৃষ্ঠা ৭১)। আর এই গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো? তারা কেমন আছে এখন? অঞ্জন দেখে: ‘হাড় জিরজিরে অসংখ্য মানুষ, ক্ষুধা দারিদ্র্য আর রোগ-শোকে ক্লান্ত এতো মুখ!’ তার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।
সে দেখে, শুধু দারিদ্র্য ও ক্ষুধাই তার গ্রামের মানুষদের নিষ্পেষিত করে চলছে না; অন্য এক বৈরী শক্তির পেষণ-পীড়নও সকলের অস্তিত্বকে ‘বিপন্ন’ করে তুলেছে। ওই অশুভ রাজনীতিক শক্তি ধ্বংস করে চলছে শুভ ও কল্যাণকে, ন্যায় ও সুস্থতাকে। সেই ক্রূর হিংস্রতার মুখোমুখি দাঁড়ায়ে অঞ্জনের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে। সে পরিত্রাণের কোনো সন্ধান জানে না।
অঞ্জন হায়দার চৌধুরীর মতোই কায়সার আহমেদ আদিত্যও অন্তরের ভেতরে তার শৈশব-কৈশোরের গ্রামকে বহন করতে করতে রাজধানী শহরের ভাড়াবাড়িতে দিনপাত করে চলে। তবে তার জীবন কেবলই মধুমাখানো স্মৃতি-ভারাতুরতা থরথর কিছু নয়। সে জীবন অসচ্ছলতা, ব্যাধি, অসহায়তা, অপমৃত্যু ও অকালপ্রয়াণের পেষণে পেষণে প্রায় মিইয়ে যাওয়া। তার স্বপ্ন ছিলো শুধুই লেখক হয়ে ওঠার, কিন্তু বাস্তবতার চাপ তাকে ঠেলে ফেলে দেয় মুদ্রা উপার্জনের পৃথিবীতে।
তার বাবা দীর্ঘকাল ধরে শয্যাশায়ী। বাবার ছিলো ‘বদলির চাকরি-কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গে সংসার বয়ে বেড়ানোর সামর্থ্য’ ‘ছিলো না’ বলে, তার সংসার-সন্তানকে ‘থাকতে হতো গ্রামে’। সেই গ্রামের নাম ‘উদাসপুর’, সেখানে ‘ম্রিয়মাণ-মৃতপ্রায় ইছামতি, প্রমত্ত পদ্মা আর উদাসীন আকাশ’ মিলেঝুলে থাকে। কলেজে পড়ার জন্য সেই গ্রামকে ছেড়ে ঢাকায় আসে কায়সার। ক্রমশ সে বয়স্ক হতে থাকে; আর বিষাদ ও বিপন্নতা ও সর্বনাশকে নিজেদের সংসারের স্থায়ী সদস্য হিসেবে পেয়ে যেতে থাকে সে। সবসময় যে বাবাকে সে দেখেছে কর্মসুখী এক মানুষ, দেখেছে বাবা যেন ‘সিংহের মতো—অন্তত বাড়িতে। তর্জন-গর্জন ছিলো, একই সঙ্গে ছিলো বুকভরা গভীর ভালোবাসা। নিজের সন্তানদের আগলে রাখতে চাইতো এসবকিছু দিয়েই।’ সে বাবাই অচল অথর্ব শয্যালীন হয়ে, কোনোমতে দেহ ধারণ করতে থাকে। লম্পট অশুভের থাবা থেকে নিজ কন্যা কাজলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় বাবা, এবং কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ‘শরীরের একটা অংশ প্যারালাইজড’ হয়ে যায়।
কন্যা কাজল একটা বিবাহিত লম্পটের কথার চটক ও ছলাকলার ভেলকিতে পড়ে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু লোকটি তাকে বিয়ে তো করে না-ই, বরং এক বাসায় আটকে রেখে, কাজলকে ধর্ষণ করে চলে। সাথে আরো কিছু স্যাঙাতও জুটিয়ে নেয় সেই লোক। কায়সার এবং অন্যরা যখন কাজলের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটাকে কোনোমতে বরদাস্ত করার শক্তি জোটানোর চেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন একদিন কাজল ফিরে আসে। কায়সারকে সব কথা জানিয়ে সে আত্মহত্যা করে। সেই শোক বাবাকে দেয় স্থবির-অর্ধমৃত জীবন। সংসার অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তবে বিপদ যেন ওই সংসারকে তার তাণ্ডব থেকে রেহাই দিতে রাজিই হয় না। হঠাৎই মৃত্যু ঘটে সংসারের বড়ো ছেলেটির। কায়সার দেখে ‘কাজলের মৃত্যু বা বাবার অসুস্থতায়’ তাদের ঘরে ‘খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা তৈরি হয়নি, কিন্তু ভাইয়ার মৃত্যুতে সেটাই’ অবধারিত হয়ে ওঠে।
তখন, যে কায়সার বরাবর স্বপ্ন দেখেছে লেখক হয়ে ওঠার, বরাবর যে স্বপ্ন দেখেছে শুধু লেখার ভেতরে নিজেকে সমর্পিত করে রাখার, সেই কায়সার তার বিপন্ন পরিবারকে রক্ষার জন্য নিজের স্বপ্নকে বলি দেয়। চাকুরি শুরু করে সে। ‘প্রথম দিকে’ তাকে পার করতে হয় ‘অমানুষিক কষ্টের’ দিন। তখনই ‘জীবন যে কী কঠিন, সে হাড়ে হাড়ে টের’ পেতে থাকে। ‘এতোগুলো মুখ কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, এই চিন্তা তাকে পাগল করে’ তুলতে থাকে তখন। ‘এই সময়টিতেই সে লেখালেখির কথা ভুলে যেতে থাকে; সত্যি বলতে কি, লেখার কথা তার চিন্তার মধ্যেই’ আর আসতে থাকে না। ‘জীবন তাকে এমনই আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে’ ফেলে তখন। আর, দিনে দিনে একা থেকে আরো একা হয়ে উঠতে থাকে সে। স্বপ্নবালিকারাও একে একে তাকে ছেড়ে চলে যায়, সে শুধু নিঃশব্দ চোখে সেই চলে যাওয়াকে দেখে চলে। প্রিয় নারী মৃন্ময়ী অজ্ঞাত কারণে তাকে ভরসা করতে সাহস পায় না। ছেড়ে চলে যায়। বীথি কাছে এসেও বরাবর অনিকট হয়ে থাকে। সে কাউকেই ফেরানোর আকুলতা বা তাগাদা বা উদ্যম পায় না। শুধু ব্যথাটুকু নীরবে বয়ে যেতে থাকে।
তখন, শৈশব-কৈশোরের সেই যে গ্রাম উদাসপুর, তাকে নিজের অন্তরের আশ্রয় করে নিয়ে সে জীবন পার করতে থাকে। তবে শুধু উদাসপুরই তার একমাত্র আশ্রয় হয়ে আসে না। বন্ধুতার আশ্রয় সে খোঁজে, খোঁজে প্রেম, খোঁজে স্বপ্নকন্যাকে। বন্ধুরা একে একে কবে যেন সরে সরে গেছে। প্রিয়বন্ধু কবীর ‘দেশ ছেড়ে চলে যায়’, অন্য বন্ধুরা ‘নানারকম কাজে জড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে’ পড়ে। তখন থাকে শুধু মনে মনে উদাসপুরের সাথে কথা বলে চলা। তখন শুধু থাকে ভোরের শুকতারার সাথে ভাব বিনিময় করা, একা একা। থাকে অগ্রজ কথাকারদের গড়া চরিত্রদের সাথে সময় যাপনের ঘোরগ্রস্ততা। থাকে বিপন্ন সংসারের কাছ থেকে পাওয়া মায়া ও দরদ। থাকে একাকিত্ব আর লিখে উঠতে চাওয়ার সুতীব্র বাঞ্ছা, থাকে আর লিখতে না-পারার দাহ। আর, উদাসপুরকে ফিরে পাবার আকুতি।
ঋভু বা পারভেজ মাহমুদ অবশ্য অতোটা ক্লিষ্ট হবার ভাগ্য পায় না। সে অত্যন্ত সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও ধনশালী এক পিতার একমাত্র পুত্র। তার বাবা ছিলো ‘উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদশালী’। এবং ‘যথেষ্টবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি ছিল বলেই কোথাও কোনো ক্ষতির মুখে পড়তে’ হয়নি কোনোদিন। সেই বাবাকে ঋভু হারায় ‘বেশ অল্প বয়সেই। …আকস্মিকভাবেই চলে’ যায় পিতা। ঋভু ‘তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোয়নি।’ তবে বাবার অকালপ্রয়াণের কারণে ‘আর্থিক সংকট বা সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো’ সংকটের মোকাবেলা করতে হয় না ঋভুকে। কারণ ‘ব্যাংকে মোটা টাকা গচ্ছিত রেখেই’ তার বাবা পৃথিবী থেকে ‘বিদায় নিতে’ পারে।
কিন্তু তারপরেও সংকট আসেই। অতি জটিলরকমের এক সংকট এসে, ঋভুর জীবনটা তছনছ করে দিতে থাকে। ঋভুর বাবা ‘কোনো এক অজানা কারণে তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা দু’ভাগে ভাগ করে’ রেখে যায়। ‘এক ভাগ’ থাকে ‘তার স্ত্রীর নামে, আরেক ভাগ ঋভুর নামে।’ এই ‘ব্যাপারটাকে মা সহজভাবে নিতে পারে’ না।
কিন্তু তারপরেও সংকট আসেই। অতি জটিলরকমের এক সংকট এসে, ঋভুর জীবনটা তছনছ করে দিতে থাকে। ঋভুর বাবা ‘কোনো এক অজানা কারণে তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা দু’ভাগে ভাগ করে’ রেখে যায়। ‘এক ভাগ’ থাকে ‘তার স্ত্রীর নামে, আরেক ভাগ ঋভুর নামে।’ এই ‘ব্যাপারটাকে মা সহজভাবে নিতে পারে’ না। মা এতে শুধু অসম্মানিতই বোধ করে না, সে ‘দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু’ করে যে, ‘এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা ঋভু জানতো’। মায়ের মনে হতে থাকে যে, ঋভুর বাবা তাকে ‘বিশ্বাস করেনি’। তার প্রতি তার স্বামীর ‘আস্থাহীনতা’ তাকে বেদনা ও লজ্জা দিতে থাকে। ক্রুদ্ধ করে তুলতে থাকে। একমাত্র ছেলের ওপর তার বিদ্বেষ জন্মাতে থাকে।
ঋভু মাকে বোঝাতে চেষ্টা করে খুবই, কিন্তু সে ‘কিছুতেই মাকে বিশ্বাস করাতে’ পারে না যে, ‘সে এগুলোর কিছুই’ জানতো না। ফলে মায়ের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। মা তাকে অবিশ্বাস করে চলে। ঋভুকে গণ্য করতে থাকে প্রতিপক্ষ বলে। তখন ‘ঋভুর কোনো কাজেই’ আর তার মায়ের যেন ‘কোনো আগ্রহ’ থাকে না। থাকে কেবল প্রয়াত স্বামীর প্রতি সীমাহীন ক্ষোভ, এবং পুত্রের প্রতি তীব্র অবিশ্বাস।
ঋভুরও কী হয়, ক্রমে সেও মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো শুরু করে। পড়াশোনা বাদ দিয়ে, দীর্ঘদিনের জন্য চলে যায় দেশের বাইরে। ক্রমে কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব এসে তার সুশৃঙ্খল জীবনটাকে পুরোই এলোমেলো করে দেয়। তখন এমনকি যে মেয়েটির স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে তখন সে অথই সুখ পাচ্ছিলো সেই অবন্তির সাথেও তার সম্পর্কটা উরাধুরা আলগা হয়ে যায়। অবন্তির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।
অবিশ্বাস ও বেদনাকে লাগাতার বয়ে চলতে চলতে, একদিন মা জটিলরকমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চলৎশক্তিরহিত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। ক্রমে ঋভু আবার পড়াশোনায় ফিরে আসে, ক্রমে কেমন করে যেন মায়ের মন থেকে পুত্রের প্রতি জেগে ওঠা অবিশ্বাসটা দূর হয়ে যায়। শয্যাশায়ী মা নানামতে পুত্রের কাছে ‘তার দুঃখ প্রকাশ, তার অনুতাপ প্রকাশ’ করে ওঠার চেষ্টাটা চালাতে থাকে। মা যে ‘ঋভুকে ভুল’ বুঝেছিলো, ‘সেটি স্বীকার’ করে নিয়ে পুত্রের অন্তরের কাছে ফিরে আসার জন্য তড়পাতে থাকে মা।
কিন্তু ঋভু তখন পলে পলে টের পেতে থাকে, ‘বড্ড দেরি হয়ে’ গেছে। ‘সেই ভুল বোঝাবুঝির দিনগুলোতে ধীরে ধীরে এতটাই দূরে সরে’ গেছে সে যে, ‘আর কাছে ফেরা’র পথ খুঁজে পাবে না সে। পায়ও নি আর কখনো। আর কখনো মায়ের অন্তরের কাছে ফিরে আসতে পারেনি ঋভুর অন্তর।’ বাবার চলে যাওয়ার পরে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের সঙ্কটকালীন পলে পলে মনে মনে নিজের ছোটো বোনটার কাছে খুব আশ্রয় আর অভয় খুঁজে চলে ঋভু। তার সেই বোন-নীলু। সে অকালপ্রয়াত। ‘কী একটা অসুখ হয়েছিল’, জটিল অসুখ। ‘দেশের চিকিৎসকরা’ বলেছিলো ‘বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে’। ‘বাবা সবাইকে নিয়েই থাইল্যান্ডে’ যায়, মেয়ের চিকিৎসার জন্য। ‘সেখানেই মারা যায় নীলু, হাসপাতালের শুভ্র বিছানায় শুয়ে।’
নীলু চলে যাওয়ায় তাদের জীবন থেমে থাকে না বটে, কিন্তু ‘জীবনের ছন্দটা’ আর ‘আগের মতো থাকে না’। বাবা নিঃশব্দে তার ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে, নিজেকে করে তোলে প্রায় ‘গৃহবন্দী’। ‘সুস্থ-সবল মানুষটা অতি দ্রুত বুড়িয়ে’ যায়, ‘তারপর যেন সময় হওয়ার আগেই চলে’ যায় বাবা, তার মেয়ের কাছে।
বাবা চলে গিয়ে মুক্তি পায়, কিন্তু ঋভুকে শেকল-মোড়ানো পা নিয়ে চলতে থাকতে হয় জীবনের পথে পথে। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সেই যে নষ্ট হয়, সেটাকে আর ভালো করা যায় না। নীলুকে হারানোর বেদনা, নিজের কর্মমোড়ানো দিবালোকে তেমন একটা বাজতে শোনে না বটে ঋভু কিন্তু চিরদিন ধরে সেই তার ‘তেরো বছরের’ কালে নীলুর মরে যাবার পর থেকে তার স্বপ্নে কেমন এক বালিকা এসে হানা দিতে থাকে। সেই এক স্বপ্ন। ‘নিয়মিত স্বপ্ন’। ‘ছোট্ট একটা মেয়ে, পানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে, তার হাতদুটো ওপরে তোলা, যখন ভেসে উঠছে তখন সেই হাত নেড়ে চিৎকার করে ডাকছে—ভাইয়া, ভাইয়া, ভাইয়া…।’ (পৃষ্ঠা ১৫৩)
এই এক ব্যাখ্যাতীত স্বপ্নকে পেতে পেতে প্রায়-প্রায়ই সচ্ছল-সম্পন্ন ঋভুর রাতের অল্পস্বল্প নিদ্রা পাবার ক্ষণটুকু ফুরায়। আর বেশিটা রাত্রি যায় বিনিদ্রায়। তার দিনগুলো ভরে থাকে বিবিধ মনস্তাপে। ‘মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার দুঃখ’ তাকে পুড়িয়ে চলে সর্বক্ষণ। অকালে হারানো বোনটাকে মনে আসে তার ক্ষণে ক্ষণে, প্রাণ হু-হু করে ওঠে। বাবাকে হারানোর বিষাদ তার সকল চলাকে থামিয়ে দিতে চায়। অসুস্থ মায়ের জোরাজুরিতে বিয়ে করা রিনি নামের মেয়েটির কথাও তার মাঝেমধ্যে মনে আসে। মনে আসে সেই বিফল বিবাহের স্মৃতি। ওই বিবাহিত সম্পর্কের ভেতরে ‘কোথাও যেন থাকে’নি ঋভ্।ু ‘একটা নীরবতার কাঁটা ছিলো দুজনের মধ্যে। ঋভু অনুভব করতো, তার যেন কোনো সংলগ্নতা নেই!’ (পৃষ্ঠা ৩২) স্ত্রী রিনি সেটা বুঝে উঠতে পারে, তারপর সে ‘তার নিজের জন্য অন্য এক জীবন বেছে’ নেয়। চলে যায় ঋভুকে ছেড়ে।
তারপর থেকে শুরু হয় পরিজনহীন একলা চলার দিন। তখন দণ্ডে দণ্ডে কেবল নীলুকে স্মরণে আসতে থাকে নিঃসঙ্গ ভাইটির। খুব মনে আসতে থাকে। তার মনে হতে থাকে যে, ‘আচ্ছা, নীলু যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে কি আমার জীবন অন্যরকম হতো? …বাবা তখন সম্পত্তি ভাগ করতেন কীভাবে? নাকি আদৌ করতেন না? মায়ের সঙ্গে ঋভুর সেই বিশ্বাসহীনতা আর সংকটের সময়ে নীলু কী করতো? নিশ্চয়ই দু-পক্ষের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন হিসেবে থাকতো ও? নিশ্চয়ই দূরত্বটা তৈরি হতে দিতো না। কিংবা মায়ের মৃত্যুর পর ঋভু আর রিনির সেই নীরব সম্পর্কের সময় ও থাকতো সরব হয়ে, হয়তো ওর জন্যই সম্পর্কটাও স্বাভাবিক থাকতো, রিনিকে চলে যেতে হতো না। কিংবা এই নিঃসঙ্গ সময়ে নিশ্চয়ই ও পাশে এসে বসতো, কান্নাকাটি করতো… বোনেরা তো মায়ের ছায়া, ও থাকলে জীবন নিশ্চয়ই এরকম হতো না। তাহলে কি তাকে চিরকালের জন্য নিঃসঙ্গ করে দেওয়ার জন্যই নীলু চলে গিয়েছিল?’ (পৃষ্ঠা ৩৭)
ঋভুর ওই বিষাদক্লিন্ন জীবনটাকে নানাভাবে হাসি-হুল্লোড়ে ভরিয়ে রাখতে চায় বন্ধু অংশু। কিন্তু সবসময় যে সে সেটা পেরে ওঠে, এমন নয়। আর্থিক-টানাপোড়েনে বিপন্ন অংশুকে মুদ্রার নিরাপত্তা দেয় ঋভু, অংশুর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায়। নামী স্থপতি হিসেবে বাহ্বা পেতে থাকে অংশু। ওদিকে অংশুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ঋভু কিছুই প্রত্যাশা করে না। কিছুমাত্র না। তার যেন কোনোখান থেকেই কিছুই প্রত্যাশা করার নেই। আছে শুধু দিন পার করা, রাতগুলো ফুরিয়ে ফেলা। এমন দিনে অবন্তি আসে আবার, ঋভু তার পাশে বসে নিজেকে সুখী বোধ করতে থাকে। তারা নিবিড়রকমে নিকটও হয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, এই দুজন এবার বিবাহিত হবে। সংসারে থিতু হবে। তেমন সময়ে ঋভুর কাছে আসে কোন এক লুসিয়া আরিয়ানা জিওভান্নির মেইল।
ঋভুর মনে পড়ে, এই আরিয়ানার সাথে তার নেপালে দেখা হয়েছিলো। সেই যখন বাবার মৃত্যুর পরে, সে মায়ের অবিশ্বাসভরা দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তখন সে গিয়েছিলো নেপালে, সেখানে থেকেছিলো দীর্ঘদিন। সেখানেই পায় সে ইতালির মেয়ে আরিয়ানার দেখা। তাদের সম্পর্ক একসময় গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে , কিন্তু নেপাল থেকে ফিরে আসার পরে ঋভুর সাথে আরিয়ানার যোগাযোগটা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। কুড়ি বছর পরে আবার আরিয়ানা ঋভুকে খুঁজে বার করে, তার কাছে এসে পৌঁছে, এবং ঋভুকে জানায় যে, সে যেই কন্যাটির জননী, তার পিতা হচ্ছে ঋভু। এই কন্যা তাদের সেই কুড়িবছর আগেকার নেপাল-বাসের ফসল। ঋভুর সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠতে থাকে সুখে ও বিস্ময়ে ও রোমাঞ্চে।
কন্যা সোফিয়া ঋভুকে জানায় যে, আরিয়ানা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। মরার আগে আরিয়ানা এসেছে কন্যাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে। শুরু হয় ঋভুর আরেক যুদ্ধ। আরিয়ানার শেষদিন পর্যন্ত তার পাশে থাকার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে সে।
তবে নিপাট সুখ সম্ভবত তার জন্য বরাদ্দ করতে পারেনি ভাগ্য কখনো। কন্যা সোফিয়া ঋভুকে জানায় যে, আরিয়ানা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। মরার আগে আরিয়ানা এসেছে কন্যাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে। শুরু হয় ঋভুর আরেক যুদ্ধ। আরিয়ানার শেষদিন পর্যন্ত তার পাশে থাকার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে সে। আরিয়ানা তার কন্যাসহ ইতালিতে ফিরে গিয়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করে, এদিকে ঋভু শুরু করে ইতালির ভিসা পাওয়ার তোড়জোর। নিজের অন্তরে অবন্তির জন্য আকুলতাকে ঠিক টের পায় ঋভু, আবার আরিয়ানার জন্যও বোধ করতে থাকে গহন মমতা।
ইতালির ভিসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঋভু ক্লান্ত হতে থাকে, ‘প্রতিদিনের অপেক্ষাকে’ মনে হতে থাকে ‘অনন্তকালীন’, মনে হতে থাকে ‘যেন কোনোদিন এর শেষ হবে না।’ ভিসা পাবার অপেক্ষায় থাকে ঋভু, আর অকারণেই, থেকে থেকে তার, মরণকে মনে পড়তে থাকে। তার মনে হতে থাকে, ‘বড়ো দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আছে সে, অকারণ-অহেতুক!’
আরও পড়ুন : মনুষ্যসম্পর্ক, পরিব্রজ্যা ও রসাতল এইখানে মূর্ত ও বাঙ্ময় : আহমাদ মোস্তফা কামালের কথাসাহিত্য – ১ম পর্ব

বাংলা ভাষার একজন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। আকিমুন রহমানের গ্রন্থসমূহ হলো : ‘আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০)’, ‘সোনার খড়কুটো’, ‘বিবি থেকে বেগম’, ‘পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে’, ‘রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি’, ‘এইসব নিভৃত কুহক’, ‘জীবনের রৌদ্রে উড়েছিলো কয়েকটি ধূলিকণা’, ‘পাশে শুধু ছায়া ছিলো’, ‘জীবনের পুরোনো বৃত্তান্ত’, ‘নিরন্তর পুরুষভাবনা’, ‘যখন ঘাসেরা আমার চেয়ে বড়ো’, ‘পৌরাণিক পুরুষ’, ‘বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০ বঙ্গাব্দ)’, ‘অচিন আলোকুমার ও নগণ্য মানবী’, ‘একদিন একটি বুনোপ্রেম ফুটেছিলো’, ‘জলের সংসারের এই ভুল বুদবুদ’, এবং ‘নিরুদ্দেশের লুপ্তগন্ধা নদী’।
আকিমুন রহমান ভালোবাসেন গন্ধরাজ আর বেলীফুল আর হিজলের ওড়াভাসা! আর তত্ত্বের পথ পরিক্রমণ! আর ফিকশন! ঊনবিংশ শতকের ইউরোপের সকল এলাকার গল্পগাঁথা আর এমিল জোলার কথা-বৈভব! দূর পুরান-দুনিয়ায় বসতের সাথে সাথে তিনি আছেন রোজকার ধূলি ও দংশনে; আশা ও নিরাশায়!