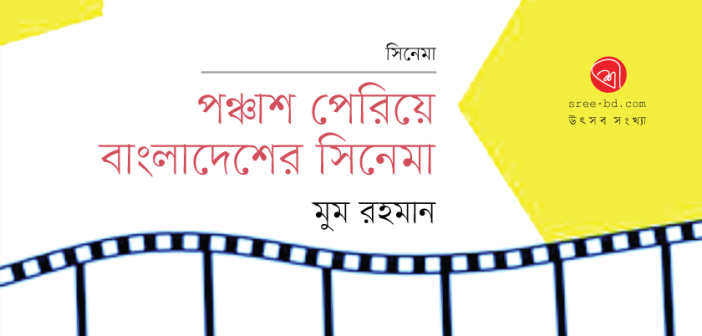পঞ্চাশ বছর একজন ব্যক্তি মানুষের জন্য অনেক বড়ো বিষয়। কিন্তু একটি দেশের জন্য তা খুব বিরাট সময়কাল নয়। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পঞ্চাশ বছর পার করার পর কি তরুণ আছে নাকি বৃদ্ধের মতো রোগে-শোকে কাহিল সেটা তলিয়ে দেখার সময় এসেছে। আমাদের আত্ম-সমালোচনার সংস্কৃতির বড়ো অভাব আছে। সেই দিক থেকে আমরা অনেক সময়ই বিপদে পড়ি। সমস্যা, অসুবিধা এগুলো জীবনের অংশ, রাষ্ট্রের অংশ। আগে সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে, মেনে নিতে হবে, পরে না হয় সমাধান। অন্তত চিকিৎসা পদ্ধতিটা তো বলে প্রথমে রোগ নির্ণ, তারপর সেই রোগের সঙ্গে লড়াই এবং টিকে থাকা। চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এটুকু ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করেছি।
মনে রাখতে হবে, ‘কাইয়ে দ্যু সিনেমা’র মতো পত্রিকা ফরাসি চলচ্চিত্রের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় সিনেমায় আসার আগেই ভারতীয় সিনেমার সংকট নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আমাদের মুষ্টিমেয় চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক, পণ্ডিত, শিক্ষকের সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।
পঞ্চাশ পেরুনো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, শিক্ষার অভাব, চলচ্চিত্র শিক্ষা। এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র শিক্ষার সূচনা হয়েছে সদ্য। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ, পাঠ ইত্যাদির সীমানাটিও অতি সীমাবদ্ধ। চলচ্চিত্র বিষয়ক পুস্তক হাতে গোনা, সে অর্থে একটি ভালো চলচ্চিত্র পত্রিকাও নেই। মনে রাখতে হবে, ‘কাইয়ে দ্যু সিনেমা’র মতো পত্রিকা ফরাসি চলচ্চিত্রের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় সিনেমায় আসার আগেই ভারতীয় সিনেমার সংকট নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আমাদের মুষ্টিমেয় চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক, পণ্ডিত, শিক্ষকের সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এফডিসিকেন্দ্রিক যে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ধারা গড়ে উঠেছিল—একটা সময় দেখা গিয়েছিল সেখানে নেহাত বাণিজ্যই হয়েছে। সে বাণিজ্য কখনো এতটা স্থূল যে রুচিশীল দর্শক সরে গিয়েছে। এফডিসি আমাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিষ্ঠান। তাকে ঋদ্ধ করা, চর্চা, প্রজ্ঞায় বর্ধিত করার অর্থই হলো জাতীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়ন হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই এফডিসির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কারিগর, শিল্পী প্রত্যেকের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে চলচ্চিত্র জ্ঞান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে চলচ্চিত্র শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা আরও সুপরকল্পিত ও বর্ধিত হওয়া উচিত ছিল, যা হয়নি। ফলে আমাদের চলচ্চিত্রের সঙ্গে বৌদ্ধিক চর্চার একটা ফারাক রয়ে গেছে। সিনেমা একই সঙ্গে বিনোদন, বাণিজ্য এবং শিল্পকলা—তাই এর কার্যক্রমকে আরও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা করা উচিত ছিল। গত ৫০ বছরে তার অভাব বেদনাদায়কভাবেই ছিল।
এরচেয়েও বড়ো বেদনার কথাটি হলো, ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল সিনেমা হলগুলো। এর জন্য যে শুধু দুর্বল সিনেমা অথবা সিনেমার দর্শক ধরে রাখার উপাদান কমে যাওয়া দায়ী তা মোটেও নয়। বরং পুঁজিবাদ, বিশ্ব সংস্কৃতি, হিন্দি, তামিল তথা অন্যান্য দেশের সিনেমার সহজলভ্যতাও দায়ী। আমরা বাজার নিয়ন্ত্রণ, বিপণন ব্যবস্থা যেমন পারিনি, তেমনি নিজস্ব চলচ্চিত্র নীতিমালা, সিনেমা হলগুলো চালু রাখার উপায় বের করতে পারিনি।
ইতিহাস বলে, সকল রকমের বঞ্চনা, অবদমন এমনকি ব্যর্থতার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে জেগে ওঠার শক্তি। এই শক্তি আমি বাংলাদেশের সিনেমার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আপাতত বেদনা ও ব্যর্থতার তলানিতেই রয়েছে সুখ ও সাফল্যের পরম খনিজ উপাদান। কারণ ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। আর সিনেমা তো মানুষের সৃজনশীল কর্ম, সে কেন ঘুরে দাঁড়াবে না।
বাংলা সিনেমার ঘুরে দাঁড়ানোর নজির আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। একসময় সিনেমা হলে হলে ঢুকে পড়েছিল অবৈধ কাটপিস, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, নৃশংসতা আর রুচিবিকৃতি। সেখান থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। অশ্লীল সিনেমার যুগ থেকে আমরা এখন মুক্ত। নতুন একটা প্রজন্ম বাংলা সিনেমার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের হাতে-নাতে তার ফলাফল আছে। আজকের ‘মাটির ময়না’ কিংবা ‘রেহেনা মরিয়ম নূর’ আন্তর্জাতিক সিনেমা অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে নবায়ন করছে।
আবার যদি একটু ইতিহাসে ফিরে যাই, আমরা দেখব বাঙালির সিনেমা বানানোর ইতিহাসটি কিন্তু সংগ্রাম মুখর এবং বিপ্লবের পথ ধরেই এসেছে। ১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার খান যখন ‘মুখ ও মুখোশ’ নামে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক সিনেমা তৈরি করলেন তখন তা কেবল একটা ভূ-খণ্ডের সিনেমা তৈরির নতুন ইতিহাস রচিত হলো না, তখন একটা ভূ-রাজনীতির জবাবও দেওয়া গেল। সে সময়কার পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার, প্রভুত্ববাদী পাকিস্তান সরকার মনেই করতেন পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ)-এর জনগণের যোগ্যতা নেই সিনেমার মতো জটিল শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার। পাকিস্তান সরকারের একচোখা প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জবাব হিসেবেই ‘মুখ ও মুখোশ’কে দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য করা দরকার, ১৯৫৬ সালে ‘মুখ ও মুখোশ’ বাংলাদেশের সূচনা হলেও, ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় কিন্তু বানিয়ে ফেলেছিলেন বিশ্বমানের বাংলা সিনেমা ‘পথের পাঁচালী’ যা আজকের দিনে এসে বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ। কাজেই তুলনায় আমরা তখনো পিছিয়ে।
আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই পিছিয়ে থাকার কারণটি কিন্তু ভূ-রাজনৈকিত, অর্থনৈতিক। কারণ বাংলাদেশকে বারবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো বটেই বিশেষত সিনেমার মতো বিজ্ঞান-বাণিজ্য-শিল্পকলা সমন্বয়বাদী কর্মের জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা, পরিবেশ দরকার তা আমাদের কখনোই অনায়াস সাধ্য ছিল না। যে বিপুল অর্থলগ্নি লাগে, যে ধরনের অত্যাধুনিক কারিগরি সহায়তা লাগে, সংগীত-নৃত্য-নাট্য-দৃশ্যকলার যে সুসংহত সমন্বয় একটি ভালো সিনেমার জন্য লাগে তার কোনো কিছুর জন্যই আমরা প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাইনি। তবুও দেরিতে হলেও, সকল প্রতিকূলতা এড়িয়ে আমরা শুরুটা করেছিলাম।
এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র সিনেমার নাম উল্লেখ করে, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সিনেমায় প্রবেশ করব। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একটি সিনেমার নাম উল্লেখ করতে চাইলেও যে সিনেমাটির নাম উল্লেখ করতে হবে সেটি হলো ‘জীবন থেকে নেয়া’। উল্লেখ্য ১৯৭০ সালে বানানো সেই সিনেমা আজকেও আমাদের সিনেমা যাত্রায় একটি মাইলফলক হয়ে আছে। তখনো মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন হয়ে গেছে, উনসত্তরের গণ আন্দোলন হয়ে গেছে। অথচ সে অর্থে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এসবের কোনো প্রভাব ছিল না। সামাজিক, রোমান্টিক, ফ্যান্টাসি, রূপকথা, মারপিট—নানা ঢঙের ছবি মুক্তি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের রাজনীতি নেই, বাঙালির চেতনার কথা নেই। বাংলাদেশের সিনেমাতে যেন বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি, বাংলাদেশের মানুষই অনুপস্থিত ছিল। সেই বিবেচনায় জহির রায়হান এ দেশের প্রথম ভূ-রাজনৈতিক সচেতন চলচ্চিত্রকার হিসাবে আবির্ভূত হলেন ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্র নিয়ে। কেবলমাত্র শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে নয়, তার ‘জীবন থেকে নেয়া’ প্রচলিত বাণিজ্যিক বাংলা চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধেও এক প্রতিবাদ। ‘একটি দেশ/ একটি সংসার/ একটি চাবির গোছা/ একটি আন্দোলন/ একটি চলচ্চিত্র…’ এমনি এক স্লোগান নিয়ে জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ শুধু বাংলা চলচ্চিত্রেই নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, স্বাধীনতার পর বাংলা চলচ্চিত্রের আরেকটি বিয়োগান্তক অধ্যায় হলো জহির রায়হানের অন্তর্ধান। ধারণা করা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে তাকে আরও দীর্ঘকাল পেলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অবকাঠামো আরও সমৃদ্ধ হতো।
কেবলমাত্র শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে নয়, তার ‘জীবন থেকে নেয়া’ প্রচলিত বাণিজ্যিক বাংলা চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধেও এক প্রতিবাদ। ‘একটি দেশ/ একটি সংসার/ একটি চাবির গোছা/ একটি আন্দোলন/ একটি চলচ্চিত্র…’ এমনি এক স্লোগান নিয়ে জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ শুধু বাংলা চলচ্চিত্রেই নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন।
জহির রায়হানের ধারাবাহিকতাতেই আমরা বাংলাদেশের সিনেমার আরেক কান্ডারি হিসেবে পাই আলমগীর কবিরকে। ‘ধীরে বহে মেঘনা’ (১৯৭৩), ‘রুপালি সৈকতে’ (১৯৭৯), ‘সীমানা পেরিয়ে’ (১৯৭৭)-এর মতো অনবদ্য বিষয় ও ভাবনার চলচ্চিত্র তিনি উপহার দিয়েছেন বাংলা সিনেমার দর্শককে। ‘রুপালি সৈকতে’, ‘ধীরে বহে মেঘনা’র মতো চলচ্চিত্রে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ‘সীমানা পেরিয়ে’ বাংলা সিনেমা দর্শকের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা, প্রেম, পুঁজিবাদ, বেঁচে থাকার লড়াই এবং মানুষের তৈরি সামাজিক শ্রেণি ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা, চিন্তা ও সম্পর্ককে তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আধুনিকতায়। এটাও আরেক বিষাদের কথা যে, আলমগীর কবিরকে আমরা হারিয়েছি অসময়ে, অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায়।
স্বাধীনতার পর, পুরো দশকটাই ছিল বাংলাদেশের সিনেমার স্বর্ণযুগ। কেবলমাত্র সেই সময়ের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলোর নামের তালিকা দেখলেই আমরা ধারণা করতে পারব কী ঈর্ষণীয় একটি সময় পার হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে। এই সময়েই আমরা পেয়েছি একের পর এক নারায়ণ ঘোষ মিতা’র ‘লাঠিয়াল’, হারুনর রশিদের ‘মেঘের অনেক রং’ (১৯৭৬), সুভাষ দত্তের ‘বসুন্ধরা’ (১৯৭৭), আমজাদ হোসেনের ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ (১৯৭৮), মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী’র ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৭৯) এর মতো কালজয়ী সব সিনেমা।
জহির রায়হান, আলমগীর কবিরের পর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মেধাবী চলচ্চিত্রকার আমার বিবেচনায় খান আতাউর রহমান। তিনি একাধারে চলচ্চিত্র পরিচালক নন, সংগীত পরিচালক, গায়ক এবং নায়ক। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে ‘জাগো হুয়া সাভেরা’, ‘জীবন থেকে নেয়ার’ মতো চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন (আনিস ছদ্মনামে)। ‘জীবন থেকে নেয়া’র বিস্ময়কর অভিনেতা খান আতাকে আমরা ‘এ খাঁচা ভাঙবো আমি কেমন করে’ শিরোনামের বিস্ময়কর গানের সুরকার ও শিল্পী হিসেবেও পাই। পরিচালক হিসেবে খান আতা নির্মাণ করেছিলেন ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’ (১৯৬৭)। স্বাধীনতার আগে হলেও ছবির নামই বলে দেয়, এ সিনেমাও বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা বলে, স্বাধীনতার কথা বলে। পলাশীর প্রান্তরে মিরজাফর ও কতিপয় কুখ্যাত বেইমানের ষড়যন্ত্রে বাংলা-বিহার-উড়িশ্যার শেষ নবাবের পতন যেন পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির কাছে সিরাজের হেরে যাওয়া বাঙালিকে দুইশ বছরের গোলামীর শাসনে (শোষণে) থাকতে বাধ্য করেছিল। খান আতার ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’র মতো ইতিহাস ও রাজনীতি সচেতন সিনেমা স্বাধীন বাংলাদেশের সিনেমার দিক নির্দেশনায় ভূমিকা রেখেছেন। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও এ সিনেমা অনন্য। আজও বহু দর্শকের স্মৃতিতে বা বয়ানে এ সিনেমার বহু সংলাপ আমরা শুনতে পাই। স্বাধীনতার পর খান আতাই নির্মাণ করেছেন ‘আবার তোরা মানুষ হ’ (১৯৭৩), ‘সুজন সখী’ (১৯৭৫)-এর মতো চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ এবং নতুন প্রজন্মকে পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রেও ‘আবার তোরা মানুষ হ’ এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সিনেমার ইতিহাসে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা বলে বিবেচিত হবে।
খান আতা’র সঙ্গে একটি বিষয়ে মিল আছে আমজাদ হোসেনের। তিনিও অভিনেতা ছিলেন। ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্রে আমজাদ হোসেনের অভিনয় আমাদের ছুঁয়ে গেছে। আমজাদ হোসেন একই সঙ্গে অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং লেখক। তার হাত ধরে আমরা ‘নয়নমণি’ (১৯৭৬), ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ (১৯৭৮), ‘ভাত দে’ (১৯৮৪), ‘দুই পয়সার আলতা’ (১৯৮২) ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নিম্নবর্গের মানুষের চিত্রায়ণের প্রসঙ্গ এলে আমজাদ হোসেনের কথা সর্বাগ্রেই আসবে বলে ধারণা করা যায়।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্যভাবেই অন্যতম অনুষঙ্গ। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে চাষী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক অবিসংবাদী নাম। তার ‘ওরা ১১ জন’ (১৯৭২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চলচ্চিত্র। তার দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সাহিত্যভিত্তিক একাধিক চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে ‘দেবদাস’ (১৯৮২) এবং সেলিনা হোসেনের কাহিনি অবলম্বনে ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ (১৯৯৭) তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস আলোচনাতেও চাষী নজরুল ইসলামের অবদান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।
একটি দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস কখনোই কোনো প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়, এর একটি ধারাবাহিকতা থাকে। বলা দরকার, ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের ভূ-খণ্ডের জন্ম হলেও, বাঙালি ও বাংলাদেশ একটি ধারাবাহিক চেতনার ফসল। ফলে ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তানি শাসক-শোষকের কালেও বাংলাদেশের নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্রয়াস ছিলই। আর কে না জানে, একটা দেশের চলচ্চিত্রের নিজস্বতা তৈরিতে তার লোকজ উপাদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন, লোক কথা, নিজস্ব পুরাণের বয়ান তাই আমরা স্বাধীনতার আগে থেকেই পাই। সালাহউদ্দিনের ‘রূপবান’ (১৯৬৫), দিলীপ সোমের ‘সাত ভাই চম্পা’ (১৯৬৮), ‘অরুণ বরুণ কিরণমালা’ (১৯৬৯), ‘বেহুলা’ (১৯৬৬) থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যে লোকজ উপাদান ও কাহিনির যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘বেদের মেয়ে জোসনা’ (১৯৮৯)-তে এসে আমরা তার চূড়ান্ত সাফল্য দেখতে পাই। তোজাম্মেল হোসেন বকুলের ‘বেদের মেয়ে জোসনা’ বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমার ক্ষেত্রে ইতিহাস নির্মাণ করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, লোক গান, লোক কাহিনি এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রারই অংশ। ভুলে গেলে চলবে না, গ্রামই আমাদের শেকড়। আমাদের শৈশব-কৈশোরের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা রূপকথা, লোককথা দিয়েই শুরু। কাজেই ফোক ও ফ্যান্টাসি ঘরানার বাংলা সিনেমার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে লোক মনোরঞ্জন আর ব্যাবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে এইসব সিনেমা অনেকটা এগিয়ে থাকলেও শিল্পরুচির প্রশ্নে লোক কাহিনি ভিত্তিক সকল সিনেমা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এখনো স্বপ্ন দেখি যে, এ দেশের লোকজ উপাদান, অনুষঙ্গ নিয়ে যথার্থ শৈল্পিক সিনেমা নির্মিত হবে একদিন।
লোক কথা, লোক পুরাণের মতোই বাঙালি জীবনে সবচেয়ে বেশি করে জড়িয়ে আছে নদী। নদী, মাঝি, নদীবাহিত মানুষের জীবন উঠে এসেছে বাংলাদেশের একাধিক চলচ্চিত্রে। স্বাধীনতার আগেই সাদেক খানের ‘নদী ও নারী’ (১৯৬৫) বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে এক অনন্য ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালে আলমগীর কবিরের ‘ধীরে বহে মেঘনা’ (১৯৭৩), একই বছর ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৭৩) বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রকে ঋদ্ধ করে। বিশেষত অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ আজ বিশ্ব চলচ্চিত্রের সেরা চলচ্চিত্র সমূহের তালিকায় ঠাঁই পেয়ে থাকে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বাংলাদেশের সিনেমার ইতিহাসে এক গর্বিত নাম।
তবুও বলা যায়, মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী’র ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে দেশভাগের কান্না কিছুটা হলেও এসেছে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করার একক কৃতিত্ব দেওয়া যায় তানভীর মোকাম্মেলকে।
দেশভাগ আমাদের স্বাধীনতাপূর্বকালের ঘটনা। কিন্তু দেশভাগের আঁচড় দীর্ঘস্থায়ী। এই দীর্ঘস্থায়ী আঁচড় বা আঘাতের চিত্রায়ণ আমাদের দেশে তুলনায় কমই হয়েছে। দেশভাগের বিয়োগাত্মক চিত্রায়ণ আমরা পেয়েছি ঋত্বিক কুমার ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) এবং ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২) চলচ্চিত্র ত্রয়ীতে। ঋত্বিকের এই ধ্রুপদি চলচ্চিত্রসমূহও আমাদের চলচ্চিত্রকারদের হয়তো তেমন উৎসাহী করেনি দেশভাগ নিয়ে কাজ করতে। তবুও বলা যায়, মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী’র ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে দেশভাগের কান্না কিছুটা হলেও এসেছে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করার একক কৃতিত্ব দেওয়া যায় তানভীর মোকাম্মেলকে। তার একাধিক চলচ্চিত্রের প্রধান উপজীব্য দেশভাগ। তার মধ্যে ‘নদীর নাম মধুমতি’ (১৯৯৪) এবং ‘চিত্রা নদীর পাড়ে’ (১৯৯৯) একই সঙ্গে প্রবাহমনতা নদীর বিপ্রতীপে মানুষের বিভাজনের ব্যথিত বয়ান।
স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাস আলাদা করে বয়ান করা উচিত। যে অর্থে সারা বিশ্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম (স্বাধীন চলচ্চিত্র) তৈরি হয় সে অর্থে বাংলাদেশে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র চর্চা দিয়েই একটা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মুখ্য দিক হলো বড়ো কোনো লগ্নিকারীর কাছে চলচ্চিত্র নির্মাণ আটকে থাকে না। বড়ো বাজেট, বড়ো তারকার ফাঁদ থেকে মুক্তি এবং সর্বোপরি নতুন ও বিকল্প ভাষাভঙ্গি তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। তানভীর মোকাম্মেলের চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘হুলিয়া’ (১৯৯১)-র মাধ্যমেই। তবে বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মোরশেদুল ইসলামের ‘আগামী’ (১৯৮৪)। বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ধারাকে বেগবান ও ঋদ্ধ করেছে মোরশেদুল ইসলামের ‘সূচনা’ (১৯৮৮), ‘শরৎ ৭১’, জামিউর রহমান লেমনের ‘ছাড়পত্র’ (১৯৮৮), আবু সাঈয়ীদের ‘ধূসর যাত্রা’ (১৯৯২), তারেক মাসুদের ‘নরসুন্দর’ ইত্যাদি চলচ্চিত্র।
পরবর্তীকালে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের অনেকেই পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানিয়েছেন এবং মূলধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় মোরশেদুল ইসলামের নাম। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ এবং শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তার ‘দিপু নাম্বার টু’ (১৯৯৬), ‘দুখাই’ (১৯৯৭), ‘দূরত্ব’ (২০০৪), ‘খেলাঘর’ (২০০৬), ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ (২০১৫) এবং ‘অনিল বাগচীর একদিন’ চলচ্চিত্রসমূহ উল্লেখের দাবি রাখে।
শিশুতোষ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সুভাষ দত্তের ‘ডুমুরের ফুল’ (১৯৭৮), আজিজুর রহমানের ‘ছুটির ঘণ্টা’ (১৯৮০), বাদল রহমানের ‘এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী’ (১৯৮০), খান আতাউর রহমানের ‘ডানপিটে ছেলে’ (১৯৮০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় যে ১৯৮০ সালেই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য তিনটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রের জন্ম হয়। ১৯৮৩ সালে সি বি জামানের ‘পুরস্কার’ চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্রে কিশোর অপরাধ সংশোধানাগারকে বিষয়বস্তু করা হয়।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তরুণ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তারেক মাসুদ এক স্মরণযোগ্য নাম। দুঃখজনকভাবে তাকেও আমরা হারিয়েছি অকালে, আনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনাতে। তার একাধিক চলচ্চিত্র আজকের বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস রচনায় নয়া অধ্যায়ের সংযোজন করতে বাধ্য। বিশেষত তার ‘মাটির ময়না’ আমাদের চলচ্চিত্রের দায় ও শক্তিকে নতুন করে ভাবতে শেখাবে।
‘বাঙালি? না মুসলমান?’—পরিচয়ের ধ্রুপদি দ্বিধাকেই ‘মাটির ময়না’ চিত্রায়িত করেছে। এক অর্থে ‘মাটির ময়না’ এক নীরব বিপ্লব। ইসলাম ধর্ম আর ধর্মান্ধ শব্দের নতুন ডিসকোর্স পাই এ ছবিতে। একজন মৌলানার মুখের সংলাপ স্মরণযোগ্য, ‘পাকিস্তান জন্মের আগেও তো এ দেশে ইসলাম ছিল। ইসলাম কি পাকিস্তানরা এনেছে যে পাকিস্তান ভেঙে গেলে ইসলাম চলে যাবে?’ পাকিস্তান আর ইসলামকে এক করে দেখার একটা প্রবণতাকে এখানে সরাসরি আঘাত করা হয়েছে।
কিন্তু কোনোভাবেই ‘মাটির ময়না’ ইসলাম ধর্ম বা তার আচারের বিরোধিতা করে না। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা, কাঠ মৌলানাদের কার্যক্রম এগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মুসলমানের ঈদের দিনে হিন্দুর জন্য মুরগি পোলাও রান্না করার সম্প্রীতির বাস্তব চিত্র এ ছবিতে রয়েছে। যদিও বেদনাদায়ক সত্য হলো, হিজাব আর টুপির লেবাসের আড়ালে সেই সম্প্রীতিতে কিছুটা চির হলেও ধরেছে আজকাল। ধর্মকে বিভাজনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার পাকি-রাজনৈতিক ভাবনা থেকে এখনো আমরা পুরোটা মুক্ত নই। কাজেই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র ‘মাটির ময়না’।
ঔপন্যাসিক এবং টিভি নাট্যকারের বিশাল পরিধির আড়ালে চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান অনেকটাই অনির্ণীত রয়ে গেছে। অথচ প্রথম চলচ্চিত্র ‘আগুনের পরশমণি’ (১৯৯৪)-তেই তিনি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শেষ চলচ্চিত্র ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ (২০১২)-তে হুমায়ূন আহমেদ চলচ্চিত্র নির্মাণে তার চূড়ান্ত পরিণতির প্রমাণ রেখেছেন। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো সিনেমায় সমকামিতা, শিশু যৌন নিগ্রহ, শিল্পের নামে অশ্লীলতা এমনই সব স্পর্শকাতর বিষয় উঠে এসেছে।
নাসির উদ্দীন ইউসুফও ‘একাত্তরের যিশু’ (১৯৯৩) দিয়ে আলোচনায় আসেন। স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় তার ‘একাত্তরের যিশু’ এবং ‘গেরিলা’ (২০১১) মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের আরও বিস্তৃত ও গভীরতর দিকগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তবে তার সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র ‘আলফা’ (২০১০) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন।
নতুন স্বাধীন দেশে মঞ্চ নাটকের চর্চাটা আন্দোলনের আকার ধারণ করে ছিল। আর আজকে আমরা জানি, বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের পাটাতন থেকে এসে পরবর্তীকালে একাধিক ব্যক্তি টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। এর মধ্যে সালাউদ্দিন জাকী, আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাসির উদ্দীন ইউসুফ উল্লেখযোগ্য নাম। সালউদ্দিন জাকী ‘ঘুড্ডি’ (১৯৮০) সিনেমার মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। নাসির উদ্দীন ইউসুফও ‘একাত্তরের যিশু’ (১৯৯৩) দিয়ে আলোচনায় আসেন। স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় তার ‘একাত্তরের যিশু’ এবং ‘গেরিলা’ (২০১১) মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের আরও বিস্তৃত ও গভীরতর দিকগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তবে তার সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র ‘আলফা’ (২০১০) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন। সিনেমার গল্প বলার ধারাটিকে যেমন তিনি পালটে দিয়েছেন তেমনি এই ছবিতে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে নতুন মাত্রাও দিয়েছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের একাত্মতা, থিয়েটারের সঙ্গম, সুর আর চিত্রের সমন্বয় নাসির উদ্দিন ইউসুফ সুচারুভাবে অনুধাবন করতে পারেন তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ‘আলফা’।
মঞ্চ নাট্যকার, অভিনেতা, টিভি প্রযোজক, লেখক আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে হবে। তার ‘সারেং বৌ’ (১৯৭৮), ‘এখনই সময়’ (১৯৮০), ‘দুই জীবন’ ইত্যাদি সিনেমা চলচ্চিত্র সমালোচক, বিশ্লেষক এবং ইতিহাস রচয়িতার জন্য অবশ্য দ্রষ্টব্য।
আমাদের সাম্প্রতিককালে আমরা অমিতাভ রেজা, মোস্তাফা সরয়ার ফারুকী, গিয়াস উদ্দিন সেলিম, রেদওয়ান রনি, দীপঙ্কর দীপনের মতো একাধিক উজ্জ্বল চলচ্চিত্রকারকে পেয়েছি টেলিভিশনের সূত্র ধরেই। বিশেষত গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ‘মনপুরা’ (২০০৯), মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘পিঁপড়াবিদ্যা’ (২০১৩), অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ‘আয়নাবাজি’ (২০১৬) যথেষ্ট উচ্চাশা তৈরি করেছে। তাদের কাছে আগামীর বাংলা সিনেমার প্রত্যাশা অনেক।

মুম রহমান একজন লেখক। সার্বক্ষণিক এবং সর্বঅর্থে লেখক। যা করেন লেখালেখির জন্য করেন। গল্প, নাটক, কবিতা, অনুবাদ, বিজ্ঞাপণের চিত্রনাট্য, রেডিও-টিভি নাটক, সিনেমার চিত্রনাট্য, প্রেমপত্র– সব কিছুকেই তিনি লেখালেখির অংশ মনে করেন। রান্নার রেসিপি থেকে চিন্তাশীল প্রবন্ধ সবখানেই তিনি লেখক।