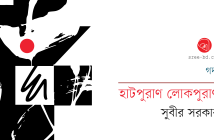রক্ষাকবচ
২৭ বছর বয়সের মধ্যেই নাকি একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী করতে পারবে না-পারবে সেটি ঠিক হয়ে যায়— রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি চিঠিতে পড়েছিলাম। লোকমুখে শুনতাম, ৩০ পার হওয়ার আগে কিছুই বলা যায় না। সুকান্ত, কীটসের মতো লোক ত্রিশের আগেই গত হয়েছিলেন। র্যাবো তো ত্রিশে পৌঁছানোর অনেক আগেই লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে এসব খুবই গোলমেলে কথা। একধরনের সংস্কার বলা যেতে পারে। কুসংস্কারও। কিন্তু মানুষের মন কিছু একটা অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। তার একটা মন্ত্র চাই। কোনো মানুষ জানেই না সে নিজের অজান্তেই কিছু একটাকে মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছে। এই মন্ত্র কারো জন্য বিকাশের সেতু তৈরি করে, কারো জন্য বিনাশের খাদ হয়ে দেখা দেয়। খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে যেকোনো সময় একটু এদিক ওদিক হলে তার পতন। লেখালেখি অনেকটা খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে দূরে সূর্যোদয় দেখার কাহিনি। কখনো অস্তাচলের দৃশ্যও তাকে দেখতে হয়।
কারো কারো মতে, এ এক শামুকের জীবন। শামুকবাস। যত চলে, ততই ক্ষয়ে যায়। একসময় সম্পূর্ণ ক্ষয়ে গেলে কেবল খোলটুকু পড়ে থাকে। ওই খোলটাই কি লেখকের লিখনকর্ম?
বহুবার লেখা ছেড়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এও মনে হয়েছে, লেখাটাই তো ধরিনি, ছেড়ে দেওয়ারইবা প্রশ্ন উঠছে কেন? লেখা এক অধরা মাধুরীর সন্ধান! ধরা দেয় তো দেয় না। সুন্দরী এত খেল খেলায়! একবার ধরা দেওয়ার আগে হাজারবার বাজিয়ে দেখে। রবীন্দ্রনাথ একেই ছলনাময়ী বলেছিলেন?
বহুবার লেখা ছেড়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এও মনে হয়েছে, লেখাটাই তো ধরিনি, ছেড়ে দেওয়ারইবা প্রশ্ন উঠছে কেন? লেখা এক অধরা মাধুরীর সন্ধান! ধরা দেয় তো দেয় না। সুন্দরী এত খেল খেলায়! একবার ধরা দেওয়ার আগে হাজারবার বাজিয়ে দেখে। রবীন্দ্রনাথ একেই ছলনাময়ী বলেছিলেন? অনায়াসে যে এই ছলনা সইতে পেরেছে তারই হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার?
লিখতে শুরু করার পর থেকেই ফরমায়েশি লেখাই (টেবিলে বসে কাগজ-কলমে বা কম্পিউটারে লিখছি কোনো একটা কিছু, এরকম সময় প্রায়ই আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, কী ওয়ার্ডারি লেখা? না নিজের লেখা?) লিখতে হয়েছে। নিজের প্রাণমন খুলে লিখতে পারলাম আর কোথায়?
১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এটা-ওটা ছাপা হতে শুরু করে। সবই গদ্য ধরনের লেখা। প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ঘোড়ারডিম টাইপের লেখাও বলা যেতে পারে। আগডুমবাগডুম। এর ভেতরে বলতে গেলে একেবারে শুরুর দিকে সিলেটের, সম্ভবত হবিগঞ্জের কোনো একটা সংস্থার স্মরণিকার জন্য আমার একটি গল্প ছাপা হয় ‘অনিবার্য অন্তর্ঘাত’ নামে। সেটিই আসলে প্রথম প্রকাশিত গল্প। এর আগে লুকিয়েচুরিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা চলেছে দিনের পর দিন। কবিতার পর কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছি খাতার পর খাতা। একটিও পাতে দেওয়ার উপযুক্ত মনে হয়নি। বিশ্বাস করবেন কি পাঠক ‘অনিবার্য অন্তর্ঘাত’ গল্পটি স্বপ্নে পাওয়া! আসলে স্বপ্নে কাহিনিটা পাওয়া হলেও ভাষা তো আর স্বপ্নে পাওয়া যায় না। (যদিও কেউ কেউ নাকি ভাষাও স্বপ্নে পেয়ে যাচ্ছেন বলে দেখতে পাচ্ছি!) ভাষাটা অনেক খেটেখুঁটে নির্মাণ করতে হয়। কৃত্রিম একটা কাণ্ড বৈকি! অনেকে অবশ্য এসব নির্মাণের ধার ধারেন না। তবে তারা হয়া, নিয়া, খায়া, লয়া জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে যখন লেখেন, তাও অকৃত্রিম নয়। কৃত্রিমের চেয়েও কৃত্রিম শোনায়। তবে এই অকৃত্রিমের ছদ্মবেশে কৃত্রিম থেকে কৃত্রিমতর তাদের এই ভাষা একদিন শিল্পসিদ্ধি এনে দেবে— এই প্রত্যাশা না করে পারি না। আমরা নিজের ক্ষেত্রে সংলাপ ছাড়া মূল বর্ণনায় এখনো পর্যন্ত এই জাতীয় অকৃত্রিম হয়ে ওঠার মন্ত্রণা তাদের মতো এখানো পাওয়া হয়নি।
‘নিজের ক্ষেত্র’ কি ‘নিজের জমিজমা’ তো আদতে ‘নিজের লেখা’। যতবারই ‘নিজের লেখা’র কথা ভাবি, ততবরাই মনে হয়, নিজের লেখা আর লেখা হলো কোথায়! এখনো ‘নিজের লেখা’ লেখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চলেছি। অথচ এর মধ্যে ১০টি তথাকথিত উপন্যাস (?) এবং ৪৯ টির মতো অযাচিত ছোটোগল্প লেখা হয়ে গেছে। সবই কোনো না কোনো পত্রপত্রিকায়। ৪টি উপন্যাস গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। আরও দুটো ছোটো ছোটো উপন্যাস নিয়ে একটি বই হতে পারে। বাদবাকি আপাতত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা নেই। ছোটোগল্পের বই এখানো করার কথা চিন্তা করিনি। প্রবন্ধ কত লিখেছি, তার কোনো হিসাব নেই। কিন্তু বই করার কথা ভাবিনি। কবিতা(?)— হঠাৎ হঠাৎ ২/৩ বছর পর পর একটা স্রোত আসে। তখন একটানা কয়েকদিন কবিতায় পেয়ে বসে। একটা পর একটা লিখে চলি। সপ্তাহখানিক এই ঘোরটা থাকে। তারপর আবার কেটে যায়। এর পর খুন করে ফেললে কি বোমা মারলেও একটি কবিতা আমকে দিয়ে লেখানো সম্ভব নয়। কেউ কেউ আমরা কবিতা দেখে ও পড়ে বলেছেন, অবশ্যই যেন বই করি— কিন্তু আমার মনে হয়েছে কী দরকার! কবিতা লেখাটা একান্তই নিজের জন্যই থাকুক না কেন!
সব লেখাই নিজের জন্য রাখতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু কবিতাকে আমার ঠিক নিজের লেখা বলে মনে হয় না, ‘নিজের লেখা’ মানে নিজের ক্ষেত্র বলতে যায় বোঝায়। গদ্যভূমিতেই আমার যাবতীয় চাষবাস করার ইচ্ছা। ফলে ওই যে ‘নিজের লেখা’ সেই জায়গাটায় যাওয়া এখনো বাকিই থেকে গেছে।
কদিন আগে কবি নূরুল হক আমার সামনে বসে একজনকে মোবাইল ফোনে বলছিলেন, ‘এখন যে কী সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। যখন নিজের জন্য লিখতাম, লিখে রেখে দিতাম। কোনো খেদ ছিল না। কী যে শান্তির জীবন ছিল! আর এখন বই বের হওয়ার পর একটা দুটো কবিতা এখানে ওখানে ছাপা হওয়ার পর এমন একটা জিনিস হলো— লেখা ছাপা হচ্ছে, কই কেউ কিছু বলছে না কেন? এমন অসহায় লাগে একটা লেখা ছাপা হওয়ার পর। এই যে লেখা, তারপর ছাপা হওয়ার পর কে কী বলল তার জন্য অপেক্ষা করা, সারাক্ষণ মনের ভেতর খচখচ। এর চেয়ে বাজে জিনিস আর হতে পারে না। এটা যে কত বড়ো সর্বনাশ— আমার মতো লোক ছাড়া কেউ বুঝে না।’
নূরুল হক বলতে গেলে বহুদিন থেকে লিখে আসলেও সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। আগে দু-একটা ছোটোকাগজে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এছাড়া তার কবিতা একরকম অগোচরেই পড়ে ছিল। প্রথম বই প্রকাশিত হওয়ার পর নানান লোকজন তাঁর কাছে কবিতা চাইতে থাকে। এবার একটু একটু করে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতাগুলো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কবিতা নিয়ে তো তিনি অন্যদের মতো কোনো মাতামাতিতে ছিলেন না। নীরবে নিভৃতে যেটুকু যখন পেরেছেন লিখেছেন। তাঁর মতে, সেই জীবনাটাই অনেক শান্তির ছিল।
জীবনানন্দ দাশ গণ্ডা গণ্ডা উপন্যাস ট্রাঙ্কে ফেলে রেখেছিলেন। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তও কম নেই যাতে মৃত্যুর পরই মূলত কোনো লেখকের লেখালেখির সিংহভাগ অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে সহজ উদাহরণ কাফকা। এভাবে লেখালেখিকে গোপন করাটা প্রকাশ করার চেয়েও বোধ হয় আরও বড়ো আনন্দের, নয় কি?
জীবনানন্দ দাশ গণ্ডা গণ্ডা উপন্যাস ট্রাঙ্কে ফেলে রেখেছিলেন। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তও কম নেই যাতে মৃত্যুর পরই মূলত কোনো লেখকের লেখালেখির সিংহভাগ অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে সহজ উদাহরণ কাফকা। এভাবে লেখালেখিকে গোপন করাটা প্রকাশ করার চেয়েও বোধ হয় আরও বড়ো আনন্দের, নয় কি? গোপনে নিভৃতে বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত কোনো নারীর সঙ্গে সময় কাটানোর মতোই কি এই সব লেখালেখি, অন্যদিকে যে নারী লেখেন তার কাছে তেমন কোনো কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গ এ।
যে লেখকটি গোপনে বেড়ে ওঠেন তিনিই তো সবচেয়ে ভয়ংকর লেখক? ‘তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে’— শিল্পের নামে চলা সমস্ত বদমায়েশি, সমস্ত জালচক্র ছিন্ন করে সেই লেখকের জন্য আমরা অপেক্ষাও করি।
নিজের ক্ষেত্রে সেই বেড়ে ওঠাটিকেও তো দেখার দরকার। ঠিক মতে পা ফেলছি কি না! কিন্তু এত মেপেজুখে কি লেখা যায়? লেখা তো কেবল লেখার নিয়ম মানে— আর কোনো নিয়ম নয়। এমন কি নিজেকেই নিজে বিদীর্ণ করে সমস্ত নিয়মকানুনশৃঙ্খল ভেঙে অন্যরকম কিছু হয়ে ওঠে। আর তা করা কারো কারো দ্বারা সম্ভব হয় বলেই সাহিত্যে নতুন যুগ আসে। আসে নতুন নির্মাণ, নতুন ভাষা।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর পেছনে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি থাকে। যারা অল্পতে সেটি করে উঠতে পারেন তারা সত্যিকারের প্রতিভাবান। কীটস, র্যাবো, নজরুল, সুকান্তের মতো এঁরা এক একটা ঘটনা। দীর্ঘদিনের এই প্রস্তুতিকে ‘লেখকের বেড়ে ওঠার দিনগুলি’ হিসেবে নাম দিলে আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি ঠিক মেলাতে পারি না, কোনখান থেকে নিজেরই এই বেড়ে ওঠাটাকে দেখা যেতে পারে? একেবারে শিশু বয়সে গল্প শোনা বা নিজে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার প্রবণতা যাদের থাকে, তারা ভবিষ্যতে লেখক হবেন— এমন ঘোষণা কেউ করতে পারে না। একটি বিরাট বাস্তবতা হলো— শিশু প্রতিভা কখনোই মহৎ প্রতিভা হয়ে ওঠে না, বরং মেধাবী কোনো মানুষে পরিণত হতে পারে সে। ডাক্তার-প্রকৌশলী-আমলা প্রভৃতি ধরনে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু প্রতিভাবান বা সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার সঙ্গে যে নিজেকে নিজের ঘাড় ধরে কাজ করানোর উদ্যম তা খুব কম লোকেরই থাকে।
লেখার পেছনে কখনো মনে হয় খ্যাতি, অর্থবিত্ত, সামাজিক মর্যাদা লাভের বাসনাও থাকে— কখনো প্রতিপত্তি, আভিজাত্য লাভ করার তাড়নাও। বালজাকের অন্তরের আকুতি ছিল, ‘ধন চাই, মান চাই ভালোবাসা চাই। লিখতে চাই না। লেখার হাত থেকে বাঁচতে চাই।’ কিন্তু তাকেই লেখার জন্য দানবিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আর তা করতে পেরেছিলেন বলেই সাহিত্যের জগতে বালজাক এক অতিমানবীয় লেখক।
কখনো স্রেফ নিজের আনন্দের জন্য লিখেছেন এমন লেখকও কম নেই। আবার শোনা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রান্তে থাকা লোকজনের কেউ কেউ লেখক হয়ে ওঠেন স্রেফ নিঃসঙ্গতা থেকে। লেখার পেছনে একেক সময় একেক তাড়নাও কাজ করে থাকতে পারে। কোনো কোনো সময় স্রেফ লেখার জন্যই লেখা। লিখে সময় পার করা মাত্র। কিন্তু যে-লেখক লেখার জন্য ‘কমিটেড’ (‘দায়বদ্ধতা’ শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি না) হতে পারেন না, নিজের খেয়াল খুশির ওপরে লেখাটা ছেড়ে দেন, তার দ্বারা কতটুকু লেখা হতে পারে? ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধ মানুষ এমন গা ছাড়া লেখালেখির পরই যেটুকু আমাদের দিয়ে গেছে, তারচেয়ে কি বেশি পেতাম না, যদি তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টিশীলতাকেই, নিজেকে নিজের হাতে অবিরাম ফলানো-কে জীবনের প্রধানতম কাজ করে তুলতেন? লেখালেখি নিয়ে কমিটেড হতেন? যদিও এসব প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু না-জেগে পারে না। কী করলে কী হতে পারত, আমরা তো এসব নিয়েই আছি, থাকি, এসব নিয়েই বাঁচি। নিজের বেড়ে ওঠার কেচ্ছা বলার চেয়ে নিজের লেখাটা নিয়ে গভীর ধ্যানে-অনুধ্যানে কোনো লেখককে থাকতে দেওয়াই তো মনে হয় অধিক স্বাস্থ্যকর।
প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, লেখককে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে হচ্ছে, পরিণতি কী দাঁড়াচ্ছে নিজের সময় তার বেশ কিছু নমুনা তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। এখন তো ঘোড়ার ওপর চড়ে লেখার দিন। লেখার চেয়ে কতটা এগুলাম, কত লোকে নাম জানল, কত লোকে সঙ্গে যোগাযোগ হলো— এখন তো সেই দিন। শঙ্খ ঘোষ লেখেন—
‘ধ্বনি আর রঙে মিলে নিরঞ্জন শ্বাস
কিছু উড়ে চলে যায় কিছু পড়ে থাকে—
নিজেকে কি জানো তুমি? কতটুকু জানো?
তুমি তা-ই, মিডিয়া যা বানায় তোমাকে।’
(‘শিল্পী’, ছন্দের ভিতর এত অন্ধকার, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৮৬)
অভিজিৎ সেন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, লেখকের খ্যাতিমান হয়ে ওঠাটা এখন সর্ম্পূণই প্রচার-বাণিজ্যের হাতে। এর সঙ্গে ভালো লেখার সম্পর্ক কম। তাই লেখালেখির নামে যারা খ্যাতি চান তারা মিডিয়ার দিকে ভিড়ে যান। তারাই বুদ্ধিমান। লেখালেখির চেয়ে তাদের কাছে দেখাদেখিটাই মুখ্য। সেটাও আমাদের অনেকের বেড়ে ওঠার গল্পের আদরা কাহিনি। খসড়া কাহিনি তো জীবনানন্দের মতো ট্রাঙ্কে পুরে রাখা ছাড়া উপায় নেই।
আমরা এখনো খসড়া খাতায়। বিশেষ করে আমি নিজে। আঁকিবুকি চলছে, হিজি-বিজি-বিজ্। কিছুই হচ্ছে না। তারপরও লিখতে হচ্ছে। লিখতে লিখতে কতটা বেড়ে উঠছি, তার বিচার করা হচ্ছে না। তাই প্রচারেও নামা হচ্ছে না। আগে তো বিচার, তারপর প্রচার। তাই তো হওয়া উচিত। অবশ্য সময় বরাবরই লেখকের জন্য উল্টোরথে-উল্টোস্রোতে চলে। তিনি এদিকে, তো হাওয়া বইছে আরেক দিকে। এই হাওয়া ও স্রোতের বিপরীতে যতদিন, ততদিনই তিনি লেখক— নইলে কিছুই নন— একথাও আজ আর জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আমরা কজন বেড়ে উঠতে পারি এই স্রোতের বিপরীতে? কী লেখককে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে? লেখকের তো কোনো রক্ষাকবচ নেই। নিজেকে অবিরাম বিপন্ন করে যাওয়া আর ঝুঁকির মুখে না রাখলে কোনো লেখক কি তাঁর লেখক সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন? লেখা নিজেই তো এক ও অনন্য আত্মরক্ষার প্রতিবেদন।
মানুষ ও জীবনকে নিয়েই তো লেখা— সেই লেখা আমাদের জীবিকার পাতা নানান ফাঁদে, কখনো ফোকরে হারিয়ে যায়। এতটাই ক্ষুদ্র আমরা যে ওই ক্ষুদ্র ফোকরের ভিতর দিব্যি এঁটেও যাই। মিলে যায় খাপে খাপ। লেখা আর হয়ে ওঠে কোথায়? লেখার প্রস্তুতি চলে মাত্র। এই প্রস্তুতি নিতে নিতেই দিন যাচ্ছে। বেড়ে উঠছি!— বলা মুশকিল, বরং দিনে দিনে আরও বামন হয়ে যাই কি না— সেই আশঙ্কায় পরানের গহীন ভেতরে কে যেন হো হো করে অট্টহাসি হেসে ওঠে। তার সে-হাসি নিত্যই শুনতে পাই।
ললাটলিখন
নিয়মিত লিখতে বসাটাই লেখকের একমাত্র ললাটলিখন হওয়া উচিত। এছাড়া অন্য কোনোকিছুর নিয়ন্ত্রণ তিনি মানুন আর না মানুন, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। লেখার অন্যতম উপাদান স্মৃতি। আরও বড়ো করে দেখলে ইতিহাস। জাতির জীবনে যা ইতিহাস প্রত্যেক লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে তা-ই স্মৃতি। স্মৃতি কেবল স্মৃতিই নয়, তা একধরনের শ্রুতিও। বেদ-এর নাম যেমন শ্রুতি ছিল। কারণ তা লেখার জন্য তখনও বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয়নি। গুরু পরম্পরায় শিষ্যরা তা শুনে শুনে আত্মস্থ করত। লেখকেরও একটা নিজস্ব বেদ থাকে। এর নাম সংবেদ। ‘সেন্স’ এবং ‘নলেজ’ মিলে এর সৃষ্টি। তবে সংবেদশীলতা বড়ো লেখকের বড়ো গুণ। সাধারণ লেখকের কাণ্ডজ্ঞান হলেই চলে। তিনি কী লিখবেন, কেন লিখবেন, কীভাবে লিখবেন, ন্যূনতম ব্যাপার হলো যা লিখবেন তা বুঝে-শুনে লিখবেন— এই কাণজ্ঞান যার আছে, তিনি আসলে লেখক হয়ে উঠতে পারেন। এই কাণ্ডজ্ঞান যে-লেখক যতভালো মতো কাজে লাগাতে পারেন, তার লেখা ততটাই গুণগত মানে ও পরিমাণগত মানেও ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। নিয়মিত লিখতে বসা সেই কাণ্ডজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে কয়েকদিন ভোরবেলা প্রশান্ত মৃধার সঙ্গে হাঁটতে বের হতাম। ঘুরেফিরে শিল্প-সাহিত্য নিয়েই কথা হতো। একদিন বললেন, ‘লেখার অর্ধেকটা হলো লিখতে বসা।’ একটু থেমে এর সঙ্গে যোগ করলেন,‘এদেশের লেখকরা যদি প্রতিদিন দুঘণ্টার জন্য লেখা হোক না হোক লেখার জন্য টেবিলে বসতেন তাহলেই এদেশের সাহিত্যের চেহারা পালটে যেত।’ বোধ করি অমিয়ভূষণ মজুমদারই কোনো একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘লেখক একজন কাপালিক। তাকে নিয়মিত তন্ত্রে বসতে হয়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে কয়েকদিন ভোরবেলা প্রশান্ত মৃধার সঙ্গে হাঁটতে বের হতাম। ঘুরেফিরে শিল্প-সাহিত্য নিয়েই কথা হতো। একদিন বললেন, ‘লেখার অর্ধেকটা হলো লিখতে বসা।’ একটু থেমে এর সঙ্গে যোগ করলেন,‘এদেশের লেখকরা যদি প্রতিদিন দুঘণ্টার জন্য লেখা হোক না হোক লেখার জন্য টেবিলে বসতেন তাহলেই এদেশের সাহিত্যের চেহারা পালটে যেত।’ বোধ করি অমিয়ভূষণ মজুমদারই কোনো একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘লেখক একজন কাপালিক। তাকে নিয়মিত তন্ত্রে বসতে হয়।’ কদিন আগে সমরেশ বসুকে নিয়ে শীর্ষেন্দুর একটি লেখা পড়ি। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শীর্ষেন্দুকে তাঁর তরুণ বয়সে একবার বলেছিলেন, ‘শোন, প্রতিদিন লিখতে বসবি। লিখতে বসাটাও লেখকের ধ্যান। দেখিস না সমরেশ প্রতিদিন লিখতে বসে। এজন্য লেখাও হয় প্রচুর।’
লেখা ও লেখক নিয়ে কে কী বলেন তার জন্য কান খাড়া করে রাখি প্রতিক্ষণ। লেখকরা কী করে লেখাকে লেখা করে তোলেন। লেখক বলতে তিনি তলস্তয় হোন কি রবীন্দ্রনাথ কি মফস্বলের সদ্য কবি হয়ে ওঠা তরুণ-তরুণী, প্রত্যেকেই কী করে লেখেন— এতে আমি অদম্য আগ্রহ বোধ করি। কিন্তু জনে জনে— আপনি কীভাবে লেখেন? কখন লিখতে বসেন? একটানা কতক্ষণ লিখতে পারেন?— এসব প্রশ্ন করা যায় না। অনেক পরে প্যারিস রিভিয়ুর সাক্ষাৎকার নিয়ে ম্যালকাম কাউলের ‘রাইটার্স অ্যাট ওয়ার্ক’-এর অনুবাদ ‘লেখকের কথা’ [জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং ফখরুজ্জামান চৌধুরী অনূদিত, বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত] পড়ে লেখালেখির রহস্যের কিছু কিছু দিক পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ফকনার যেমন বলেছিলেন, ‘অন্যরা কে কত ভালো লিখল সেদিকে নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। নিজের চেয়ে ভালো লেখাটাই লেখকের প্রধান স্বপ্ন হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই তাকে কাজ করে যেতে হবে। লেখক এক অদৃশ্য দৈত্যের তাড়নায় শিল্প সৃষ্টি করেন। সেই নির্দেশ না মেনে তার আর কোনো উপায় থাকে না। সব বাদ দিয়ে কেন যে ওই দৈত্য তাকে বেছে নিল সেটুকু ভাবার সময়ও লেখকের নেই, দরকারও নেই। কি চুরি করে, কি ডাকাতি করে কি ভিক্ষা করে হলেও লেখককে ওই দৈত্যের আদেশ পালন করতে হবে।’ ফকনারের সাক্ষাৎকার পড়ে মনে না হয়ে পারে না যে, তিনি মূলত আত্মজিজ্ঞাসাকেই লেখকের একমাত্র সহায়তাকারী বলে শনাক্ত করতে চান। আমি আসলে লেখক কি না, যদি হয়ে থাকি তো আমি কী লিখছি, কীভাবে লিখছি— এগুলোই একজন লেখকের প্রধান বিবেচনা হতে পারে।
ফলে নিজেকে প্রশ্ন করাটাই সবচেয়ে জরুরি। আর সেই প্রশ্নের উত্তর আছে অতীতে তথা স্মৃতিতে, বর্তামনের আমি কেবল তার ফলশ্রুতি মাত্র (কীভাবে কীভাবে যেন আমি একজন লেখক এই প্রচারণা কম করে হলেও ছড়িয়েছে। সঙ্গে আরও ছড়িয়েছে, আমি নাকি নিয়মিত লিখতে বসি।) কিন্তু আমি বর্তমানে আমার সম্পর্কে এই ‘নিয়মিত লিখতে বসার ব্যাপারটি’র প্রশ্নে খুবই হতাশ হই। নিয়তিম লিখতে তখনই বসা হয়, যখন একগাদা ফরমায়েশি লেখার তাগাদা থাকে। কেউ ফোন করে, কী সামনা সামনি লেখা চাইলে, যদি শক্তমতো কথা দিয়ে থাকি, তাহলে তাকে লেখা না দিয়ে পারিনি। কিন্তু টের পেয়েছি, নিয়মিত এই লেখার মানে ‘নিজের লেখা’ নয়। ফরমায়েসি লেখা ‘নিজের লেখা’র ক্ষতি করে না উপকার করে সে তর্কে যেতে চাই না। বহুবার চেষ্টা করেছি এরকম ফরমায়েসি লেখা আর লিখবো না। অন্যের চাপে বা তাগাদায় কোনো লেখা লিখব না। মাঝে মাঝে কারো কারো মুখের ওপর ‘না’ যে বলিনি তা তো নয়, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারিনি। ফরমায়েশের পর ফরমায়েশের দাবি পূরণ করতে হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী দুয়েকজন আমাকে তীব্রভাবে এসব ফরামায়েশি লেখা লিখতে নিষেধ করেছেন, দুদিন যেতে না যেতে তাদের পক্ষ থেকেই এসেছে ফরমায়েশি লেখার তাগাদা। আমি তাদের কথা ফেলতে পারিনি। এই করতে করতে ‘নিজের লেখা’র জন্য বসতেই পারিনি। নিজের লেখা মানে গল্প-উপন্যাস লেখা। ব্যক্তি বা বিষয় উপলক্ষ্যে লেখা প্রবন্ধের বদলে এমন কোনো বিষয় যা আমাকে ভাবায়, সেসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখাও নিজের লেখা— সেইসব লেখা লেখা হয়ে ওঠে না। ছাপাছাপির জন্য নয়। নিজের মনে জেগে ওঠা কবিতার মতো কিছু একটা— এর জন্য সময়ই দেওয়া হয় না।
তরুণ লেখকদের একটি বিপদ ডেকে আনেন সম্পাদকরা। তাদের ধরিয়ে দেন গ্রন্থ-আলোচনা। গ্রন্থ-আলোচনাকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি; কিন্তু এও মনে করি— গ্রন্থালোচনা করানো উচিত প্রবীণ লেখকদেরকে দিয়ে। লিখে লিখে ঝানু, প্রচুর পাঠ ও অভিজ্ঞতা যাদের আছে, প্রচুর তুলনা ও ক্রশরেফারেন্স যাদের টানার সাধ্য আছে তাদের দিয়েই গ্রন্থ-আলোচনা করানো দরকার। যাই হোক প্রচুর গ্রন্থালোচনা আমাকেও লিখতে হয়েছে। লিখে যে আমি আনন্দ পাইনি তা তো নয়। তারপরও মনে হয় একটা অদৃশ্য চক্রে পড়েই কাজটা করেছি, পরে টের পাই সেই চক্রটি হল— আলোচনার জন্য বই নেওয়া, বিনা পয়সায় বই পড়া আর আলোচনা ছাপা হলে কিছু টাকা— যা দিয়ে দুতিনটা পছন্দের বই কেনা।
আগে ঈদের মৌসুম এলে কোনো কোনো সম্পাদক আমার কাছে উপন্যাস চাইতেন। প্রায় ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা কোনো একটা লেখাকে তখন উপন্যাসের আকার দিতে বসে যেতাম। এইভাবে নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছি। কারণ এসব লেখার কোনোটাকে নিজের লেখা মনে হয় না। আর এভাবেই এতদিন যা লিখেছি এমনকি এই যে লেখাটি লিখছি তাও অন্যের তাগাদায় লেখা। অন্যের উস্কানি ছাড়া নিজের লেখা লিখতে আজো বসা হল না— এমন একটা ধারণা আমার মনেরও মধ্যেও প্রায় গেড়ে বসেছিল। তখন স্মৃতির পাতা থেকে উত্তর এলো। না আমিও একসময় ঘড়ি ধরে নিয়মিত লিখতে বসতাম। সেই স্মৃতিটা যার-পর-নাই দামি। কিন্তু আমি নিজেই প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম যে তেমন কোনো স্মৃতি আমার ছিল কি না।
তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। প্রথম বর্ষ থেকেই একটুআধটু লেখা চলছে। দেয়াল পত্রিকা, ভাঁজপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেসবের কিছু কিছু। প্রচুর কবিতা লিখেছি সেসময়। তার মান বা রুচি কোনোটাই বিচার করিনি; কেবল লিখে গেছি যখন যা মনে এসেছে। অনেক পরে আমার বন্ধু আসাদ আহমেদের কাছে একটি কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছি। এক তরুণ তাঁর শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিল, ‘কীভাবে লিখব স্যার?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘যদি লিখতে চাও, উইথদাউট এনি হেজিটেশন লিখতে শুরু করে দাও। স্রেফ লিখতে থাক। কী হলো না হলো পরে দেখা যাবে। একদিন লেখা ধরা দেবে।’
আমি নিজেই এক অগ্রজকে প্রশ্ন করেছিলাম যে— তিনি কী করে লেখেন। তিনি জীবনানন্দ দাশের ‘বোধ’ কবিতার কটা লাইন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন,
‘আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে।
আমি থামি,—
সে-ও থেমে যায়;’
লেখালেখির মূল পদ্ধতি এটাই। লেখাটা বোধের ব্যাপার। একবার শুরু করলে তা মাথার চারপাশে, চোখের চারপাশে, বুকে চাপপাশে কেবল ঘুরে চলে, তখন লেখা শুরু করলেই লেখা শুরু হয়ে যায়, থামিয়ে দিলেই সে নিজে থেমে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায়ও এর সায় আছে। রবীন্দ্রনাথও একবার বলেছিলেন, তিনি কী থেকে কী লেখেন নিজেও ঠিক জানেন না, তার কাছে এটাই লেখালেখি করার ও লেখার ভেতরে থাকার একমাত্র উপায় মনে হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই আমার বন্ধুদের প্রায় সবাই কবিতা লিখেছে। ছাপাও হয়েছে। শামীম রেজার কবিতা ছাপ হলো শিবনারায়ণ রায়ের ‘জিজ্ঞাসা’ পত্রিকায়। এ নিয়ে আমাদের উৎসাহ আগ্রহের শেষ নেই। আসাদ আহমেদ নিয়মিত কবিতা লিখলেও ছাপার ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। কবি হিসেবে তার নাম ছড়িয়েছে। শামীম রেজা ও রনজু রাইমের গল্প-কবিতা ছাপা হলো সরকার আশরাফের ‘নিসর্গে’র মতো ছোটোকাগজে। অন্যদিকে আমাদের একক্লাস ওপরে পড়া প্রশান্ত মৃধা একেবারে পাকাপোক্ত লেখক। আমার খুব কাছ থেকে দেখা প্রথম গদ্য লেখক। তার কাছে লেখালেখির অনেক সহবত বা এটিকেইট শেখার চেষ্টা করেছি: নিজের লেখা নিয়ে নীরব থাকা। নিজের ঢোল নিজে না পেটানো। লেখা প্রকাশিত হলে এই নিয়ে লোকজনকে না জানানো, এমনকি নিজের বাবামাকেও। কেউ পড়ে কিছু বললে বলল, না বললে না বলল।— তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কি দেবেশ রায়ের এই নিয়ে নির্মোহতার কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে টানতেন। আর হরদম তাঁর কাছে জানতাম কাদের বই পড়ব, কোন বই পড়ব।
এই-ই চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দুই বছরে কিছুটা ওই কবিতা লেখার বাই পেয়ে বসলেও দিনে দিনে তা থিতিয়ে যেতে শুরু করে। লেখার চেয়ে পড়ার মাত্রা বেড়ে যায়। তাও যে খুব বেড়েছিল সেরকম কিছু না। তারপরও রটে গিয়েছিল আমার ভেতরে লেখালেখি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ, একদিন আমি সত্যিই ভালো কিছু লিখব। আমার সমানেই প্রশান্ত মৃধা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিতলায় মাসুদুল হককে বললেন, ‘হামীম কিন্তু গোপনে গোপনে লেখে। কাউকে কিছু বলে না, দেখায়ও না।’ মাসুদুল হক বললেন,‘দেখবে, এই রকম লেখকরাই একদিন ভালো একটা কিছু লিখে ফেলেছে।’ এসব কথা মনে পড়লে আজো পুলকিত হই, কিন্তু তার কোনো নমুনা আজো অবধি দেখা গেল না— তা-ই মনে মনে নিজেকে নিয়ে হাসি।
যাই হোক তৃতীয় বর্ষও শেষ। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছিল। তখন ঠিক করি, নাহ্, অনেক হয়েছে। এবার থেকে নিয়মিত লিখতে বসব। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমার লেখা’ নামের একটা প্রবন্ধসহ আরও কিছু লেখা পড়ে কেমন একটা অনুপ্রেরণা জাগে। আসলে দুজন লেখক— একজন সমরেশ বসু, আর অন্যজন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়— প্রথম জন লেখাটাকে একটা অন্তহীন লড়াই হিসেবে, পরের জন একটা জেদি একরোখা ব্যাপার হিসেবে আমার কাছে দাঁড় করিয়েছিলেন। সমরেশের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। লেখার মালমশলা পেতে তার কোনো সমস্যা হয়নি। অন্যদিকে শ্যামলের নাকি কিছুই জানা ছিল না, কি জীবন সম্পর্কে, কি লেখালেখি সম্পর্কে।
যাই হোক, এবার কবিতা বাদ দিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রতিদিন দুপুরে হলটা নীরব হয়ে ওঠে। আমার রুমমেট সারোয়ার ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। গভীর রাতে রুমে আসে। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। আমি রাত দশটা এগারোটার ভেতরে ঘুমানো আর ভোরের দিকে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করেছিলাম। ফলে ওর সঙ্গে দিনের বেলা আমার দেখাই হতো না প্রায়। অন্যদের রুমমেট নিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল জানি না, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটানো ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল অবধি সাত বছরের ওর সঙ্গে আমার ন্যূনতম কথাকাটাকাটিও হয়নি। অদ্ভুত একটা বোঝাপড়া ছিল বোধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সময়টায় দিনের অল্প কিছু সময় ছাড়া ওর সঙ্গে কথাবার্তাই হতো না। ও সারাদিন পুরো ক্যাম্পাস টো টো করে ঘুরে বেড়াত। খুবই মজার মানুষ ছিল। কথায় কথায় লোকজনকে হাসিয়ে পেট ব্যথা করে দিতে পারত। এজন্য সর্বমহলে ওর বিরাট জনপ্রিয়তা। দুপুরে রুমে প্রায়ই থাকত না। আমিও দেখি দুপুরবেলাটাই লেখালেখি করার মোক্ষম সময়। শ্যামলও দুপুর বেলা লিখতে বসতেন। তাঁর মতে, জেদ ও অপমান— এই দুই-ই নাকি লেখককে লেখক বানিয়ে তোলে। আমার জেদটা থাকলেও অপমান জাতীয় কিছু ছিল কি না জানি না। স্রেফ লিখতে পারি কি না— এর একটা পরীক্ষা নিজের কাছে নিজের দেওয়ার দরকার বোধ করছিলাম। আর তা-ই চলছিল।
শ্যামলও দুপুর বেলা লিখতে বসতেন। তাঁর মতে, জেদ ও অপমান— এই দুই-ই নাকি লেখককে লেখক বানিয়ে তোলে। আমার জেদটা থাকলেও অপমান জাতীয় কিছু ছিল কি না জানি না। স্রেফ লিখতে পারি কি না— এর একটা পরীক্ষা নিজের কাছে নিজের দেওয়ার দরকার বোধ করছিলাম। আর তা-ই চলছিল।
দেখতে দেখতে কয়েকটা প্যাড সমাপ্ত-অর্ধসমাপ্ত ছোটোগল্পে ভরে ওঠে। কিন্তু একটাও কারো পাতে দেওয়া বা কোথাও পাঠানো তো দূরের কথা ঘনিষ্ঠ কাউকে পড়তে দেওয়ার সাহস পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। এর কিছুদিন পরে শুরু হল উপন্যাস লেখার চেষ্টা। সেই পুরোনো সূত্রে— কবিতা-ছোটোগল্প দুই-ই লিখতে ব্যর্থ হয়ে উপন্যাস লেখার দিকে এগুলাম। ঠিক করি প্রতিদিন কমপক্ষে চার পৃষ্ঠা করে লিখব। সে অনুযায়ী বেলা ঠিক দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা অবধি লেখার টেবিলে কাটতে থাকে। একেবারে ঘড়ি ধরে। কোনো কোনো দিন বাদ গেলে সন্ধ্যায় ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে লেখার দাবি পূরণ করার চেষ্টা করেছি। এভাবে মাত্র পয়তাল্লিশ দিনে একশো আশি পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যায়। আমি তো অবাক। কী লিখেছি— কোনোদিন পড়েও দেখিনি। কিন্তু স্রেফ চারপৃষ্ঠা লিখবোই যেভাবে হোক এই পণ রাখা হচ্ছে কি না তাই খেয়ালে রেখেছি। লেখা ২০০পৃষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে। হঠাৎ একদিন চারটা কি পৌনে চারটার দিকে দরজায় টোকা। মজার ব্যাপার এতদিনের একদিনেও কেউ দেখতেও আসেনি আমি এসময় কী করি। ‘হামীম ভাই আছেন?’ মাহবুব মোর্শেদের গলা। আমি কোনোমতে লেখার কাগজগুলি সরিয়ে দরজা খুলি। ও ঢুকেই জিজ্ঞাসা করে, ‘কী করতেছেন?’ বলতেই চাইনি তবু মুখে অদ্ভুতভাবে এসে গেল, ‘উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি।’ ও কিছুক্ষণ বসল। তারপর মাহবুব যাকে যাকে বলা যেতে পারে তাদের ভেতরে রাষ্ট্র করে দেয় যে, হামীম ভাই উপন্যাস লিখছে। কথাটা সত্যি কি না আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞাসাও করে। তার ভেতরে প্রশান্ত মৃধাও একজন, ‘কী হামীম! তুমি বলে উপন্যাস লিখতিছো?’
অদ্ভুতভাবে সেদিনের পর থেকে আমি অনেকদিন আর সেই ঘড়ি ধরে লিখতে বসতে পারিনি। হঠাৎ হঠাৎ, তাও ৯/১০ দিন পর, কি ১৫/২০ দিন পর, এক অনুচ্ছেদ কি ১-২ পৃষ্ঠা লিখি। এরপর যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, অল্পই সময় ছিল এম.এ পাশ করার, বলতে গেলে সেভাবে আর নিয়মিত লিখতে বসা হয়নি। এম. এ পরীক্ষা দিলাম। পাশ করার অল্প কদিন পরেই বিয়ে হয়ে গেল পাক্কা বেকার অবস্থায়। আসলে ‘হয়ে গেল’ আর ‘করে ফেললাম’ দুটো মিলিয়ে। বৌয়ের বিএ পরীক্ষা শেষ হলে আর আমার এম,ফিল শেষ হলে তবে সংসার শুরু হবে। তাই দুজনে আলাদা থাকি। লেখালেখি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বলা যায়। অসমাপ্ত সেই উপন্যাস, ব্যর্থ গল্প-কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলো নাড়াচাড়া করার সময় পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। তবে বই পড়া আর বই কেনা চলতে থাকে। হঠাৎ একদিন পল্টনের ফুটপাত থেকে সমরেশ বসুর ‘শ্রীমতি কাফে’ কিনি। বইটা পড়তে পড়তে বহুদিন পর লেখার তীব্র ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে। এবার দিনে নয়। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে রাতে বাসায় ফিরি। বাবা মা ঘুমিয়ে পড়লে প্রতিদিন লিখতে বসি। ঠিক আগের মতো প্রতিদিন ৪ পৃষ্ঠা। দেখতে দেখতে ৫০০ পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যায়, কিন্তু নিশ্চিত জানি এটা একেবারেই কিছু হয়নি। তারপর আবার ভাবি, নাহ্, অনেক হলো, লেখালেখি ছেড়ে দেব, আমাকে দিয়ে একম্ম হবার নয়। বৌ ঘরে তুলে আনি। ঠিক এসময় শাহবাগের গ্রন্থনিলয় নামের দোকানে (এখন দোকানটা নেই, জয়নুল আবেদীন নামের এক ভদ্রলোক এর মালিক ছিলেন, দেকানে গেলেই তার সঙ্গে ছোটোখাট আড্ডা হয়ে যেত) “টলস্টয়’স ডায়েরিস”— আর. এফ. স্ক্রিটিয়ান-এর সম্পাদিত, বইটা পেয়ে দুই কিস্তিতে বইটি কিনি। আর এর কয়েকদিন পরেই নীলক্ষেত থেকে রাদুগা পাবলিশার্স, মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদে তলস্তয়ের একটা বই জোটে। এতে একসঙ্গে ছিল দুটো বই— ‘টেলস অব সেবাস্তোপল’ ও ‘দ্য কসাকস’। সেই বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপে লেখা, ‘টু লিভ অ্যান অনেস্ট লাইফ ওয়ান মাস্ট প্ল্যাঙ্গ ইনটু থিংস, গেট ইনভলব্ড, এনটেঙ্গলড, মেইক মিসটেকস, গিভ আপ অ্যান্ড স্টার্ট এগেইন, দেন গিভ আপ ইয়েট এগেইন বাট স্টিল কিপ অন ফাইটিং অ্যান্ড সাফারিং। পিস অব মাইন্ড ইজ মিনিংলেস অব সোল।’ এই কটি কথা আমাকে নতুন করে সচকিত করে তোলে। তাহলে তো খুব ভুল কিছু করে বসিনি। অন্যদিকে, সেই ডায়েরি পড়তে পড়তে আমার দিনগুলো আবার নতুন দিকে মোড় নেয়। লেখার জন্য আমি আবার ঘুরে দাঁড়াই। এগিয়ে যাই লেখার টেবিলের কাছে।
জিয়নকাঠি
পথটা কী? What is the way?
এগোও! Go!
— জেন ভাবনা
পাঠ, পথ, শপথ, স্ব-পথ এই কয়েকটি কথার ভেতরে কোথাও মিল আছে, হয়তো একটা পরম্পরাও আছে। পাঠই পথ— এমনটা মনে করতে পারলে ভালো বোধ করতাম, কিন্তু তা তো নয়। পড়া দিয়ে সব সম্ভব নয়। কাজ চাই। পড়লে কাজটা জুতসই হতে পারে। যে-কাজের পেছনে জ্ঞান নেই, সেই কাজ তো ভয়ংকর। জ্ঞান কী? মানুষের কল্যাণে যা কাজে লাগে, কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগে।— এভাবে দেখতে চাই। সরাসরিভাবে। যা কিছু ক্ষতিকর, তা-ই অজ্ঞান ও মূর্খতা। দার্শনিক-ভাবুক জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তির মতে, জ্ঞানী লোক কখনো খারাপ লোক হতে পারে না, খারাপ লোক জ্ঞানী হতে পারে না। জ্ঞানী কিন্তু খারাপ লোক, সে আসলে জ্ঞানী-ই না। সেই ‘দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য’ কথাটাই বলেছেন তিনি।
পড়ার ভেতর দিয়ে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে প্রজ্ঞার স্তরে, দ্রষ্টার স্তরে নিতে পারলে কাজ হয়। কাজ নিজে না করেও অন্যকে দিয়ে করানো যায়। গুরুরা কাজ করেন না। তাঁদের শুধু কথা আর কথা। সেই কথায় প্রাণিত-অনুপ্রাণিত হয়ে কত কত মানুষ কাজ করে। সফলতা বিত্ত বৈভব সুখ শান্তির চূড়ায় ওঠে। আর পাঠ মানুষকে পোড়াতেই থাকে। দগ্ধ করে। এই দগ্ধানিতে কেউ কেউ পড়ে পড়ে বিদগ্ধ হয়।
আমার সমস্ত পড়াকে একটা কাজে লাগতে চাই সেটা হলো লেখা। পড়াটা ও লেখাটা যদি ভালোভাবে বাঁচবার পথ তৈরি না করে দেয় তো পড়ে কী লাভ, তাও ভাবি। বছরখানিক আগে পেয়েছিলাম ‘রাইট লাইক হেমিংওয়ে’। বইটির লেখক আর. অ্যান্ড্রু উইলসন। নির্ঘণ্ট আর ছোট্টকরে লেখক পরিচিতি মিলিয়ে ২৫৫ পৃষ্ঠার বই। পুরো বইটা মূলতই হেমিংওয়ের লিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে। বেশ সুখপাঠ্য বই। কিন্তু পড়া হয়েছিল ১২২ পৃষ্ঠা। তারপর এদিক-ওদিক গিয়ে আর এ বই ধরা হয়নি, তাই পড়াও হয়নি। সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি রিচার্ড কোহেনের লেখা ‘হাউ টু রাইট লাইক টলস্টয়’। এ বই কেবল তলস্তয় নয়, বিশ্বের বিখ্যাত অনেক লেখকের লিখন ও পঠন-অভিজ্ঞতা নিয়ে। ঠিক এর আগে আগে পাই রোবের্তো বোলানিয়ো-র ‘২৬৬৬’ উপন্যাসটি। ৮৯৩ পৃষ্ঠার বিশাল বই। প্রতিটি পৃষ্ঠায় গড়ে ৪০০ শব্দ হলে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ শব্দের বই। পড়তে শুরু করে ছাড়তে পারছি না। ধুমসে পড়া হচ্ছে, তাও না। এক দু-পৃষ্ঠা পড়ে রেখে দিই, ফের হাতে তুলে নেই। এর ভেতরে অন্যান্য বই থেকে ঘুরে আসার কাজ হয়। এবং যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চাশটি গল্প’ বা অ্যান্থনি বার্জেসের ‘আর্থলি পাওয়ার্স’।— এগুলো সবই আকারে বড়ো বই। বিশাল বই। তবে বিশাল বিরাট বই পড়ার একটা উপায় অনেক দিন পর বের করতে পেরেছিলাম। সেটা হলো— বিরাট বই দেখে পাহাড় ডিঙাবার ভয় না পেয়ে, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে নয়, পরিচ্ছেদ ধরে ধরে নয়, পড়তে হবে অনুচ্ছেদ ধরে ধরে, ‘এখন আমি এই অনুচ্ছেদটা পড়ে শেষ করব’, অর্থাৎ একটা পৃষ্ঠার অর্ধেক বা একটা একটা পাতা করে পড়ে এগুনো। বিন্দু বিন্দু জল পান করে মহাসাগর পান করা।
বিচিত্র বিষয়ে আমার আগ্রহের জন্য পড়াটা সব সময় একই খাতে বয় না। পড়ে আছে দস্তয়েভস্কির ‘দ্যা ব্রাদার্স কারামাজভ’। সেও প্রায় ৯৩৬ পৃষ্ঠার বই। পড়েছি মাত্র ৩৫০ পৃষ্ঠা। ২০০৩-৪ সালের দিকে এই বইটি পড়েছিলাম কন্সটান্স গার্নেটের অনুবাদে। এখন পড়ছি অ্যান্ড্রু আর. ম্যাকান্ড্রু-র অনুবাদে। প্রথমবার পড়ার সময় এর ৬৫ পৃষ্ঠার মতো অনুবাদও করেছিলাম। সেটা জীবন-জীবিকার নানান ফাঁদে পড়ে আর এগোয়নি। শুনেছিলাম, উপন্যাস পড়ার নিয়মই এ-ই। অনেকটা পড়ার পর রেখে দেওয়া। তারপর অনেকদিন পর আবার হাতে তুলে নেওয়া, ততদিনে অনেক কিছুই ভুলে গেছেন, আবার পড়তে পড়তে মনে পড়বে, কিছুদূর পড়ার পর ফের রেখে দেওয়া, তারপর আবার মাস দুতিন পর হাতে নেওয়া। এই ধারায়ই পড়তে হয় উপন্যাস। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ক্ল্যাসিক জাতের বই একটানা না পড়লে আর পড়াই হয় না। পড়াতেও নানা মুণির নানা মত। তবে কী করে সত্যিকারভাবে একটি বই পড়তে হয়, সেটা শিখতেই এক জীবন লেগে যেতে পারে।
এখানে আসলে সম্প্রতি পড়া কিছু বইয়ের কথাই বলছি বা বলতে চাইছি। সব যে বলছি, তাও নয়। এর বাইরেও থেকে যাচ্ছে আরও বই। য়ুজেন ইয়োনেস্কো-র ‘ম্যাকবেত’ পড়লাম কদিন আগে। এতে থাকা ‘ভালোবাসাই সবকিছুকে পরাজিত করে’ কথাটির বিপরীতে ‘ভালোবাসাকে সবকিছু পরাজিত করে’— দুম করে অনেক কিছুকে চিনিয়ে দেওয়ার চাবিটা হাতে তুলে দেয়।
এভাবে কিছু বইয়ের একটা দুটো কথা, কখনো কখনো মাত্র একটা দুটো শব্দ জীবনের অন্য মানে তৈরি করে দিতে পারে। এজন্য পড়ার ভেতর দিয়ে নতুন করে ভাঙা-গড়া বার বার। পড়া তবু শেষাবধি আমার এই ছোট্ট জীবনের জিয়নকাঠি।
বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটা তো ‘গীতবিতান’, নয় কি? তাঁর গানগুলি পড়ে কত কত বার মিইয়ে যাওয়া দশা থেকে ফের দারুণ রকমের তাজা হয়ে উঠেছি। পড়া তাই জিয়নকাঠির মতো। পড়ার ভেতর দিয়ে ‘স্পিরিটেড’ বা প্রাণিত হওয় ছাড়া আর কী পাই? পড়া তো জীবন নয়। পড়া জীবনে কিছু প্রেরণা তৈরি করে দিতে পারে মাত্র।
প্রতিদিনের বিচিত্র সব ঝক্কি-ঝামেলায় পরানটা জীর্ণ হয়, এক ধরনের মরণ হয় প্রতিদিন, সেই মরণ থেকে জেগে উঠি পড়ার ভেতর দিয়ে। অবশ্যই গানের ভেতর দিয়ে, কবিতার ভেতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান শুনলেই অনেক সময় ‘গীতবিতান’ তুলে নিই। এভাবে বার বার পড়া হয় তাঁর গান। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটা তো ‘গীতবিতান’, নয় কি? তাঁর গানগুলি পড়ে কত কত বার মিইয়ে যাওয়া দশা থেকে ফের দারুণ রকমের তাজা হয়ে উঠেছি। পড়া তাই জিয়নকাঠির মতো। পড়ার ভেতর দিয়ে ‘স্পিরিটেড’ বা প্রাণিত হওয় ছাড়া আর কী পাই? পড়া তো জীবন নয়। পড়া জীবনে কিছু প্রেরণা তৈরি করে দিতে পারে মাত্র। যেমন মিশেল ফুকোর বইপত্র পড়তে চাই। ফুকো সম্পর্কিত বইপত্র পড়তে চাই। ফুকোকে জানতে চাই— এজন্য? আসলে তো ফুকোর বিচিত্র জ্ঞান এবং তিনি যে বিচিত্র শাস্ত্রের একজন তদন্তকারী, সেই তদন্তের ভেতর দিয়ে আমরা নিজেকে ও আমাদের কালকে যদি চিনতে না পারি তো এই পাঠ ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলাবাহুল্য, ফুকোর নাম নিলাম উদাহরণ হিসেবে। এর জায়গায় যে কারো নাম বসিয়ে দেওয়া যায়। বসিয়ে দিতে পারেন চালর্স ডারউইন, কার্ল মাকর্স, সিগমুন্ড ফ্রয়েড বা আলবার্ট আইনস্টাইনের কথাও।
আসলে সব পড়ার ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখা ও বিচার করার পথ পাওয়া যায়। এজন্য আত্মজীবনী, আত্মকথা ও স্মৃতিকথার দিকে টান আছে আমার। শিবরাম চক্রবর্তীর ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা’র মতো আত্মজীবনী পড়াটা স্মরণীয় হয়ে আছে। এখন যেমন পড়ছি তলস্তয়ের ‘অ্যা কনফেশান’। ছোট্ট একটা বই। কিন্তু বিপুল এর শক্তিমত্তা। তলস্তয়ের লেখা বলে কথা। মনে হলো তলস্তয়ের অন্যান্য লেখা পড়ার আগে ‘অ্যা কনফেশান’ বইটা পড়া দরকার। জেন কেনটিশ-এর অনুবাদে পড়া চলছে এ বইয়ের। এটা পড়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল লুইজি ও এলমার মার্দ-এর অনূদিত ‘গ্রেট শর্ট ওয়ার্কস অব লিও টলস্টয়’ বইটায় থাকা জন বেইলে-র অসাধারণ ভূমিকাটি। এতে বলতে গেলে বিশ্বসাহিত্যের একটা দিকের তুলনামূলক পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায়। তলস্তয়ের কথা বলতে গিয়ে কত না লেখক ও তাঁদের লেখার আলোচনা করেছেন জন বেইলে। যেমন গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করে বলা কথাটা দারুণ ধাক্কা-মারা। তিনি লিখেছেন যে, গ্যেটে ও তলস্তয় দুজনেই ছিলেন ইগোইস্ট। তবে দু’ধরনের ইগোইস্ট। মূল কথাটা ছিল: ‘ইফ গ্যেটে কেয়ার্ড নাথিং বাট হিমসেল্ফ, টলস্টয় ওয়াজ নাথিং বাট হিমসেল্ফ।’ মানে: যদি গ্যেটে নিজেকে ছাড়া আর কিছুকে পাত্তা দিতেন না, তলস্তয় নিজে ছাড়া কিছু ছিলেনই না।— কথায় ধন্দ তৈরি হয়, প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। কারণ ‘ওয়াজ’ কথাটা ইটালিক্স করা। এই একটি কথায় দু’জন লেখকের মনোভঙ্গির এই যে বিশেষ পরিচয়, এর আগে তো পাইনি। এভাবে পড়া বইগুলি একটা অন্যটার সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। উমবার্তো একো ধরিয়ে দিয়েছিলেন যে, এক বই অন্য বইয়ের সঙ্গে কথা বলে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’র সঙ্গে কথা বলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়বনামা’। ‘খোয়াবনামা’ আবার কথা বলে আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর ‘এই মর্ত্যরে রাজত্বে’র সঙ্গে। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বইগুলিও কথা বলে রুশ, মার্কিন, জার্মান কত কত বইয়ের সঙ্গে। বলাবাহুল্য, বিশ্বসাহিত্যের সবই পড়া হয় দু’হাত বা তিন হাত ঘুরে। মূল ভাষা থেকে ইংরেজি বা মূল ভাষা থেকে ইংরেজি হয়ে বাংলায়। তবে বাংলায় পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তেমন বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ধার করে বলি: ‘আমি তারি হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি।’ হ্যাঁ, বাংলার হাত ধরে যদি জ্ঞান ও অনুভব নিজের মতো করে নিজের হাতে না আসে, তাহলে তা সম্পূর্ণ হয় না। তাই নিজের ভাষায় কোনো কিছুর ভালো অনুবাদ পড়া রীতিমতো দরকারি। নইলে কোনো পাঠই প্রাণ পায় না, তা আমি যত ভালো জার্মান আর ইংরেজি জানি বা না জানি।— পাঠ-অভিজ্ঞতার ভেতরে এই সত্যটা বার বার বেজে ওঠে।
এদিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে কত কত লেখক— মিখাইল বুলগাকভ, ভ্লাদিমির নবোকভ, জ্যাক কেরুয়াক, ইসাবেল আলেন্দে, হোসে সারামাগো, ভি এস নাইপল, মিলান কুন্দেরা, সালমান রুশদি, জে এম কোয়েটজি, ওরহান পামুক কি মার্টিন অ্যামিস থেকে সুবিমল মিশ্র আর নবারুণ ভট্টাচার্যরা। পড়ে আছে মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, টমাস মান, রবার্ট মুসিল, ফ্রানৎস কাফকার বইগুলি। কিন্তু সব কিছুর হাতছানি অগ্রাহ্য করে যাঁর কাছে যাওয়া দরকার, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, ভক্তি দিয়ে নয়, প্রশ্ন করে করে বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথকে। চন্দ্রিল ভট্টাচার্য আবার এই দায় নেওয়ার কোনো মানেই পান না, কেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে? কিন্তু পাঠ-অভিজ্ঞতা আমাকে বলে, বাঙালির সত্যিকারের সাহিত্যপাঠের শেষটা না হোক শুরুর জন্য রবীন্দ্রনাথকে চাই। বাংলা ভাষায় ‘অনুভব এবং ভাবনার সমগ্রতা’র জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ তো নেই আমাদের হাতের কাছে! তাঁর ভাষা সংগীত ও গদ্যপ্রবাহের ভেতর দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে না পারলে বাঙালি লেখকের মুক্তি নেই বলেই বোধ করি। কবি গল্পকার ঔপন্যাসিক আবুবকর সিদ্দিককে কদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাঙালি লেখকের জন্য পুরো রবীন্দ্রনাথ পড়া কি আবশ্যক? তিনি এক কথায় বলেছিলেন, হ্যাঁ। আমি মনে করি। একজন ইংরেজ বা আমেরিকান লেখক শেক্সপিয়র, একজন স্প্যানিশ লেখক সার্বেন্তেস, একজন জার্মান লেখক গ্যেটে, একজন ফরাসি লেখক ফ্রাঁসোয়া র্যাবেলের লেখা পুরো না পড়ে সাহিত্যচর্চা করতে এসেছেন— এটা কি ভাবা যায়? বা নানান সময়ে তাঁদের পাঠ করছেন না— ভাবা যায়?
পড়ার ভেতরে নিত্য যেটা— তা হলো কত কত কবি আর কবিতা। গদ্যলেখকের জন্য কবিতা পড়ার তো কোনো বিকল্প দেখি না। একেবারে চর্যাপদ থেকে চঞ্চল আশরাফ কি শামীম রেজা হয়ে মাদল হাসান-সোহেল হাসান গালিব কি ইমতিয়াজ মাহমুদ; চন্দ্রবতী থেকে আয়শা ঝর্না-আসমা বীথি-শাফিনূর শাফিনদের কবিতা। (এভাবে সমকালীন কারো নাম নেওয়া ও বিপুল অংশের নাম না-নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ, তাই বলি, এখানেও নামগুলি দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়েছি। মহামান্য পাঠক, এঁদের নামের জায়গায় বাংলাভাষার যেকোনো কবির নাম বসিয়ে নিন নিজের মতো করে; যদি নিজে কবি বা লেখক হন তো নিজের নামটাও সেখানে অনুভব করতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই।) কবিতা পড়া মানেই হাতের মুঠায় কিছু না কিছু পেয়ে যাওয়া। পড়তে চেয়েছি বা পড়ার ভেতরে রেখেছি বাংলা কবিতার প্রধান সবাইকেই। বার বার ফিরে যাই ফার্সি কবিতায় ফেরদৌসী, রুমি, হাফিজ, ওমর খৈয়ামদের দিকে। অন্যদিকে ইয়েটস-এলিয়টের পর ফিলিপ লারকিন কি সিমাস হিনিদেরও। বিশ্বের অন্যান্য ভাষার কবিতা তো আছেই। আরবি আদোনিস থেকে দক্ষিণ কোরিয়ান কো উন— সবার কবিতার ভেতরে দিয়ে সৃজন ও মননের স্নান ঘটে বার বার। কবিতা পাঠ কখনো ব্যর্থ হয় না। পাঠ যদি হয় জীবনের জিয়নকাঠি, তাহলে পাঠের জিয়নকাঠি হলো কবিতা।— যতটুকু পড়ে উঠতে পেরেছি আর-যে বিপুল পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এখনও শত শত আলোকবর্ষ দূরে আছি, সেই অভিজ্ঞতা আমাকে এ-ই বলে।

জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩। নব্বই দশকরে মাঝামাঝি থেকে লেখালেখি করছেন। তিনি লিখে চলছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনা। এছাড়াও করছেন অনুবাদ ও গবেষণামূলক কাজও। বর্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। ২০০৭ সালে রাত্রি এখনো যৌবনে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির জন্য তিনি পেয়েছিলেন ‘কাগজ তরুণ কথাসাহিত্য পুরস্কার’। বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা অনুষঙ্গের প্রতি আগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই তাঁর। তিনি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসাই হলো জগতের সমস্ত প্রশ্ন, সমস্যা ও সংকটের একমাত্র উত্তর। তিনি বাংলাদেশের নৌবাহিনী উচ্চবিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে প্রাথমিক, সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উর্ত্তীণ হন। এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; পরর্বতীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে ‘তুলনামূলক নাট্যতত্ত্ব’ বিষয়ে পিএইচডি র্অজন করেছেন। বাংলা একাডেমিতে ২০১০ সালের ১ জুন থেকে থেকে ২০১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অব্দি কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করছেন।