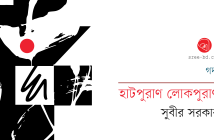আমার ছেলেবেলায় প্রথম বই পড়ার স্মৃতি খুব আনন্দের নয়, বেদনার। কারণ যতদূর মনে পড়ে আমি তখন দেখে দেখে বানান করে পড়তে পারি। বাংলা পড়তে পারি, কিন্তু ইংরেজি পড়তে পারি না। একজন শিক্ষক বাড়িতে এসে প্রতিদিন বিকেলে আমাকে পড়ান, কাঠের একটি কালো স্লেটে চকখড়ি দিয়ে ইংরেজি অক্ষর ঘোরাতে দেন, সব অক্ষর চিনি, দুয়েকটা শব্দ জানি। বাবা যে ওয়ার্ডবুক এনে দিয়েছেন, সেখান থেকে স্যার পড়ান, অক্ষরগুলো বাংলা অর্থসহ মুখস্ত করান। দিনের বেলা মা বাড়ির সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, শুধু খাবার সময় বিছানার কাছে এসে একটু সময় বসেন। খাবার দেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন, আমি খাই। মায়ের মুখখানা ঘামে চিকচিক করে। গলা ও গালে সামান্য ঘাম মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মোছেন। মায়ের দাঁতগুলো ছিল ভীষণ শাদা আর খুব সুন্দর। মা শব্দ করে হাসতেন না, কিন্তু নিঃশব্দে হাসলেও খুব সুন্দর দেখাত। শাদা বা হালকা নীল রঙের তাঁতের শাড়িতে মাকে অপরূপ লাগতো, ঘামে ভেজা গলদেশে মোটা সোনার চেইনটা লেপটে থাকত। খাওয়া শেষ হলে মা বলতেন, দুপুরে একটু ঘুমাও, আমি সন্ধ্যায় এশার নামাজের পর বই পড়ে শোনাবো। প্রায় সারা বছরই আমি অসুস্থ, বিছানাবন্দি থাকতাম। বিকেলে দাদী অনেক সময় নাড়ু বা মুড়ির মোয়া খেতে দিতেন। আমার দুই বড়ো বোন, দুজন কাজিন আনোয়ারা বুজান ও চাচাতো বোন শামসু (শামসুন নাহার) বুজান মাঝে মাঝে আমার পাশে এসে বসতেন, মাথায় হাত দিতেন। শামসু বুজান আমাদের সবার বড়ো। প্রায় মায়ের সমবয়সী। জিজ্ঞেস করতেন আমি গল্পের বই শুনব কি না। যদি মাথা নাড়তাম, পড়ে শোনাতেন।
আমার স্মৃতিতে যে বইটি পাঠ প্রথম শুনি সেটি শরৎচন্দ্রের ‘বড়দিদি’। আমাদের বাড়িতে আলমারিতে যে কিছু বই ছিল সেগুলো সবই আমার বাবার বই। বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার, এ টি দেবের অভিধান দুটি। একটি চেম্বারস ডিকশনারিও ছিল। ইতিহাসের ও রাজনীতির কিছু বই যা আমি কিছুই বুঝতাম না। আলমারির মাঝের তাকে অনেকগুলো বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই ছিল। এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের বই বেশি ছিল, কারণ মা এসব বই খুব পছন্দ করতেন।
আমার স্মৃতিতে যে বইটি পাঠ প্রথম শুনি সেটি শরৎচন্দ্রের ‘বড়দিদি’। আমাদের বাড়িতে আলমারিতে যে কিছু বই ছিল সেগুলো সবই আমার বাবার বই। বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার, এ টি দেবের অভিধান দুটি। একটি চেম্বারস ডিকশনারিও ছিল। ইতিহাসের ও রাজনীতির কিছু বই যা আমি কিছুই বুঝতাম না।
মনে পড়ে একদিন আমার শরীরে জ্বর, আমি শুয়ে আছি, গরমের দিন, ডাক্তার বলেছে আমার টাইফয়েড। মা ও বাবা খুব চিন্তিত, আমাকে দুধ আর সাগু খেতে দিয়েছে, বিছানার পাশে বশে শামসু বুজান আমাকে একটা ক্ষীণকায় বই পড়ে শোনাচ্ছেন, বইটির গল্প আমার চোখে পানি এনেছে। শামসু বুজান পড়া বন্ধ করে আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে বললেন, ‘আজ আর পড়ার দরকার নেই। এই গল্প তোমাকে কষ্ট দেয়।’
মা সারাদিনের কাজের শেষে মাগরেব বা এশার নামাজ পড়ে কখনও কখনও শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো বই পড়ে শোনাতেন, মাঝে মাঝে আমার বড়ো বোনদের স্কুলের পড়ার বই থেকে কবিতাও পড়ে শোনাতেন। তবে মায়ের ছেলেবেলায় স্কুলে পড়া কোনো কোনো কবিতা মুখস্ত ছিল, যেমন অনেকবার তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন, ‘মা গো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই!’ এভাবে আমি অক্ষর জ্ঞানের আগে গল্পের বই থেকে পাঠ শুনেছি। অসুস্থতার জন্য মা আমাকে স্কুলে যেতে দেননি। বাড়িতে বাবা একজন শিক্ষক রেখে দেন যিনি প্রতিদিন বিকেলে এসে পড়াতেন আমাকে, সঙ্গে আমার বড়ো বোনও অংক ইংরেজি ইত্যাদি বিষয় পড়তেন। আমি প্রায় আড়াই তিন বছর এই শিক্ষক, মানে রশীদ স্যারের কাছে পড়েছি। এরপর সাত আট বছর বয়সে বাবা আমাকে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। স্কুলে শের আলী কাকা শিক্ষক ছিলেন। তিনি সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখতেন শরীর তখনও খুব দুর্বল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি বলে। মা খুব উদ্বেগে থাকতেন, যদিও আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ; আমরা হেঁটেই স্কুলে যেতাম। শের আলী কাকা ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে থেকে প্রাইমারি ও হাইস্কুলে পড়ে মেট্রিক পাশ করেছিলেন। তিনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু বাবা কাকারা তাঁকে সারাজীবন ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন। তিনিও আমাদের বাড়ির সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দাদী তাঁকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন। কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই মানুষটি আমার প্রতি ছিলেন ভীষণ দুর্বল। কারণ তাঁর ছাত্র জীবনে তিনি আমাকে বাড়িতে কোলে-পিঠে করে বড়ো করেছেন। আমার স্কুলে যাওয়ার আগে মা বা বোনদের সাথে সাথে তিনিও আমাকে অনেক গল্পের বই পড়ে পড়ে শোনাতেন। এসব কারণে কিনা জানি না, গল্পের বই থেকে পাঠ শোনা বা নিজে বানান করে করে পড়ার প্রতি আমার একটা নেশা জন্মে যায়। শের আলী কাকাই আমাকে যত্ন করে শিশুদের জন্য লেখা পড়াতেন। সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়, লীলা মজুমদারসহ বেশ কয়েকজন শিশু সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে তিনিই আমাকে পরিচয় করান। কিন্তু কেন জানি না, আমার কাজিনদের মতো বা অন্য ভাইবোনদের মতো আমি শিশুসাহিত্য বেশিদিন পড়িনি, খুব ছোটো ক্লাসে পড়ার সময়ই আমি বড়োদের লেখার প্রতি আসক্ত হই। স্কুলে যাওয়ার শুরুর সময় বাবা আমাকে চার্লস ল্যাম্বের লেখা ‘টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার’ বলে একটি ছোটো ইংরেজি বই কিনে দেন। তখন আমি ইংরেজি অক্ষর লিখতে শিখেছি, কিন্তু টানা পড়তে পারি না। বাবা আমাকে পড়ে শোনাতেন বাড়িতে যখন থাকতেন। এটিই আমার জীবনে প্রথম কোনো ইংরেজি বই থেকে পাঠ শোনা। বইটিতে শেক্সপিয়ারের প্রায় সকল নাটকের গল্প শিশুতোষ ভাষায় লেখা ছিল। এর ফলে শেক্সপিয়ারের নাটকের গল্পগুলো আমার নাটক পড়ার আগে জানা হয়ে যায়। ভীষণ ভালো লাগে এসব গল্প। পরে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় আমি শেক্সপিয়ারের নাটক সমগ্র কিনি স্কুলের সামনের পুরনো দোকান থেকে। তখনও পুরনো দিনের মানে এলিজাবেথিয় যুগের ইংরেজি পাঠ করতে আমার কষ্ট হতো, কিন্তু আমাদের ইংরেজির শিক্ষক ক্ষীরলাল মুখোপাধ্যায় এবং জলিল স্যারের সাহায্যে আমি সেগুলো ভালোই পাঠ করেছি। আমাদের স্কুল থেকে বেরোবার বছর খানেক আগে শিক্ষক হয়ে এলেন মহিউদ্দিন স্যার, তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তিনি ক্লাসে শেক্সপিয়ারের নাটকের অনেক গল্প করতেন, কিছু কিছু চরিত্রের বিশ্লেষণও করতেন। মহিউদ্দিন স্যারই ক্লাসের পড়ার বাইরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং ছোটোগল্প নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করে আমাদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টি করতেন। কোনো কোনোদিন তিনি নিজেই বলতেন আজ তোমাদের বইয়ের পড়া পড়াচ্ছি না, এগুলো সহজ, তোমরা নিজেরাই পারবে। তার চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা নিয়ে কথা বলি।’ এই বলে একদিন তিনি ‘অধ্যাপক’ গল্পটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন মনে আছে।
ছেলেবেলায় গ্রামে থাকতে বাবা আমাকে অনেক বই কিনে দিতেন ফরিদপুর বা ঢাকা কোনো কাজে গেলে। বিশেষ করে জীবনী গ্রন্থ তিনি বেশি কিনে দিতেন। তখন আমি মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছি, একদিন বাবা আমাকে জওহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনী এনে দিলেন। ইংরেজি বইটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু এই বৃহৎ বইটি পড়ার মতো ইংরেজি জ্ঞান আমার ছিল না। কিন্তু বাবার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে অনেক ছোটো সময় থেকে বাবার মুখে এই নেতার অনেক গল্প আমি শুনেছি। এছাড়া ছোটোদের জন্য সরল বাংলায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর একটি বই বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন, সেটি পড়ে গান্ধী ও ভারতের রাজনীতির কিছু কথা সামান্য জেনেছিলাম। নেহেরুর আত্মজীবনীটি আমি বানান করে করে পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রের পক্ষে এর বিভিন্ন শব্দ বোঝা কঠিন, তাই বাবা আমাকে অভিধান দেখে দেখে অজানা শব্দগুলো লিখে রাখতে পরামর্শ দেন, এবং খুব ধীরে ধীরে হলেও সব শব্দের অর্থ জেনে পড়তে বলেন। আমি সে অনুযায়ী অনেকদিন ধরে বইটি দুয়েক পাতা দিনে পড়তাম। এক সময় পড়া শেষ হলে খুব ভালো লাগে, কিন্তু ততদিনে দেখি আমার খাতা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে নতুন জানা শব্দগুলোতে। এরপর বাবা আমাকে বলেন বইটি আরেকবার পড়তে। সেভাবে পড়তে গিয়ে দেখলাম আমি প্রায় অভিধান ছাড়াই সব বুঝতে পারি। এই প্রথম বুঝতে পারলাম আমার অনেক ইংরেজি শব্দ জানা হয়ে গেছে। আমার সেই প্রথম নেহেরুর লেখা পড়ার অনেকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শেষদিকে সাতাত্তর সনে ‘দেশ’ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় দেখি আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর বাংলা শেখা নিয়ে লেখা ‘ভাষা শেখার তিন পর্ব’ প্রবন্ধে ঠিক একই রকম কথা লিখেছেন। প্রবন্ধটি পরবর্তীতে তিনি ‘পথের শেষ কোথায়’ বইতে গ্রন্থিত করেছেন। একটি বই অভিধান দেখে দেখে দুই বা তিনবার পড়লে যেরকম একটি নতুন ভাষা বিষয়ে জ্ঞান হয়, দশটি বই একবার করে পড়লেও তা হয় না।
এছাড়া ছোটোদের জন্য সরল বাংলায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর একটি বই বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন, সেটি পড়ে গান্ধী ও ভারতের রাজনীতির কিছু কথা সামান্য জেনেছিলাম। নেহেরুর আত্মজীবনীটি আমি বানান করে করে পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রের পক্ষে এর বিভিন্ন শব্দ বোঝা কঠিন
বাড়িতে এভাবেই প্রাইমারি স্কুলে থাকতেই আমার অনেক বই পড়া হয় বাবার ইচ্ছায়, আর মা ও বড়ো বোনদের কল্যাণে গল্প ও উপন্যাস শোনা ও পড়া হয়। এর ফলে আমার মনে পড়া বিষয়ে খুব আগ্রহ জন্মাতে থাকে। একদিন বাবা আমাকে ঢাকা থেকে ফেরার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীটি এনে দেন। আমি তখন মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছি। এই বইটি আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমি বার দুয়েক পড়ি। আমার বালক মনে বইটি বড়ো রকমের প্রভাব ফেলে। আমি সারাজীবন আচার্য রায়ের জীবনের দুয়েকটি বিষয় অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, একটি হলো আহার ও পোশাকের ব্যাপারে খুব মিতব্যয়ী হওয়া এবং সব ধরনের বই পড়ে সময় কাটানো। মেরুন রঙয়ের রেক্সিনে বাঁধানো সেই বইটি বহু বছর আমার সঙ্গে থাকত। আমি বন্ধুদের অনেককে পড়তেও দিতাম। পরে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে (যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির অংশ) পড়তে গিয়ে সেই একই রেক্সিনে বাঁধাই বইটি দেখতে পাই। এর কিছুদিন পর জানতে পারি বইটি তিরিশের দশকের শুরুতে আচার্য রায় ইংরেজিতে প্রথমে লেখেন, পরে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আমি এটা জেনে একটি ইংরেজি সংস্করণও সংগ্রহ করি, যা আমাকে খুব মুগ্ধ করে, বিশেষ করে আচার্য রায়ের ইংরেজি ভাষা!
ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পর আমি আমাদের স্কুলের সিনিয়র ভাই শাহ আবদুল কাদের ভাইয়ের পরামর্শে কিছু বই পড়ি। তবে আমার ফুফাতো ভাই খুব মেধাবী মানুষ, যিনি আমার সিনিয়র ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি বই আমাকে পড়তে দেন, একটি মৃণালিনী, দ্বিতীয়টি বিষবৃক্ষ। সেটাই আমার জীবনে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র পড়া। প্রথমে তাঁর বাংলা ভাষা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয়েছে, এমনকি অনেক শব্দ আমি বাবার অভিধান ‘চলন্তিকা’ দেখে দেখে অর্থ খুঁজে পড়েছি। কিন্তু বঙ্কিমের এই দুটি বই আমার মনে এই লেখক সম্পর্কে খুব আগ্রহ সৃষ্টি করে। এছাড়া বাড়িতে অনেক সিনেমা পত্রিকা পড়তেন আমার বোনরা। আমি সেসব পত্রিকায় রঙিন ছবি দেখতাম যা আমার খুব ভালো লাগত। সেভাবেই ‘সিনেমা জগৎ’, ‘প্রসাদ’ ও ‘উল্টোরথ’ পত্রিকা পড়ার নেশা জন্মে আমার মাঝে। এসব পত্রিকায় বাজার কাটতি অনেক লেখকের লেখা বের হতো, বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, শচীন ভৌমিক ও আরও কেউ কেউ। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব নামকরা ভালো লেখকদের লেখাও এসব পত্রিকায় সে সময় বের হতো। আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবীসহ অনেক প্রতিভাবান লেখকদের লেখাও সিনেমার পত্রিকাগুলোতে পড়েছি। ‘উল্টোরথ’ পত্রিকাতেই আমি জীবনে প্রথম সমরেশ বসুর লেখা পড়ি। সেই বিস্ময় এবং ঘোর আমাকে অনেকদিন তাড়া করে ফিরেছে।
আমাদের জাজিরা মোহর আলী হাই স্কুলের লাইব্রেরিটি খুব বড়ো ছিল না, কিন্তু নতুন আসা শিক্ষক সালাম স্যার, রব মুন্সী স্যার ও শামসুল হক স্যার স্কুলে যোগ দিয়ে বেশ কিছু বই লাইব্রেরির জন্য কেনেন। সেখানে সেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই সালাম স্যার শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবনী ও জন এফ কেনেডির জীবনী পড়তে দিয়েছিলেন। আমি কেনেডির জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই সময় বড়ো ভাইদের মুখে একটি বইয়ের খুব নাম শুনি, সেটি আবদুর রাজ্জাকের লেখা ‘কন্যাকুমারী’ । এই উপন্যাসটি আদমজী পুরস্কার পেয়েছিল। শুনলাম বড়োদের বই, কিন্তু আমি লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়লে তেমন কিছু মনে হয়নি। ভালো লেগেছিল। আমি এর আগে সমরেশ বসুর ‘বিবর’ এবং ‘প্রজাপতি’ও পড়েছি। কিন্তু কোনো খারাপ কিছু মনে হয়নি, যা আমার সিনিয়র কাজিন মজিদ শিকদার বা শাহ কাদের ভাই আমাকে সতর্ক করে বুঝিয়েছিলেন। জানি না আমার পাঠের প্রতিক্রিয়া কেন তাঁদের থেকে আলাদা ছিল। যাহোক মজিদ ভাই এবং কাদের ভাই দুজনে আমাকে বাংলা সাহিত্যের বড়ো লেখকদের বইয়ের তালিকা করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ বা একেবারে হাল আমলের শংকর বা আশাপূর্ণা দেবীর কোন কোন বই পড়তে হবে তা দীর্ঘ তালিকা করে দেন। জাজিরা হাইস্কুলে এই তালিকার সব বই ছিল না। সামান্য কিছু ছিল, আমি তা পড়ে শেষ করেছি। আমি খুব দ্রুত বই পড়ে ফেরৎ দিতাম স্কুলে। সম্ভবত শামসুল হক স্যার ভাবতেন আমি না পড়েই ফেরৎ দিচ্ছি। একদিন তিনি আমাকে বিমল মিত্রর বই ‘এর নাম সংসার’ এবং শংকরের ‘রূপতাপস’ বই দুটি ফেরৎ দিতে গেলে রেজিস্টার খাতায় লিখে আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি লাইব্রেরি অফিসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি লেখা সেরে আমাকে বললেন, এই বই দুটির গল্প সংক্ষেপে তাঁকে বলতে। আমি বললাম, তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। আমি দুইদিন আগে বই দুটি নিয়েছিলাম।
এরপর আমি কলেজিয়েট স্কুলে চলে যাই, সেখানে আমার পড়ার অভ্যাস বেড়ে গেল, কারণ কলেজিয়েটের লাইব্রেরিতে অনেক বই ছিল। এত বই আমি আগে কোথাও দেখিনি। শত বছর আগের ইংরেজি সাহিত্যেরও অনেক বই সেখানে ছিল। এছাড়া প্রতিটি ক্লাসে একটি করে আলমারিতে বই থাকত। ক্লাসের মনিটর সেখান থেকে বই দিত, আবার পরের সপ্তাহে ফেরৎ দিতে হতো। আমি সেখান প্রথম যে বইটি নিয়ে পড়েছিলাম সেটি ছিল ‘অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট’। এর আগে আমি এরিক মারিয়া রেমারকের কোনো বই পড়িনি। ভীষণ মুগ্ধ হলাম। স্কুল হোস্টেল আমরা দুজন ছাত্র ছিলাম, আমি আর আইয়ুব ভাই। আইয়ুব ভাই আমার এক বছর সিনিয়র। তিনিও বই পাগল ছিলেন। এক তলা এবং দোতলায় আমাদের ছয়জন শিক্ষক থাকতেন। আমরা দুজন থাকতাম দোতলার একটি কক্ষে। আমাদের পাশের রুমে থাকতেন আমাদের বাংলার শিক্ষক বদরুদদোহা খান স্যার। তিনি লক্ষ্য করলেন আমি প্রায় প্রতিদিন স্কুল থেকে বই এনে পড়ি। তিনি বই নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। তাঁর নির্দেশেই আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সব লেখকদের লেখা পড়তে শুরু করি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একেবারে তিরিশের দশকের লেখকদের বই এনে পড়ি। খান স্যার আমার পড়া হলে বই নিয়ে আলোচনাও করেন। এতে দেখা গেল আমার ক্লাসের পড়ার চাইতে ঢের বেশি সময় ব্যয় হয় এসব সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের বই পড়ে। তবে অধিকাংশ সময় ইংরেজি বই পড়ার দিকেই আমার নেশা শুরু হয়। এর মধ্যে ডিকেন্স ও হারডি প্রথমে প্রায় যা পাওয়া গেল পড়লাম। এছাড়া মোহাম্মদ আলী স্যার আমাদের ইংরেজি পড়াতেন ক্লাসে, তাঁর পরামর্শে জনাথন সুইফটের ‘গালিভারস ট্রাভেল’ পড়লাম। খুব ভালো লাগল। কিন্তু আমাদের কয়েক বছর সিনিয়র আবদুল কাইউম মুকুল ভাই মাঝে মাঝে স্কুলে আসতেন ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য করার জন্য। তিনি ‘৬৫ সালে আমাদের স্কুল থেকে বোর্ডে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন, তাঁকে সবাই ভালোবাসতেন। তিনি এসে আমাদের রুশ সাহিত্যের তালিকা দেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য বানান। প্রথমে তলস্তয়ের একটি ছোটোগল্পের সংকলন পড়ি আর এর ফলে সারাক্ষণ তলস্তয়ের বই খুঁজে খুঁজে পড়ি। মুকুল ভাইই আমাকে দস্তয়েভস্কি, পুশকিন ও গোগোলের লেখা খুব যত্ন করে পড়ান। খুব সহজে বুঝতে পারি আমার সাহিত্যরুচি বদলে যাচ্ছে। কলেজিয়েট স্কুলের সামনে একটা দোকান ছিল লিয়াকত এভেনিউতে যেখানে শুধু চীন আর রাশিয়ার পত্রিকা আর বই পাওয়া যেত ভীষণ সস্তায়। বয়স্ক ভদ্রলোক দোকানের মালিক, কিছুদিন বই কেনার পর তিনি আমাকে এমনিতেই বই দিলেন পড়তে এবং বলে দিলেন পাতা না মুড়তে বা কোনো দাগ না দিতে। ফলে আমি সেখান থেকেই কয়েক মাসের মধ্যে অনেক রুশ ক্লাসিকস পড়ে শেষ করি।
কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকরা বুদ্ধদেব বসুর নাম করতেন খুব, কারণ তিনি ছিলেন এই স্কুলের তারকা ছাত্র। স্কুলের লাইব্রেরিতে তাঁর প্রায় সব বই ছিল, তবে সেগুলো ‘৬৫ সালের আগের বই, কারণ পাক-ভারত যুদ্ধের পর কলকাতা থেকে বই আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমি প্রথমে একটি গল্পের বই পড়ি, যেখানে পুরানা পল্টন নিয়ে একটি লেখা আমাকে খুব মুগ্ধ করে।
কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকরা বুদ্ধদেব বসুর নাম করতেন খুব, কারণ তিনি ছিলেন এই স্কুলের তারকা ছাত্র। স্কুলের লাইব্রেরিতে তাঁর প্রায় সব বই ছিল, তবে সেগুলো ‘৬৫ সালের আগের বই, কারণ পাক-ভারত যুদ্ধের পর কলকাতা থেকে বই আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমি প্রথমে একটি গল্পের বই পড়ি, যেখানে পুরানা পল্টন নিয়ে একটি লেখা আমাকে খুব মুগ্ধ করে। ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব বসুর অনেক বই পড়া হয়ে যায় আমার। ‘তিথিডোর’ পড়ার সময় কাসেম স্যার, যিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, তিনি আমাকে ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন মনে আছে। এভাবে আমার কলেজিয়েট স্কুলের বছরগুলোতেই সবচেয়ে বেশি বই পড়া হয়। এর আরেকটি কারণ ছিল আমাদের ক্লাসের বন্ধুরা স্কুলের উল্টোদিকে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে ভাড়ায় বই এনে সারাক্ষণ তিন চারজন মিলে দ্রুত পড়ত। তিন আনা বা চার আনায় সারা দিনের জন্য বই আনতাম আমরা। ক্লাস চলার সময়ও পেছনে বসে বই পড়ে শেষ করতাম আমি, সুব্রত, হামুদর, আলো, কামরুল। আরেকটি বেঞ্চে বসে একইভাবে নাজমুল, শহীদ রিয়াজ ও ফিরোজ কবিরও এরকম বই দ্রুত পড়ে শেষ করত। এছাড়া রিয়াজ, আলো, ফিরোজদের বাড়িতে পূজাসংখ্যা কলকাতার পত্রিকাগুলো থাকত, আমরা সেগুলো নিয়েও পড়তাম। এভাবেই বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। তবে সাহিত্যের বাইরে রাজনীতির বই আমাকে ভীষণ টানত, কারণ মুকুল ভাইয়ের কাছ থেকে আমি বেশ কিছু রাজনীতির বইয়ের খোঁজ পাই, তবে তার সবই মার্ক্সবাদী রাজনীতির বই। আমি অবশ্য এর বাইরেও মার্কিন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বই পড়ি।
ঢাকা কলেজে যাওয়ার পর আমার পড়ার বিষয় অনেকটাই বদলে যায়। আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিনের প্রথম শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শওকত ওসমান। কলেজিয়েট স্কুলের বড়ো ভাই আইয়ুব ভাই, যিনি তখন ঢাকা কলেজে, আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন শওকত স্যারের ক্লাস যেন কোনোমতেই মিস না করি। প্রথম দিনেই অধ্যাপক শওকত ওসমান জানিয়ে দিলেন তিনি কোনো নাম ডাকবেন না। সুতরাং যে খুশি ক্লাসে থাকতে পারে বা চলে যেতে পারে। তিনি বললেন, ‘Just imagine, য পলায়তি, স জীবতি’! এরপর জানালেন, নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকান ‘মল্লিক ব্রাদার্স’- এ একটি বই এসেছে বারট্রানড রাসেলের ‘Introduction to Mathematical Philosophy’, সেটি কিনে পড়ার পরামর্শ দিলেন। আমি সেদিনই বিকেলে বইটি সংগ্রহ করি। পড়তে গিয়ে বুঝলাম আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পরদিন অধ্যাপকদের কক্ষে শওকত স্যারকে গিয়ে বইটির কিছুই বুঝতে না পারার কথা বলি। তিনি আমাকে এক পাশে ডেকে বসতে বলেন এবং জিজ্ঞেস করেন আমি দর্শনের কোনো বই আগে পড়েছি কি না। আমি বলি দার্শনিকদের কারো কারো জীবনী পড়েছি, কিন্তু এ ধরনের দর্শনের বই পড়িনি। স্যার আমাকে পরামর্শ দিলেন রাসেলের ‘History of Western Philosophy’ বইটি খুব মনোযোগ দিয়ে ভালো করে আগে পড়তে। এরপর তাঁর অন্যান্য বই পড়তে। আমি আবার মল্লিক ব্রাদার্স- এ গিয়ে বইটি সংগ্রহ করে পড়া শুরু করি। এবার কিন্তু আমার তেমন অসুবিধা হয় না বুঝতে। এভাবে আমি অভিধানের সাহায্য নিয়ে বইটি মাস দুয়েকের মধ্যে পড়া শেষ করি। এরপর রাসেলের ছোটো আকারের জনপ্রিয় বইগুলো পড়ার পরামর্শ দেন শওকত স্যার। আমি তাঁর কথা মতো কলেজ লাইব্রেরি থেকে প্রায় সবগুলো নিয়েই পড়ে শেষ করি। কেমন একটা ঘোর লাগানো নেশায় পেয়ে যায় আমায়। শওকত স্যার আমাকে কিছু জার্মান ও ফরাসী উপন্যাসিকের লেখাও পড়ার নির্দেশ দেন। স্যারের খুব প্রিয় লেখক প্রুস্ত ও এমিল জোলা। আমাকে সবগুলো পড়ার নির্দেশ দেন। নিজে অনেক বইয়ের গল্প করতেন কলেজের করিডোরে দাঁড়িয়ে, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।
কোনো কোনো বই পড়ার সঙ্গে কিছু অনুষঙ্গ কিছু স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। অনেক বছর পর বইটি পড়তে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সেইসব স্মৃতি মনে এসে ভর করে। যেমন কাফকার কোনো লেখা যখন আমি পড়ার চেষ্টা করি, আমার স্মৃতিতে ভাসে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু স্মৃতি। আমি কাফকার লেখা প্রথম পড়ি ’৭০ সালের শেষ দিকে, কলেজের প্রথম বর্ষে, হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে শীতের এক বিকেলে। পেঙ্গুইন প্রকাশিত ‘Metamorphosis and other stories’. বইটি আমাকে বিষণ্ণ করেছিল। কলেজ লাইব্রেরি থেকে নেওয়া বইটি। আমার বন্ধু ও সহপাঠী খন্দকার খলিলুর রব আমাকে বইটি পড়তে বলেছিল। খলিল আমাদের সাউথ হোস্টেলেই থাকত। আমাদের সঙ্গে আরমানিটোলা স্কুল থেকে এস এস সি তে প্রথম দশের মধ্যে ছিল। বন্ধু হিশেবেও অসাধারণ। খলিলের বাবা আমাদের কলেজের লাইব্রেরিয়ান, আদি বাড়ি মাদারীপুর, আমার বাবার পরিচিত, অনেকটা সমবয়সী। কলেজ তাঁকে আমাদের হোস্টেলে বাসা বরাদ্দ করেছিল। খলিল বাবা মায়ের সঙ্গে থাকত, কিন্তু সারাক্ষণ আড্ডা দিত আমাদের সঙ্গে। খলিলের বড়ো ভাই খন্দকার শহীদুর রব খুবই মেধাবী মানুষ এবং বিখ্যাত স্থপতি। বুয়েটে যারা প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন স্থাপত্য বিভাগে, তাদের সবাইকে পরে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি দিয়ে নিয়ে যায়, সেখান থেকেই তারা ডিগ্রি করেন। ড. শহীদুর রব ’৭১ সালে বুয়েটে পড়াতেন, বিয়ে করেছিলেন বিখ্যাত স্থপতি ওয়াজেদা জাফরকে। ’৭১ সালে তারা আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। খলিল বুয়েটে ভর্তি হয়ে কয়েক মাস পড়েছিল, পরে রাশিয়া চলে যায় বৃত্তি নিয়ে। ঢাকায় ফিরে কিছুদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হন, সেখান থেকে আবার মাস্টার্স করে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করেন মেরিল্যান্ডে আজ প্রায় সাড়ে তিন দশক।
কিন্তু কাফকাকে নিয়ে সত্যিকার দীর্ঘ আলোচনা করে কাফকার জীবন ও লেখাকে গভীরভাবে আমাকে বুঝতে সাহায্য করেন আমার প্রিয় কবি ও বন্ধু আলতাফ হোসেন। আলতাফের পরামর্শে আমি ইউজিন ইউনেস্কোসহ বেশ কয়েকজন আধুনিক ফরাসী, জার্মান, সুইডিশ এবং ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের লেখা পড়ি। এসময়েই আমি বোর্হেস ও পাজের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাকে স্প্যানিশ ভাষার বেশ কয়েকজন লেখক খুব মুগ্ধ করে।
কাফকার ‘মেটামরফোসিস’ পড়ার স্মৃতির পর বাহাত্তরের গোড়ায় কলেজে ফিরে জার্মান কালচারাল সেন্টারে যাতায়াত শুরু করি, ওদের লাইব্রেরিটা খুব সুন্দর ছিল, বিনা পয়সায় ভালো ছবি দেখা যেত। সেখানেই আমি কাফকার ক্যাসেল, ট্রায়ালসহ অন্যান্য লেখা পড়ি। কিন্তু কাফকাকে নিয়ে সত্যিকার দীর্ঘ আলোচনা করে কাফকার জীবন ও লেখাকে গভীরভাবে আমাকে বুঝতে সাহায্য করেন আমার প্রিয় কবি ও বন্ধু আলতাফ হোসেন। আলতাফের পরামর্শে আমি ইউজিন ইউনেস্কোসহ বেশ কয়েকজন আধুনিক ফরাসী, জার্মান, সুইডিশ এবং ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের লেখা পড়ি। এসময়েই আমি বোর্হেস ও পাজের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাকে স্প্যানিশ ভাষার বেশ কয়েকজন লেখক খুব মুগ্ধ করে। নেরুদা এবং আরও কয়েকজন। আমি তখন লন্ডন ম্যাগাজিনসহ অন্যান্য বিলেতের পত্রিকার সাপ্লিম্যানট পড়তাম, বিশেষ করে টি এল এস। লন্ডন ম্যাগাজিনেই আমি অক্তাভিও পাঁজের এক গুচ্ছ কবিতা পড়ি এবং অনুবাদ করি। এর কয়েকদিন পর পাজের একটি গদ্য গ্রন্থ ‘অলটারনেটিং কারেন্ট’ পড়ে ভালো লাগে। বইটির একটি আলোচনা আমি লিখি দৈনিক বাংলার সাময়িকীর জন্য। মার্কেজ পড়ি আরও কিছুদিন পর কবি বেলাল চৌধুরীর সাহায্যে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় আলতাফ বার্ড এর চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চাকরি নিয়ে এলে আমরা প্রায় প্রতিদিনই আড্ডা দিতাম। সাহিত্য এবং ক্লাসিক্যাল সংগীত বিষয়ে আলতাফ এতো সুন্দর করে বোঝাতে পারত! ওঁর মধ্যে আমি অসাধারণ শিল্পগুণ নয় শুধু, গভীর প্যাসান লক্ষ্য করেছি সব শিল্প বিষয়েই, যা খুব বেশি বন্ধুদের মধ্যে দেখিনি। আমার বিবেচনায় আলতাফ কবি এবং গদ্য লেখক হিশেবে আমাদের সমাজে ভীষণ আনডাররেটেড। সেটা কিছুটা মনে হয় ওঁর নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতা, প্রচারবিমুখতা এবং লাজুক স্বভাবের জন্য! কলিন উইলসন, ইউজিন আয়নেসকো, কাফকা এবং সিল্ভিয়া প্লাথকে নিয়ে আলতাফ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। সত্যিই আধুনিক পশ্চিমা সাহিত্য ওঁকে খুব বুঁদ করে রাখত। কাফকার ডায়েরির বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে কাফকার মনোজগৎটা বোঝাতে চাইতেন আমাদেরকে।
এর পর আরেক চেক লেখককে আমায় প্রথম পড়ান মঞ্জুর ভাই, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ’৮১ সাল, ক্যানাডা থেকে ডিগ্রি শেষ করে মাত্র ফিরেছেন। জোক, আনবেয়ারেবল লাইটন্যাস অফ বিং, ছাড়াও কুণ্ডেরার প্রায় সব বইই আমি মনজুর ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে পড়ি। তারপর নিজেও সংগ্রহ করি। সে-সময়ের কিছু পরে কলকাতার রুপা প্রকাশনীর পুনর্মুদ্রিত ‘দ্য আর্ট অফ নভেল’ নামে তাঁর একটি অসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থ পড়ি। বইটি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। উপন্যাস কী এবং কীভাবে আধুনিক উপন্যাস বুঝতে হয় তা তিনি ভিন্নভাবে বোঝান। কুণ্ডেরায় বুঁদ থাকার কবছর আগে আমি হাভেলের লেখা পড়ে মুগ্ধ হই। সেটা ’৭৬-’৭৭ সাল, কিছুটা রাজনৈতিক কারণে, কিছুটা তাঁর সাহিত্যের জন্য হাভেল আমাদের নিত্যদিনের পাঠ ও আড্ডার আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জন্মেছিলেন ইউরোপের এক ঘন অন্ধকার সময়ে। যে সময়টায় জার্মানি এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে শুধুই পাথরের কুচি আর কাচের গুড়ো ছড়ানো ছিল, ধ্বংসের বিস্তীর্ণ চরাচর! পূর্ব ইউরোপ ছিল প্রায় ‘চিন্তাহীন’ এক দমবন্ধ করা টোটালেটেরিয়ান হাওয়ায় ঘেরা। মার্ক্সবাদী শাসন সবার কণ্ঠকেই কিছুটা স্তব্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। কিন্তু ১৯৬০ দশকের তরুণরা পশ্চিমা খোলা সংস্কৃতিকে শুষে নিতে চায়। বিশেষত হাভেলের নতুন শিল্পতত্ত্ব, যা কিনা শুধু একটু দর্শন-ছোঁয়া বিষয় নয়, বরং অনেকখানি রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির দিশা। যেহেতু চেক সেন্সরশিপ তাঁকে বাধ্য করেছিল স্বদেশের রাজনীতি নিয়ে নীরব থাকতে, তাই তিনি হাতে যে বই পেতেন জেলে বসে, তা নিয়েই রাজনৈতিক-দার্শনিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা করতেন। এমনকি রুশ সামাজিক ইতিহাস বা ফরাসী অস্তিত্ববাদী উপন্যাস, সবকিছু ঘিরেই তিনি রাজনৈতিক ডিসকোর্স সৃষ্টি করতেন চিঠির মাধ্যমে। ছোটো ছোটো রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে অনুপুঙ্খ দৃষ্টিভেদী আলোচনা, যার মূলে থাকত বাঁচার তীব্র ক্ষুধা, মানবের বাঁচার ক্ষুধা! জেলজীবনের বেদনাবিদ্ধ একাকীত্ব আর বাঁচা এবং স্বদেশকে বাঁচানো, এসব চিন্তাই করোটিকে সক্রিয় রাখত তাঁর সারাক্ষণ। যে সব পঙক্তিমালা চিটি জুড়ে থাকত, তার সুর ছিল ভিন্ন, নিজেকে আরও বেশি যন্ত্রণাবিদ্ধ করে বাইরের মানুষের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করা। তাই সহজেই লিখেছেন, ‘a need to experience the world, again and again, in as direct and unmediated a way as possible.’
দস্তেভস্কির সময় থেকেই জেল-স্মৃতি সাহিত্য ও দর্শনের সীমানা ঘেঁষে এগোচ্ছে, এমন কি সেই কল্পনাবিলাসী জ্যঁ জেনে পর্যন্ত, যাকে সার্ত্রের দীর্ঘ বই লিখে দুধ থেক ছেনে মাখন তোলার মতো দর্শন ও রিজনকে ছেনে তুলতে হয়েছে। আমাদের কৈশোরে সার্ত্রের সেইন্ট জেনেকে রোমান্টিক চোখেই দেখেছিলাম।
দস্তেভস্কির সময় থেকেই জেল-স্মৃতি সাহিত্য ও দর্শনের সীমানা ঘেঁষে এগোচ্ছে, এমন কি সেই কল্পনাবিলাসী জ্যঁ জেনে পর্যন্ত, যাকে সার্ত্রের দীর্ঘ বই লিখে দুধ থেক ছেনে মাখন তোলার মতো দর্শন ও রিজনকে ছেনে তুলতে হয়েছে। আমাদের কৈশোরে সার্ত্রের সেইন্ট জেনেকে রোমান্টিক চোখেই দেখেছিলাম। আজকের তরুণরাও নিশ্চয় তাই করেন। তাঁর নিজের বয়ান অনুযায়ী, লেখা বিশেষ করে সৃষ্টিশীল কিন্তু তীব্র রাজনৈতিক দ্রোহের লেখা খুব সহজে আসে না, যখন বলেন, ‘From the sketch to the work one travels on one’s knees’, রক্ত ঝরে বেশ! অন্যান্য ডিসিন্ডেট চেক লেখকদের সঙ্গে হাভেলের তফাৎটা হলো তিনি প্রজন্মান্তরের আনুগত্যপ্রেমী লেখক, একটা ট্র্যাডিশনাল চেক সাহিত্যের ধারা এটা। শক্তিশালী সেই ধারার ছবি মনে আসতেই যার কথা সবার আগে মনে পড়বে তিনি কাফকা। সেন্ট্রাল ইউরোপের লেখকদের মধ্যে, বা অন্য সমকালীন বা প্রজন্মান্তরের লেখকদের কাছেও, বিশেষ করে চেকদের কাছে কাফকা শুধু রূপক বা প্যারাবল সাহিত্যের জনক নন, তাঁর সাহিত্যকে বিচার করা হয় এক বাহ্যের সীমানাতিক্রান্ত ‘সত্য’ হিশেবে, ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি ‘Truth, pure and simple’! কাফকা সর্বকালের বিভীষিকাময় ব্যুরোক্রেসির বন্দিদশার চিত্রকে মহান শিল্পে রূপ দিয়েছেন। কাফকার শিল্প-দৃষ্টি বেদনাবিদ্ধ মানবের রক্তাক্ত আত্মাকে অনেকখানি মমতার ছোঁয়া দিয়ে যায়। তিনি আমাদের ‘আধুনিক’ যন্ত্রণাময় জীবনের মাঝে যে গভীর ও ব্যাপ্ত-নিরাশা স্থায়ীভাবে প্রোথিত তাকে শনাক্ত করেন শিল্পিতভাবে। হাভেল কাফকার মাঝে নিজের স্বপ্নের শিল্পীকে খুঁজে পান। অন্য চেক লেখরাও তাই পান যেমন মিলান কুণ্ডেরা, যদিও একেবারে ভিন্নভাবে। হাভেলের শিল্পীমন একটু অতিরিক্ত সিরিয়াস- মাইন্ডেড। যদিও সেই হাভেলকে আমরা জেলের চিঠিতে পাই না। আমরা জানি না কুণ্ডেরা জেল থেকে চিটি লিখলে কেমন হতো, কিন্তু তাঁর শিল্পী-চারিত্র দেখে আন্দাজ করা যায় অনেক ঢিলেঢালা হতো চিঠির স্টাইল নিশ্চয়! হাভেল বিশ্বাস রাখেন স্বভূমিতে, প্রায় ধার্মিকের মতো। কিন্তু কুণ্ডেরা কনফার্মড সিনিক। হাভেল এক্টিভিস্ট, যিনি স্বদেশ ত্যাগে রাজী নন, যদিও তাঁকে সেই অপশন দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে কুণ্ডেরার নায়কোচিত কিছু করার অভিলাষ ছিল না। তাঁর সবচেয়ে বড়ো ‘শৈল্পিক’ দুর্বলতা হলো নস্ট্রালজিয়া। কুণ্ডেরার সঙ্গে তুলনা করলে হাভেলকে প্রায় নিরীহ মানুষ মনে হতে পারে। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায় কুণ্ডেরা প্রায় একটি পঙক্তিও লিখতে পারেন না রহস্যময়তার কোনো না কোনোভাবে সংযোগহীন। শেষ বিচারে এই দুই চেক লেখক আসলে মানবের দুই বিশেষ ধারাকেই প্রতিনিধিত্ব করেন। নিয়ত ব্যথিত এক আত্মঅন্বেষণকারী ও এক্টিভিস্ট হাভেল, এবং শক্তিশালী কিন্তু সংশয়ী দার্শনিক-সিনিক শিল্পী কুণ্ডেরা! যদিও তিনি নাট্যকার, কিন্তু হাভেল হয়তো জনচিত্তের গভীরে যেতে চাননি, হয়তো ভীত ছিলেন, না জানি তাদেরকে দোষারোপ করতে হয় অনেক ব্যাপারেই। বাহ্যত মানব চরিত্রের শুভ দিকটাই তিনি স্মৃতিতে রাখতে চান, মানবের জটিল মনের অন্তঃস্রোত ও তার বিচিত্র প্রকৃতি থেকে হাভেল দূরে থাকেন। কিন্তু প্যারাডক্সিক্যালি দেখলে কুণ্ডেরা দারুণ নিবন্ধকার হয়েও কিন্তু মানব চারিত্র আঁকেন সিদ্ধহস্তে, তার ভেতরের সকল জটিলতা এবং কেলাইডস্কোপিক বর্ণচ্ছটাসহ। আমি যখন হাভেলের জেলের চিঠি আর কুণ্ডেরার উপন্যাস মিলিয়ে পড়ি, আমার মনে ভিন্ন এক ভাবনা কাজ করে। জেলের চার দেয়ালের বন্দিদশা থেকে লেখা আর আরেকজনের স্বাধীন জীবনের গোঙানি মিশ্রিত ভাষায় মানব চরিত্র নির্মাণ আসলে একই বেদনা ও ক্ষরণ থেকে উৎসারিত! যদিও দুই ভিন্ন শিল্পীর কাজ, তবুও তাঁরা একই ভূমি আর সময়ের সন্তান, বড়ো শিল্পী!
আমি একটু বেশি বয়সে, মধ্য তিরিশে বিদেশে এসেছি, একটু আগে এলে আমার প্রিয় কয়েকটি বিষয়ে আরও পড়তে বা গবেষণা করতে পারতাম মনে হয়! পড়াতেই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই, আজও! এবং তা বিচিত্র সব বিষয়ে!
ঢাকা ছাড়ার আগেই আমি সমাজবিজ্ঞানের কিছু কিছু বই পড়ি আমার বন্ধু ড. মনিরুল ইসলাম খানের পরামর্শে। আশির গোড়ার দিকে মুনীরের সঙ্গে আমি খুব আড্ডা দেই এবং সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কিছু বইপত্রের সন্ধান জানি। সেখান থেকেই আমার সমাজবিজ্ঞানে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এর পরের প্রায় চল্লিশ বছর আমার সমাজবিজ্ঞানের বইই বেশি পড়া হয়েছে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে। ’৯৩ সালে নিউ ইয়র্কবাসী হওয়ার পর আমার সামনে জগতের সকল ভালো বই পড়ার সুযোগ আসে, যা কিনা আমি ঢাকায় থাকতে পাইনি। সেই সময় থেকে আজ প্রায় উনত্রিশ বছর আমার পড়ার বই আমি সহজে সংগ্রহ করতে পারি। আমি যে সারাজীবন বই পড়ার তীব্র ক্ষুধায় ভুগেছি তাঁর অনেকখানি মিটেছে নিউ ইয়র্কের নতুন ও পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে! আমি সারাজীবন বিলাসিতাহীন জীবন যাপন করেছি, বলা যায় বেশ মিতব্যয়ী মানুষ। কিন্তু ছাত্রজীবনে আমার বৃত্তির সকল টাকাই বই কিনতে ব্যয় হয়ে যেত। ঢাকা কলেজে এবং কলেজিয়েট স্কুলের লাইব্রেরিতে আমি অগণিত বই পড়ার সুযোগ পাই। তবুও আমার মাঝে বইয়ের ক্ষুধা থেকে যেত, মেটেনি কোনোদিন। নিউ ইয়র্কে এসে সে ক্ষুধা অনেকটা মিটেছে। জীবনে যে দুয়েকটা ক্ষুধা আমাকে সব সময় ভীষণ তাড়া করে ফিরেছে, পুরো মেটেনি কোনোদিন, বই পড়ার ক্ষুধা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। নিউ ইয়র্কের জীবন আমাকে বই সংগ্রহের সহজ সক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু এখনও আমার পড়ার ক্ষুধা সত্যিই গভীর। জীবনের পেছন দিকে ফিরে ভাবি, ছেলেবেলা থেকে যদি আরও বই পড়তে পারতাম, তাহলে মনটা তৃপ্ত হতো কিছুটা। আমি একটু বেশি বয়সে, মধ্য তিরিশে বিদেশে এসেছি, একটু আগে এলে আমার প্রিয় কয়েকটি বিষয়ে আরও পড়তে বা গবেষণা করতে পারতাম মনে হয়! পড়াতেই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই, আজও! এবং তা বিচিত্র সব বিষয়ে!

১৯৫৫ সালে শরীয়তপুরের জাজিরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এসএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে তথ্য ক্যাডারে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৯৩ সালে পড়াশোনার জন্য নিউইয়র্ক যান। নিউইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Communications-এ এমএ এবং নিউ স্কুল থেকে Political Sociology-তে এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি নেন। ২০০১ সাল থেকে নিউজার্সির এসেক্স কলেজে সমাজবিজ্ঞান পড়ান। এছাড়া খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে সমাজবিজ্ঞান পড়ান। নিউইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫ সাল থেকে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখা শুরু। মূলত প্রবন্ধ লেখেন গবেষণা, পড়াশোনা এবং আগ্রহের বিষয় সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান। তিনি সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ এবং ইমদাদুল হক মিলনের ‘পরাধীনতা’ উপন্যাস দুটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এছাড়া দেশের কয়েকজন লেখকের গল্প ও কবিতাও ইংরেজি অনুবাদ করেন। ‘বড় বেদনার মতো বেজেছ’ ছাড়াও তার আরও একটি প্রবন্ধের বই ‘দ্বীপান্তরের গান’। ইংরেজি প্রবন্ধের বই একাধিক। এ-বছরের নতুন ‘Media Power and other Essays’. তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তেরো। ১৯৯৩ সাল থেকে আবেদীন কাদের নিউইয়র্ক প্রবাসী।