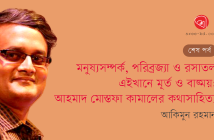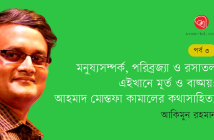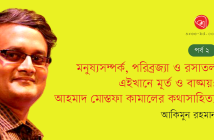উৎসববিমুখ মানুষ পৃথিবীতে ক’জন আছে কে জানে!
উৎসববিমুখ মানুষ পৃথিবীতে ক’জন আছে কে জানে!
এই ক্লেদ ও রক্ত, মারী ও মৃত্যুজর্জর পৃথিবীতে উৎসবকেই কেন্দ্র করেই তো বাঁচার অর্থ খোঁজে মানুষ, খোঁজে তৃষ্ণার শান্তি। এ কারণে নিরবধিকাল ধরে নানারকম উৎসব পালন করে আসছে মানুষ। কেবল একটা উপলক্ষ্য চাই, সেটি যেমনই হোক। উপলক্ষ্য পেলেই জীবনের অজস্র দীর্ঘশ্বাস আর অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তিকে একপাশে সরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মানুষ মেতে ওঠে উৎসবে।

প্রাচীন মিশরীয় উৎসব
একুশ শতকের যন্ত্রময় পৃথিবীতে উৎসবগুলোও হয়ে গেছে যান্ত্রিক। সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তরিত করার অদ্ভুত মেধা নিয়ে জন্ম নেওয়া সওদাগরেরা শ্যেনদৃষ্টি মেলে, থাবা পেতে বসে আছে কখন উৎসবের ডামাডোলে পকেট কেটে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতে পারবে সাধারণ মানুষের। এ কারণেই নতুন নতুন দিবস আর উৎসবের জন্ম হতে দেখি। এ যেন বাণিজ্যের আকাশে উৎসবের বুদ্বুদ-প্রাণ নেই, আবেগ নেই, আছে কেবল পালনের দায়বদ্ধতা আর অন্তঃসারশূন্য কেনাকাটা। কে জানে, একুশ শতকের বাদবাকি সবকিছুর মতো উৎসবেরও হয়তো এমনই হওয়ার কথা।
একুশ শতকের যন্ত্রময় পৃথিবীতে উৎসবগুলোও হয়ে গেছে যান্ত্রিক। সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তরিত করার অদ্ভুত মেধা নিয়ে জন্ম নেওয়া সওদাগরেরা শ্যেনদৃষ্টি মেলে, থাবা পেতে বসে আছে কখন উৎসবের ডামাডোলে পকেট কেটে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতে পারবে সাধারণ মানুষের। এ কারণেই নতুন নতুন দিবস আর উৎসবের জন্ম হতে দেখি।
আমরা বরং বাণিজ্য আর লোক দেখানোর মচ্ছবকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে ফিরে যাই সহস্র বছর আগে। ইতিহাসের ঊষালগ্নে মানুষ কীভাবে উৎসব পালন করত সেটাই দেখে আসি এক ঝলক। ফিরে তাকাই মিশরীয়, রোমান, আথেনীয় আর মায়াসভ্যতার দিকে।
মিশরের পুরনো সভ্যতায় (২৭৮৭ থেকে ২১৯১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সবচেয়ে জমকালো উৎসব ছিল ‘ওয়েপেত রেনপেত’। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ‘বছরের শুরু’। প্রতিবছর নীলনদের প্লাবনের সঙ্গে মিল রেখে পালিত হতো এটি। প্রাচীন মিশরীয়দের জীবন নীলনদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। উত্তর আফ্রিকার পর্বত এলাকার প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে দেখা দিত নীলনদের প্লাবন, এ সময় নীলের দুপাশে পলিমাটির যে গভীর স্তরের সৃষ্টি হতো মিশরীয় কৃষকদের জন্য সেটিই ছিল প্রকৃতির পরম আশীর্বাদ। কৃতজ্ঞতাভরে নতুন বছরকে বরণ করার জন্য তাঁরা পালন করতেন ‘ওয়েপেত রেনপেত’ উৎসব, যেটি শুরু হতো জুলাইয়ের মাঝামাঝি। ধুপধুনো আর প্রদীপ জ্বালিয়ে, মন্দিরে আরাধনা করে এটি পালন করতেন তাঁরা, মিশরীয় নৃপতি ফারাও-ও এ উপলক্ষ্যে দর্শন দিতেন প্রজাদের। উৎসবের দিন বিকেলে রুটি, আঙ্গুর, ডালিম, খেজুর, তরমুজ, গোমাংস, মাছ আর প্রচুর পরিমাণে বিয়ার খেয়ে আনন্দে মাতত মানুষ। ধনী মিশরীয়রা করতেন এন্তার মদ্যপান। আবার এ সময়টাতেই সরকারি কর্মকর্তারা খামারে খামারে গিয়ে কতটুকু শস্য উৎপাদিত হতে পারে তার নিরিখে হিসাব করতেন কোন খামারির ঘাড়ে চাপানো হবে কতটুকু করের জোয়াল।
প্রাচীন রোমানরা শনিদেবতার সম্মানে পালন করতো ‘স্যাটারনালিয়া’ উৎসব। স্যাটার্ন ছিলেন বীজ রোপণের দেবতা। প্রতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পালিত হতো এ উৎসব, নতুন চারা রোপণের ঠিক পরপর।
প্রাচীন রোমানরা শনিদেবতার সম্মানে পালন করতো ‘স্যাটারনালিয়া’ উৎসব। স্যাটার্ন ছিলেন বীজ রোপণের দেবতা। প্রতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পালিত হতো এ উৎসব, নতুন চারা রোপণের ঠিক পরপর। প্রথম শতাব্দীতে লেখা দার্শনিক সেনেকার একটা চিঠি থেকে জানা যায়, রোমানরা স্যাটারনালিয়া উৎসবকে টেনে নিয়ে যেত নির্দিষ্ট দিন থেকে আরও বেশ খানিকটা সামনে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্যাটারনালিয়া পালিত হতো এক সপ্তাহ জুড়ে। ইতিহাসবিদ ক্যান্ড্রা এসেলম্যান লিখেছেন, এ উৎসবের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুটো অনুষঙ্গ ছিল। জনসমক্ষে যে উৎসব তার অন্যতম অংশ ছিল শনিদেবতার উদ্দেশে পশু বলিদান। আর পারিবারিক পর্যায়ে যে উৎসব— তার প্রধান অনুষঙ্গ ছিল নানারকমের খেলাধুলা, মদ্যপান, চটকদার পোশাক পরা আর ভোজ। বছরভর মেনে চলা সামাজিক প্রথা ভেঙে উৎসবের উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠত সবাই। প্রথাগত সাদা পোশাকের পরিবর্তে রঙিন পোশাক পরত মানুষ, ভৃত্যদের সঙ্গে বসে খাবার খেত মালিকেরা, এমনকি কখনও কখনও ভৃত্যদের খাবার পরিবেশন করত। এসেলম্যান লিখেছেন, ‘স্যাটারনালিয়ার সময় সামাজিক স্তরবিন্যাস উল্টে যেত।’ এর কারণ হচ্ছে, প্রাচীন রোমান নথিপত্র অনুসারে, স্যাটারনালিয়া বা শনির সময় হচ্ছে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের। ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার সময় বিশেষ যে টুপি পরানো হতো সেটিই পরত প্রভু-ক্রীতদাস নির্বিশেষে সবাই, সমতার উৎসব স্যাটারনালিয়ার সম্মানে।

প্রাচীন গ্রীকের বিয়ের অনুষ্ঠান
এবার বলি প্রাচীন মায়াসভ্যতার কথা। মধ্য আমেরিকান এই সভ্যতার মানুষের দুটো দিনপঞ্জিকা ছিল। একটি অনুসারে বছরের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬৫ দিন, অন্যটি অনুসারে ২৬০ দিন। যেহেতু তাদের ৩৬৫ দিনের ক্যালেন্ডারেও লিপ ইয়ার ছিল না সেহেতু তাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব কা’তুন-এর সঠিক তারিখটি হিসাব করে বের করা কঠিন। তবে এটুকু জানা যায় যে মায়া ক্যালেন্ডারে কা’তুন ছিল সবচেয়ে বড়ো উৎসব এবং প্রতি বছরের শেষভাগে এটি পালিত হতো। প্রতি দু’ দশক পরপর এটি পালন করা হতো বিশেষভাবে, চোখ ধাঁধানো আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে। টার্কি মোরগ, ভুট্টা, মধু, কোকো এবং পানীয় সহযোগে ভোজসভার আয়োজন করা হতো। বড়ো বড়ো শহরে পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষও যোগ দিত ভোজসভায়। ভোজসভার অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন স্বয়ং রাজা, যিনি মণিমুক্তাখচিত দামি পোশাক পরে উৎসবে অংশ নিতেন। রাজার পোশাকের শোভা বাড়াত বহুমূল্য জেড পাথর, মায়া প্রথানুসারে যে পাথরের ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা।
এনথেস্টেরিয়ার শাব্দিক অর্থ ‘নতুন মদের উৎসব’। সুরার দেবতা ডায়োনিসাস-এর সম্মানে পালিত হতো এ উৎসব, নতুন শস্য ওঠার ঠিক আগে। ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে তিনদিন ধরে চলত এ উৎসব এবং নতুন তৈরি করা মদের জার খোলার মাধ্যমে সূচনা হতো এর। উৎসবের তৃতীয় দিনে বিরাজ করত ভাবগম্ভীর পরিবেশ।
সবশেষে বলি এনথেস্টেরিয়ার কথা, যা ছিল প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। এনথেস্টেরিয়ার শাব্দিক অর্থ ‘নতুন মদের উৎসব’। সুরার দেবতা ডায়োনিসাস-এর সম্মানে পালিত হতো এ উৎসব, নতুন শস্য ওঠার ঠিক আগে। ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে তিনদিন ধরে চলত এ উৎসব এবং নতুন তৈরি করা মদের জার খোলার মাধ্যমে সূচনা হতো এর। উৎসবের তৃতীয় দিনে বিরাজ করত ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ইতিহাসবিদ নোয়েল রবার্টসনের মতে, ‘ডায়োনিসাস হচ্ছেন নতুন জীবন আর আনন্দ বয়ে আনা দেবতা, একইসঙ্গে আত্মার নিয়তি আর মৃতদেরও দেবতা তিনি।’ এ কারণেই উৎসবের তৃতীয় দিনে মৃতদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হতো বীজ এবং গমের পাত্র— যারা উৎসবের দিনগুলোতে জীবিত মানুষদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলে বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিকরা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এনথেস্টেরিয়ার বেশিরভাগ তথ্যই কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও এটি জানা গেছে যে, এটি ছিল উদ্দাম, বল্গাহীন মদ্যপানের সময়। মদ্যপানের এই উৎসবে স্বাগত জানানো হতো এমনকি ক্রীতদাস ও শিশুদেরও। উৎসবের প্রথম দিনটির নাম ছিল পিথোইজিয়া। যখন মদের নতুন জার খোলা হতো, ডায়োনিসাসের উদ্দেশে পাত্র থেকে ঢালা হতো মদ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হতো তাঁর উদ্দেশে। দ্বিতীয় দিনের নাম ছিল খোস। কে কত মদ্যপান করতে পারে তার প্রতিযোগিতা হতো এদিন। দেবতা ডায়োনিসাসের সাথে রাজমহিষীর গোপন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হতো এদিন। ডায়োনিসাসের মন্দিরের একটি গুপ্তকক্ষে আয়োজিত হতো এ আনুষ্ঠানিকতা। তৃতীয় দিনটির নাম ছিল খাইত্রাই। এদিনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো মৃতদের উদ্দেশে। নানারকম খাবার এবং শস্যবীজ বিশেষ পাত্রে করে রেখে দেওয়া হতো মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে। তবে মৃতদের আত্মাকে যথেষ্ট সম্মান করা হলেও তারা যেন খুব কাছে চলে না আসে সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা হতো। বিশেষ ধরনের ভেষজ চিবানো, মন্দিরে দড়ির বেষ্টনী দিয়ে রাখা এবং বাড়ির দরজায় আলকাতরা মাখিয়ে রাখা হতো মৃতদের আত্মাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার জন্য।

জন্ম ফেনীতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বর্তমানে একই বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। লেখালেখির শুরু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, পত্রপত্রিকায়। গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি ইতিহাস, তথ্যপ্রযুক্তি, ছোটোদের জন্য রূপকথা নানা বিষয়ে লিখেছেন। বিশেষ আগ্রহ অনুবাদে। সিলভিয়া প্লাথের ‘দি বেল জার’ ছাড়াও ইতিহাসভিত্তিক কয়েকটি বই অনুবাদ করেছেন। মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বাইশ।