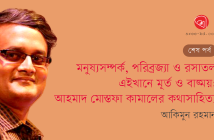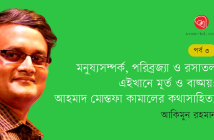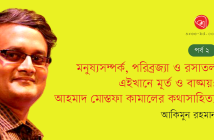এক.
ভূমিকা
জীবনের উপান্তে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’। জীবনের শুরুতেও একবার ‘মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’-এর প্রত্যয় দৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। মানুষকে গ্রহণ করেছিলেন অথবা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন মানুষের ভিতরের শুভশক্তির উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে। ‘মানবকে মহান বলে জেনো’ এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা এবং সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুই ছিল মানুষ। যে মানুষ খণ্ডিত নয়, বিভাজিত নয়; যে মানুষ ঐক্যের মধ্যদিয়ে, সংস্কারের মধ্যদিয়ে মহামানবে উন্নীত সেই মানুষ। যে মানুষের চেতনাই সকল কিছুর নির্ধারণকারী এবং সৃষ্টিকারী। মানুষের চেতানাকে তাই মানবিক করে, সৃষ্টিশীল করে এবং কর্মময় করে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবগত এবং বস্তুগত কর্মময়তা চালিয়ে গেছেন আমৃত্যু। একজন পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি মানুষের ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করার কথা কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে যেমন লিখে গেছেন তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে, গ্রাম উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। একারণেই প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন,‘ রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন।’ আরেক প্রখ্যাত সমাজ চিন্তক, গবেষক, লেখক যতীন সরকার এই বেঁচে থাকার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—
বেঁচে থাকা মানে প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠতে থাকা, নব নব সৃষ্টিশীলতার মধ্যদিয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলতে থাকা, পুরনো পশ্চাৎপদ ভাবনার বৃত্ত ভেঙে কেবলই সামনে যেতে থাকা, প্রতি মুহূর্তে নবীন তাজা বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকা, সর্বদা বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া অনুভব করতে থাকা, ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে বৈশ্বিক ও সর্বমানবিক স্বার্থের মহাসমুদ্রের দিকে জীবনপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা।
এইসব ভাবনা একটি কলোনিয়াল পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথ যে কোনভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হননি তা কিন্তু নয়। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের মতো আরো অনেকেরই উত্তরাধিকার তিনি বহন করেছেন। পরাধীন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জাগরণের কালে যে জন্মেছিলেন সে কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। অন্যদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ধারাবাহিক যোগসূত্রতা থাকলেও রবীন্দ্রচিন্তনের গভীরতা এবং ব্যাপকতা অন্যদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ সকল কিছুর একটি জাতীয় পরিচয় খাড়া করতে চেয়েছেন। সেটি যেমন মানুষের মানস কাঠামোগত তেমনি শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও। ‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার/ সেথা হতে সবে আনে উপহার।/ দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে…’ এইসবভাবনার পিছনেও রয়েছে জাতীয় পরিচয় দাঁড় করানোর তাগিদ। তিনি স্পষ্টই উচ্চারণ করেছেন,‘আত্মবিলোপ নয় আত্মআবিষ্কার’। তিনি আমাদের দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন আত্মপরিচয়ে দৃঢ় চিত্তের নাগরিক হিসেবে। এই পরিচয় ভূমিলগ্ন, নিজের সংস্কৃতিলগ্ন। নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টকোন থেকে তাঁর সাহিত্যকর্ম বিচার করলেও আমরা দেখতে পারব যে সেখানেও তিনি নিজ ভূমিজাত সংষ্কৃতিকে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর সংগীত ও নাটকে এই বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। একসময় সরাসরি বলেছেন ‘ঐসব ইউরোপিয় বর্বরতা পরিহার করিতে হইবে।’ তবে রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর নিজের ভাবনা সংস্কারকৃত অর্থাৎ সংস্কৃত করতে হয়েছে। জীবনের শুরুর দিকে তিনি যে ইউরোপের সবকিছুকেই অকাতরে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন তার নজিরও কম নেই।
আমরা তাই রবীন্দ্রনাথকে, যে রবীন্দ্রনাথ মানবকে মহান বলে জানার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন এবং মানুষকে মানবে উত্তীর্ণ হবার জন্য ভাবগত এবং বস্তুগত পথ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন আর এইসবকিছু করবার জন্য বাংলার সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনার জন্য বাংলার সংস্কৃতি, সংস্কৃতির নানা মাত্রিকতা, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আলো ফেলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন খুঁজতে চাই বর্তমান সমায়ের নানান সংকটের মাঝে। এর মধ্যদিয়েই ‘তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি’ এই মনোবৃত্তির নিরসন ঘটিয়ে বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা অথবা প্রয়োজনিয়তার বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে চাই। সেই সময়ই করতে চাই যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে পরাজয় ঘটছে মানুষের।
দুই.
বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য
রবীন্দ্রভাবনার প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্য বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলার সাংস্কৃতিক আবহেই গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রমানস।
দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা নামের যে ভৌগলিক সীমানা তৈরি হলো, সেই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় বিশ্লেষণ করলে আমরা যে বিষয়গুলি পাই তা হলো—বহুত্ববাদের সমন্বয়, বৈচিত্র্য, আত্মিকরণ প্রবনতা, সাম্যচেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, মানবতা। এইসব বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাব ও চলন বাংলার মানুষের মানস নির্মাণ করেছে। নির্মিত এই মানসে ভৌগলিক প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ভৌগলিক সীমানায় জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম, প্রকৃতির প্রভাব। মাটিলগ্ন মানুষের জীবন চেতনায় তাই লোকধর্ম প্রভাব ফেলেছে বিস্তর।
বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে সমন্বয় ধর্মিতা লক্ষ করা যায়। বহিরাগত সব ধর্মই বাংলায় এসে বঙ্গীয় রূপ গ্রহণ করেছে। বাঙালি সংস্কৃতির পর্যালোনা প্রসঙ্গে আহমেদ শরিফ বলেছেন— “বাঙালি মনোভূমি কর্ষণ করেছে সযত্নে। এবং এই কর্ষিত ভূমে মানবিক সমস্যার বীজ বপন করে সমাধানের ফল ও ফসল পেতে হয়েছে উৎসুক।… এইজন্য বর্ণবাদী বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেও সে কায়া সাধনায় নিষ্ঠ। তার কাছে এ মর্ত্য জীবনই সত্য।” বৌদ্ধযুগ বাঙালির বেঁচে থকার লড়াইটাকে তাই তাঁর মন্তব্য,— ‘বাঁচার কেবল মাটি আঁকড়ে বাঁচার।’ বাঁচার অনুষঙ্গগুলি উঠে এসেছে হরগৌরীর মহাযান, দীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা-কানুফা, ময়নামতি-গোপী চাঁদ প্রভৃতির নামে। বঙালি তার জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য লোকায়ত দেব-দেবী নির্মণ করে তাদের আরাধনা করেছে। মনসা, চণ্ডী, শিতলা, ষষ্ঠী, শনি বাঙালির সৃষ্টি। এই দেব-দেবীরা জীবনলগ্ন। ওহাবী-ফারায়েজী আন্দোলন পূর্ব ইসলাম একপ্রকার লৌকিক রূপ গ্রহণ করেছিল। আহমেদ শরীফের মতে—
পার্থিব জীবনের স্বস্তির ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য কল্পিত হয়েছিলেন দেব-প্রতিম পাঁচবিবি ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্থ পেয়েছে দরগাহ…তারপরেও প্রয়োজন হয়েছিল সত্যপীর-খিজির-বড়খাঁ-গাজী-কালু-বনবিবি-ওলাবিবি প্রভৃতি দেবকল্প কাল্পনিক পীরের।
বাঙালি সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে এর ভৌগলিক অবস্থান। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে তার চিন্তায় ও কর্মে। সৃজনশীলতায় উঠে এসেছে মাটি ও মানুষলগ্নতা। বহুধর্মের প্রচলন থাকার পরেও এখনকার মানুষ অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই চেতনাই তকে পরিচালিত করেছে।
ভৌগলিক কারণেই বঙ্গবাসীর মাঝে নানাধরনের সাংস্কৃতিক বিভাজন রয়েছে। কিন্তু এই বিভাজনের পরেও বাঙালির মধ্যে যে ঐক্যের ধারা নির্মিত হয়েছে তা ভাষার মধ্যদিয়ে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,“বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভুগলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবুও এরমধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি”।
তিন.
বিশ্বায়নের সংস্কৃতি ও সংকট
কিন্তু ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই ভাবনা ধারনকারী বঙ্গবাসী আজ বিশ্বায়ন সংস্কৃতির সংকটে। রবীন্দ্রনাথ একভাবে যাকে বলেছিলেন ‘সভ্যতার’ সংকট। গোটা পৃথিবীতে আজ আন্তর্জাতিকতাবাদের স্থান দখল করেছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের জোয়ারে সবাই এখন প্লাবিত। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বত্র বিশ্বায়নের থাবা প্রসারিত। যদিও বিশ্বায়নের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ধারনা নেই। সাধারণভাবে উৎপাদন. শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, বিনিময়, পুঁজি, তথ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদিও বিশ্বব্যাপী বিস্তার হলো বিশ্বায়ন। তবে প্রকৃত অর্থে বিশ্বায়ন বলতে বুঝায়Ñ পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ। বিশ্বের সকল দেশের সকল প্রান্তকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শৃঙ্খলে বাঁধা। এই বিশ্বায়ন একদিকে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা সহ সকল প্রকার দুর্দশা দূরকরার বস্তুগত সম্পদে সমৃদ্ধ করছে মানবজাতীকে। তেমনি পৃথিবীজুড়ে শোষণ-বঞ্চনা-অন্যায়-অবিচার বিলোপ করে গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায়বিচার, শান্তি, মানবাধিকার ও মানবিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্বায়নের এই সম্ভাবনা বাস্তবরূপ লাভ করেনি। বরং দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসাম্য, কালোরাজনীতি-অর্থনীতি, দুর্বৃত্তায়ন, ভোগবাদ, সন্ত্রাস, যুদ্ধ-সংঘাত, বেকারত্ব ইত্যাদি বিশ্বায়নের সহযোগী হয়েছে। মার্কিন মুল্লুক থেকে উৎসারিত এক বিশ্বায়নী সংস্কৃতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। একারণে দেশে দেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লোপ পেতে চলেছে। নিজস্ব সংস্কৃতি হারানোর ভীতি মানুষকে বিচলিত করছে। একই ধরনের পোশাক, আহার্য ও পানীয় গ্রহণ স্মার্ট, উন্নত বা আধুনিক জীবনের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশ্বায়নের সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে অসহায় বোধ জাগিয়ে তুলছে। নিঃশর্তভাবে বাজারের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য মনোজাগতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করছে। বাজার অর্থনীতির তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এর কোন বিকল্প নেই প্রচার চালাচ্ছে। বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদের কাব্যগাথা। জনপ্রিয় সংস্কৃতির নানা আয়োজনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বাজারি ব্যবস্থার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য বিস্তার চলছে। অন্যদিকে মানুষের সৃজনশীল ও মানবিক সজীব কর্মতৎপরতা আটকে পড়ছে সাইবার/ ডিজিটাল সংস্কৃতির ফাঁদে। গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তব সংগ্রামের স্থান দখল করছে এখন ই-মেইল, ফেসবুক, ব্লগ, টুইটার, টক শো। ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে সবাই সমান ঘোষণা করা হলেও এই নয়া গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি সৃষ্ট মহাসড়কে হাঁটার সুযোগ নেই বিশ্বের শত শত কোটি মানুষের। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নির্দিষ্টমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগহীনতা এ ক্ষেত্রে বাধা। কেননা কোটি কোটি মানুষের ঘরে টিভি, কম্পিউটার নেই। অসংখ্য মানুষ এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে। তাই এ অবস্থা নতুন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করছে। মানুষ কেবল ধনের গরীব নয়, জ্ঞানের গরীবও হচ্ছে। শুধুু তাই নয় এ তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের উপর অতিনির্ভরশীলতা মানুষকে স্বেচ্ছা বন্দীত্বের কারাগারে নিক্ষেপ করছে। ঘরে-বাইরে মানুষ এখন মজে আছে মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভি নিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির এ উপকরণসর্বস্বতা মানবীয় সম্পর্কহীনতায় ঠেলে দিয়ে মানুষের বিমানবিকীকরণ ঘটাচ্ছে।
বস্তুত মানুষের ঐক্যময়তা, সামষ্টিকতাকে ধ্বংস করছে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমঅধিকার, সমবণ্টন, ন্যায্যতার বদলে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, মনুষ্যত্বহীনতা, বৈষম্য ও পক্ষপাত এখন এই সংস্কৃতির আদর্শ। বিশ্বমানবজাতিকে জাত-পাত, লিঙ্গ, গোষ্ঠী, বর্ণ ও অঞ্চল ইত্যাদি বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্তিত্বে বিভাজিত করা হচ্ছে। শ্রেণিচেতনার স্থানে জন্ম নিচ্ছে নানা ভ্রান্ত চেতনা। ফলে বিশ্বমানবজাতি জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে গণশত্রুর বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারছে না। বর্তমান সময়ের সংকটগুলি যা সাধারণ মানুষকে সর্বতভাবে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে সেইসব উপাদান গজিয়ে উঠেছে রাষ্ট্রব্যাবস্থার পরিকাঠামোর মাঝেই। সরাসরি বলা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আমাদের উপহার দিয়েছে মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী একটি সমাজ কাঠামো। কী আছে এই ব্যাবস্থার মাঝে? অগণতান্ত্রিক, লুটেরা, দুর্নীতিপরায়ণতা, নীতিহীন রাজনীতির নোংরামো, অসাম্প্রদায়িক চেতনা নষ্ট করে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্য, সর্বত্র বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি, কর্পরেট পুঁজি ও কর্পরেট সংস্কৃতির আগ্রাসন, জাতীয় পরিচয় ও সাস্কৃতিক বৈচিত্র্য নষ্ট করে একই ছাঁচে সব মানুষকে ঢালা। এইসবই একটি মানবিক সমাজ নির্মাণের পরিপন্থি। মানুষের এই পরাজয়ের কালে দেখতে চাই রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক কিনা।
চার.
রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গিকতা: অতীত পর্যালোচনা
আমরা রবীন্দ্রনাথকে এখন বহন করে নিয়ে চলেছি নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। পাঠ্যপুস্তক, ২৫শে বৈশাখ-২২শে শ্রাবণ, সভা-সেমিনার ইত্যাদির মাঝে রবীন্দ্রনাথ আটকে গেছেন। কিন্তু এই ‘বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ’কে মুক্ত করে সংকটে কাজে লাগনো যায় কিনা তার চেষ্টা করাটাই জরুরি।
অতীতে নানান সংকটে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হাত ধরেছেন। ‘শুভকর্মপথে’ নির্ভয়ে গান গাইবার সাহস জুগিয়েছেন। চেতানায় দেশপ্রেম জাগ্রত করেছেন। রবীন্দ্রনাথতো শুধু লিখে আমাদের পথ নির্দেশ করেন নি। তাঁর ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর জন্য নিজেই কর্মী হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করে রাস্তায় নেমেছেন, গান লিখে মানুষের অন্তরে স্বদেশ প্রেম এবং অসাম্প্রদায়িক বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন, নাইট উপাধী পরিত্যাগ করেছেন। কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি বাস্তবে তা রূপদানের জন্য কাজ করেছেন। শিক্ষাব্যাবস্থা নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি তার বাস্তব প্রয়োগও ঘটিয়েছেন।
১৯৪৭ পরবর্তী তৎতালীন পূর্বপকিস্তানে যখন বাঙালি, বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেবার পাঁয়তারা চলছিলো তখন রবীন্দ্রনাথই আলো ধরেছিলেন, পথ দেখিয়েছিলেন। বাঙালিকে পথ দেখানো রবীন্দ্রনাথকে একারণেই পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। রবীন্দ্রচর্চার মধ্যদিয়ে যাতে পূর্ববাংলার মানুষ আত্মশক্তি লাভ করতে না পারে তার সমূহ ব্যবস্থা করেছিলো পাকিস্তান সরকার। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন, এই সংগীত পাকিস্তানের আদর্শের বিরোধী। সেই সময়ের কিছু বিশিষ্ট নাগরিক এই নির্দেশের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। পাল্টা বিবৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ব্যক্তিরা। এর প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা), ছায়ানট, ক্রান্তির সম্মিলিত অনুষ্ঠান। এর মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রচর্চার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
উপমহাদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরির নামে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। এখানে রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়েছেন কলিম শরাফী, ভক্তিময় সেনগুপ্ত এবং আরো পরে আতিকুল ইসলাম। তৎকালীন পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় এই সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বুবুল ললিতকলা একাডেমি রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ভালোভাবেই চালিয়ে গেছে সেইসময়। এমনকি শান্তিনিকেতন থেকে ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে এসে তারা অনুষ্ঠান করেছে। কলকাতা থেকে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষদের নিয়ে এসে তারা অনুষ্ঠানে গান গাইয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির বিরাট ভূমিকা ছিলো সেই সময়।
১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের পরই গড়ে ওঠে সমমনা সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে ‘ছায়ানট’। ঢাকায় রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখের আবাহনী অনুষ্ঠান শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান আমলে এগুলো ছিল প্রতিবাদেরই প্রকাশ। এই প্রতিবাদের শরিক হয় ছোটবড় আরো সাংস্কৃতিক সংগঠন। আন্দোলনের নানা পর্বে নানা অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। ‘সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গাওয়া হয়েছে মিছিলে। অনুষ্ঠান হলে সেখানে ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ গাওয়া হয়েছে। সময়ের কথা বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গান দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন শিল্পীরা— ‘কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে। কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ’পরে, সে যে আমার জননী রে।’ এর পরের কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ— ‘কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি। কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়, সে যে আমার জননীরে।’ এই গানটা রবীন্দ্রনাথ বহু আগে (১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা ভাষায় যে বক্তৃতা দেয়া হত না তা নিয়ে দুঃখ করে লিখেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের পরে এই গানটা নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এছাড়াও পাকিস্তান আমলে শিল্পীরা যেটা করেছিলেন, যখনই কোনো একটা বিরূপ ব্যাপার হত তখনই রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে মনের ব্যথা- ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। একটা অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিলো এরকমই একটি গান— ‘কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো! বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।’ এবং সেটা বিশেষভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া একবার পাকিস্তানে আইয়ুব খানের আমলে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের গ্রামে শিশুনারী নির্বিশেষে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আর্মি গিয়ে করেছিল। সেই সময় বৌদ্ধরা কয়েকজন ঢাকায় এসেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের কাছে আশ্রয় খুঁজতে। তারা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তারা রবীন্দ্রনাথের গান শিখে, সেই গান গেয়ে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’, সহ আরো কিছু গান শিখে তারা অনুষ্ঠান করেছিলেন। এও রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা। সংকটে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে বাঁচার জন্য সাহস সঞ্চয় করা।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নানা উদ্দীপক গানের সঙ্গে প্রচারিত হয় রবীন্দ্রনাথের গান। সনজীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক এঁদের সক্রিয় উদ্যোগে গড়ে ওঠে গানের দল। তাঁরা ঘুরে বেড়ান মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। কাজেই রবীন্দ্রসংগীত আমাদের আন্দোলনের মস্তবড় একটা হাতিয়ার ছিল ।
এর চেয়েও ভয়াবহ সংকটে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরেছিলেন একদল মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। এই ঘটনা আমাদের দেশে নয়, পোল্যান্ডে। ১৯৪১ সালে জার্মানি পোল্যান্ড দখল করে নেয়। অকথ্য অত্যাচার চালায় পোল্যান্ডবাসীর উপর। নির্বিচারে হত্যা করে মানুষ। যত ইহুদি ছিলো তাদের হত্যা করা হয় আউসউইচ-এর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে। পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে ১৯১২ সালে সে যুগের বিখ্যাত পেডিয়াট্রিশিয়ান ড. কোরচখ খুলেছিলেন একটি অনাথ আশ্রম। নিজে ইহুদি না হয়েও ইহুদি অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম খুলেছিলেন তিনি। কোরচখ একজন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকও ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মাত্র ১৮ দিনের মাথায় নাৎসিবাহিনী পোল্যান্ড দখল করে নেয়। অনাথ আশ্রমের বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয় নাৎসিবাহিনীর জন্য। এর কিছুদিন পর নাৎসিবাহিনী ড. কোরচখকে আদেশ দেন তাঁর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাচ্চাদের নিয়ে গ্যাস চেম্বারে যাবার জন্য। এরপরও ডাক্তার অবিচলিত থেকে আশ্রমের ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি চারমাস পরপর যে নাটক অভিনয় করার কথা ছিলো তার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আর এবারের নাটক হলো রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’। ড. কোরচখ নিহত হবার আগে ডাইরি লিখতেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিটলারের সেন্সর বাহিনীর নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাৎসি জার্মানিতে নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু তারপরও কোরচখ এটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর কোরচখ এবং তার অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের সহকারী সমেত অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয় । আশ্রমমাতা ডন ব্লচকে ডাক্তার জানালেন মৃত্যু যখন সন্নিকটে তখন তারা ‘ডাকঘর’ নাটক করবেন মৃত্যুপথযাত্রী বাচ্চাদের নিয়ে। তিনদিনে পোলিশ ভাষায় নাটকটি অনুবাদ করে ফেলেন। শেষপর্যন্ত ‘ডাকঘর’-এর অভিনয় হলো ১৮ জুলাই, ১৯৪২-এ। এর ঠিক ১৭ দিন পর, ৫ আগস্ট ১৯৪২ এদের মেরে ফেলা হলো।
এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, নাৎসিবাহিনীর ভয়াবহতার মাঝে ‘ডাকঘর’ কেনো? কেনো কোরচখ আশ্রয় খুঁজলেন এই নাটকে? উত্তর একটাই মুক্তিপথের নিশানা খোঁজার জন্য। নারায়ণ সান্যাল তাঁর ‘মৃত্যোর্মা অমৃতাম্’ গ্রন্থে ড. কোরচখ এবং তাঁর অনাথ শিশুদের উল্লেখ করে লিখেছেন যে, মৃত্যুপথযাত্রীরা গান গাইতে গাইতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাটল ওয়াগানের দিকে এগিয়ে যায়। আর গনেটি ছিলো,‘তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চল রে।’
নব্বইয়ের দশকে, সভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার কালে, রবীন্দ্রনাথকে সমাজতন্ত্রের পক্ষের এবং বিপক্ষের দুই দলই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলো। ১৯৩০-এ স্ট্যালিনের আমলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ঘুরে এসে রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মত ব্যক্ত করেছিরেন এবং যা ‘রাশিয়ার চিঠি’ নামে বই হিসেবে ছাপা হয়েছিলো সেই মত ৬০ বছর পর সোভিয়েত ভাঙার কালে পুঁজিবাদীদের ‘আলোকিত সামাজিক উদ্যোক্তাদে’র কাছে এবং সমাজতান্ত্রিক গ্রুপের ‘নবায়িত সমাজতন্ত্রে’র প্রবক্তাদের কাছে— এই উভয় চিন্তাধারার কাছেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে খুবই প্রত্যক্ষ এবং প্রায়োগিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন বা প্রয়োজনে কাজে লেগেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।
পাঁচ.
রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা: বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে
বর্তমান সংকটের কালে রবীন্দ্রনাথকে শুধু বহন না করে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা ভাবা প্রয়োজন। তাঁকে কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির সঙ্গে অথবা নীতির নানান উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়া যায় এবং তা নিশ্চয়ই অন্ধের মতো বা ভক্তি গদগদ চিত্তে নয় বরং বর্তমান বিশ্বব্যাবস্থার নানান আনুষাঙ্গীক বিষয়কে ধারণ করে, রবীন্দ্রনাথকে নতুন কালের প্রেক্ষাপটে আবিষ্কার করা যায় সেই ভাবনাটা জরুরি। আমরা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়গুলি লক্ষ করি তা হলো মানবিকাতর বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িকতার উত্থান, আত্মশক্তি বিবর্জিত পরাশ্রয় প্রিয়তা, দেশপ্রেমহীন লুটেরা মনোবৃত্তি, স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য পরিবেশ ধ্বংস করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে শিক্ষাকে সর্বতভাবে বাণিজ্যিকিকরণ, জাতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময়তার বিলোপ ঘটিয়ে এক ছাঁচের হৃদয়হীন যন্ত্র হয়ে ওঠা।
রবীন্দ্রনাথ মানুষের খণ্ডায়ণকে বিশ্বাস করেন নি। মানুষকে একটি ইউনিটে দেখতে চেয়েছেন। বর্তমান সময়ে মানুষকে নানাভাবে বিভাজিত করা হয়েছে। ধর্মে, লিঙ্গে, শ্রেণিতে মানুষ আজ বিভাজিত। সকল মানুষকে একটি ঐক্যের মাঝে নিয়ে আসা ছিলো রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। ‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—
একত্র সংঘঠনসমূহ সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্ব-চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।…কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।
‘রাশিয়ার চিঠি’তে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন,‘অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধ।’
হিন্দু-মুসলিম বিভাজন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন এবং লিখেছেন। হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য কামনা করেছেন। তিনি মনে করেছেন একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে। ১৯০৮-এ যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে তখন পাবনায় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বিষয়টির দিকে ইংগিত করেছেন। তাঁর ভাষ্যে—
চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন ঘটিবে না।…ভারতবর্ষে এই দুইটি প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্র সম্মিলনের মধ্যে বাধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।
বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে, যন্ত্র দ্বারা যে ভাবে মানবিকতার বিপর্যয় সাধিত হচ্ছে নিশ্চয়ই তা উদ্বেগের বিষয়। যন্ত্রদ্বারা যখন মানুষ পরিচালিত হয় তখন মানবিকতার কোনো জায়গা থাকতে পারে না। আমরা এনই এক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। যান্ত্রিকতা মানুষকে মুনাফালোভী করে ফেলে এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দেয়। ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য আমাদের মতে এখনও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,“আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে শুধু তার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করাটা মানুষের কর্তব্য নয়, বরং মুনুষ্যত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে নতুন ভাবে নির্মাণ করাই জরুরী।” মুনূষ্যত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে যেদিকে তা নিশ্চয়ই মানবিক নয়। সুতরাং এইসব বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনা যে আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
আমাদের শিক্ষাব্যাবস্থা আমাদের মুনাফালোভী যান্ত্রিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। শিশুর শৈশব, কিশরের কৈশোর. তরুণের তারুণ্য হত্যা করে দিয়েছে। পাশাপাশি আমাদের জাতীয় পরিচয়হীন, প্রতিবাদহীন একটি জাতীতে পরিণত করে দিচ্ছে। শিক্ষার বদলে পরীক্ষাটাই মূল হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন এবং তাঁর ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য চেষ্টাও করেছেন। কতটুকু সফল হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে অথবা বৈশ্বিক নানাবিধ পরিবর্তনের মাঝে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রায়োগিক অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু আমরা যদি একটি মানবিক সমাজব্যাবস্থার আকাক্সক্ষা করি তাহলে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের দিকে নজর দেয়াটা জরুরি বলে মানা যেতে পারে আর সেখানে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াটি খোলা রাখা যেতে পারে। শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমরা স্মরণ করতেই পারি। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—
ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গা, কেবলই ঠেঙ্গা লাঠি মুখস্থ এবং একজামিন আমাদের এই ‘মানব জনম’— আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্রলভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধুলির সঙ্গে অবিশ্রাম কর্ষণ রস থাকা চাই।
ছয়.
রামপ্রসাদ বলেছিলেন ‘মন রে কৃষিকাজ জানো না/এই মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা’। রবীন্দ্রনাথ এই ‘মানবজমিন’ পতিত না রেখে সেখানে সোনা ফলানোরই আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুই হলো মানুষ এবং একটি মানবিক সমাজ নির্মাণ। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ‘এই বিশ্ব তো মানুষেরই পৃথিবী’। আজকে অমানবিকতার কালে মানবিক সমাজ বিনির্মাণে তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন।
আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথের দুটি লোখার দিকে একটু মনোযোগ রাখতে চাই, একটি ‘The Religion of Man’, অন্যটি ‘শিশুতীর্থ’। প্রথমটি প্রবন্ধ গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি একটি দীর্ঘ কবিতা। ১৯৩০-এ, যে বছর ‘শিশুতীর্থ’ লেখা হয়, সে বছর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ সফর করেন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুটি— এক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা প্রদান এবং দুই তাঁর ছবির প্রদর্শনী। এ ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে সেটি হচ্ছে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ। রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট বক্তৃতা (১৯, ২১ ও ২৬ মে) যে বিষয়ে দিয়েছিলেন সেটি হল ‘The Religion of Man’ যা পরে ‘মানুষের ধর্ম’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মাঝে ২৪ মে ‘কোয়েকারদের’ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। ‘সোসাইট অব ফ্রেন্ডেস’-এর সদস্যদের সাধারণ মানুষ অবজ্ঞাভরে ‘কোয়েকার’ বলত। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ধর্মনেতা জর্জফক্স (১৬২৪-৯১) ‘সোসাইট অব ফ্রেন্ডেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা শান্তিবাদী ও পরোপকারী। কোয়েকারদের ২২৬ বছরের ইতিহাসে নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরের কাউকে তারা বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই প্রথম। শান্তিবাদী এই সম্প্রদায় ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তা শান্তির পথে সমাধানের উপায় খুঁজছিলো। একারণেই তারা ভারতের কথা শোনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর দুঃখের কারণ কী সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন,“ যন্ত্ররাজ্যে হৃদয়ের স্থান নাই, গবর্মেন্ট যন্ত্র চালিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে লোক এত বেদনা সহিতেছে, তাহার কারণ যন্ত্রচালিত গবর্মেন্ট নৈব্যক্তিক, হৃদয়হীন”। বক্তৃতার এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘Life creates, machine constructs’- জীবন সৃষ্টি করে যন্ত্র তৈরী করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যন্ত্র যখন মানুষকে সাহায্য করে তখনই সে সার্থক। তাঁর মতে অজ্ঞানকে দূর করার ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের অপবিত্র মিলনই পৃথিবীতে দুঃখ নিয়ে আসে।
কোয়েকার সম্মেলনের পরেরদিন রবীন্দ্রনাথ ম্যানচেস্টার কলেজের উপাসনালয়ে ‘Night and Morning’ শিরোনামে একটি ভাষণ দেন, যা পরে ‘Spectator’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে ছাপা হয়। ২৬ মে হিবার্ট বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতাটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য এলমহার্স্ট-এর বাড়িতে চলে আসেন এবং এখান থেকে তিনি ‘Religion of Man’ পত্রিকার জন্য একটি পত্র-প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধেও তিনি ভারতবাসীর বর্তমান দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘য়ুরোপ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সভ্যতা প্রদর্শনের জন্য এশিয়াতে যান নাই। অহমিকা ও ক্ষমতা প্রকাশের অসীম ক্ষেত্র অন্বেষণে গিয়াছিলেন। কিন্তু এশিয়া কখনোই ইহা স্বীকার করিবে না যে, মনুষ্যত্ববিহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরদিনের জন্য সাফল্য লাভ করিবে।’
এরপর ১৪ জুলাই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আমন্ত্রণে অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান। আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২, পৃঃ ৬৫-৬৬, অনুবাদ কানাই সামন্ত)—
গত বৎসরের (১৯৩০) গ্রীষ্মে আবার যখন জার্মানিতে যাই (১৯৩০-এ আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার দেখা হয়। প্রথমবার দুজনের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৬-এ), বার্লিনের অদূরে (কাপুথ) Kaputh- এ আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। ‘দুদিন’ আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, আর Religion of Man নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সুত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, ‘আমার বিশ্ব’ মানবিক ধ্যান ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এদিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতই মানবিক।
আইনস্টাইনের সঙ্গে যেদিন রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় সেই রাত্রেই ম্যুনিকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘The child’ ।
একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, হিবার্ট বক্তৃতার বিষয়বস্তু (‘The Religion of Man’), কোয়েকারদের বার্ষিক সম্মেলন, ‘Spectator’ পত্রিকার পত্র-প্রবন্ধ, আইনস্টাইনের সঙ্গে সংলাপ সবকিছুর মূলেই রয়েছে মানুষ সম্পর্কিত ভাবনার একটি যোগসূত্র। কখনো মানুষের স্বরূপ অনুসন্ধান, কখনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্পেষণে মনবতার অবমাননার কথা। হিবার্ট বক্তৃতামালায় উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের মানুষ সম্পর্কিত ভাবনার কথা। মানুষের স্বরূপ উন্মোচনই এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু। তিনি এখানে মানুষের মহত্বকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মনুষ্যত্ব কী, মানুষের ধর্ম কী— এই ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে, নানা উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, “যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।” তাঁর মতে,
ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তাঁর বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে। যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি।
মানুষের চলার ঐতিহাসিকতা বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে হয়েছে তা,‘ঐক্যের দিকে প্রসারিত।’ সত্যলাভ ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডীর মাঝে যে সম্ভব নয় সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন এই ভাবে,“যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।” তাঁর মতে, ‘ সে (মানুষ) শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম।’ ‘…বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা।’ ব্যক্তিগণ্ডি অতিক্রম করাই যে মানুষের মূল লক্ষ্য এবং মানুষের ধর্ম সে কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে মানুষ ‘চিরপথিক’। মানুষের চলা বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। এই চলা, “দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্যদিয়ে, তপস্যার মধ্যদিয়ে।” কিন্তু এই ‘চিরপথিক’-এর মাঝে, “ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।”
আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যখন সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর মন ‘The Religion of Man’’-এর ‘ভাবনায় ভরপুর’। আইনস্টাইন ধরেই নিয়েছিলেন রবীন্দ্রবিশ্ব ‘মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব।’ এই সংলাপে রবীন্দ্রনাথ খুব দৃঢ় ভাবেই বলতে পেরেছিলেন,‘এই বিশ্ব তো মানুষেরই পৃথিবী’। ‘মানব সম্পর্ক-নিরপেক্ষ’ কোন কিছুই নয়। সবকিছুই মানুষ দ্বারা উপলব্ধ ও প্রমাণিত, তা সে সত্যই হোক আর সুন্দরই হোক। আর এই মানুষ রবীন্দ্রচিন্তনজাত ‘চিরপথিক’ ‘বিশ্বমানব’। এই সংলাপের ছয় বছর পর, ১৯৩৬-এ, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ‘আমি’ কবিতাটি। সেখানেও উঠে এলো আইনস্টাইনকে বলা মানুষ সম্পর্কিত তাঁর ভাবনার বিষয়টি। কবিতার শুরুতেই লিখলেন—
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললুম ‘সুন্দর’
সুন্দর হল সে।
‘The child’ কবিতার মর্মবাণীর মাঝে গাঁথা রয়েছে মানুষ সম্পর্কিত রবীন্দ্রদর্শনের মূল সুর। যে দর্শন শুধু বেদ, উপনিষদ দিয়ে জারিত নয় বরং অনেকটাই বাংলার লোকদর্শনের সারবস্তুকে স্পর্শ করে গঠিত। বলা যায় বঙ্গ দর্শনের ভিত্তিভূমির উপর রবীন্দ্রনাথ মানুষ সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাকে নির্মাণ করেছেন।
‘The child’-এর অনুবাদ ‘শিশুতীর্থ’ পাঠে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতা বিকাশের ঐতিহাসিক রূপটি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি ‘মানুষের ধর্ম’ গ্রন্থে যে মানবজাতিকে ‘চিরপথিক’ রূপে আখ্যা দিয়েছেন সেই পথিকদের চলা ‘দুর্গমের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে’, অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে সেই ‘চিরপথিক’-এর কথাই উঠে এসেছে ‘শিশুতীর্থে’। এই কবিতার শুরুতেই আছে ‘রাত কত হল’ বলে এক আর্তনাদময় প্রশ্ন। রাত্রির ভয়াবহতার মাঝে একদল মানুষ যারা ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ নিজেদের মাঝে অবিশ্বাস, হানাহানি, মানবতার চরম অবমাননার এক ভয়ঙ্কর চিত্র। অন্ধকার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসারও শক্তি এইসব মানুষেরা অনুভব করে না। ‘মানবকে মহান বলে জেনো’— বলে কেউ যখন তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে মানবিকতার স্তরে উন্নীত করতে চায়, মানবিক মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা শোনে না এবং বোঝেও না, বলে, ‘পশুশক্তি আদ্যাশক্তি’, ‘পশুই শাশ্বত’। কিন্তু মানুষ চিরকাল পশুত্বের মাঝে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। তাকে তার মানবিক মর্যাদায় পৌঁছাতে হয়। এই পৌঁছানোর জন্যই তাকে ‘চিরপথিক’ হয়ে যাত্রা করতে হয় ‘সার্থকতার তীর্থে’। রবীন্দ্রনাথ ‘শিশুতীর্থে’ দিখিয়েছেন এই যাত্রায়—
যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
এই যাত্রায় আছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। যাদের মাঝে—
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
এই যাত্রীদলের মাঝে রয়েছে ‘নানা ধর্মের পূজারি’, রাজা, ‘ছিন্নকন্থা প’রে ভিক্ষু, ‘রাজ-অমাত্যের দল’, ‘জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপক’, তাকে ‘ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক’, মা, কুমারী, বধু, ‘বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে’—
চলেছে পঙ্গু খঞ্জ অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
বিভিন্ন শ্রেণির এই মানুষ বেরিয়ে পড়েছে মানবজাতির ‘সার্থকতার তীর্থে’ পৌঁছানোর জন্য। এই সার্থকতার তীর্থ মানব সভ্যতা বিকাশের চরম স্থান। যা ব্যষ্টি নয় সমষ্টির সংগ্রাম এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই অর্জন সম্ভব।
এই দীর্ঘ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘযাত্রার ইতিহাস আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। কবিতার শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় এই চলমান মানুষের স্রোত দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে যেখানে এসে পৌঁছালো সেখানে—
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
ঊষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে—
‘জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের!’
মানুষের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করাই মানবসভ্যতার চরম লক্ষ্য, যে লক্ষ্য অর্জিত হয় মানবজাতির সম্মিলিত চলার মধ্যদিয়েই। এখানে নবজাতকের উপস্থিতি এ কারণেই যে, নবজাতকই তো মানবসভ্যতার সমস্ত সম্ভাবনার আধার।
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মাঝে বিশ্বের প্রায় সব স্থানেই আজ মানবতা বিপর্যস্ত। ভোগবাদী সংস্কৃতির লোলুপতায় মানুষের মানবিক বোধ হারিয়ে যেতে বসেছে। ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত’ প্রতিটি মানুষ তার ঠিকানা থেকে, নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে ছিটকে যাচ্ছে। মানুষের চলার কোন সুমহান লক্ষ্য নেই। আর চলাবেন যিনি সেই মহৎপ্রাণ, মানবপ্রাণ নেতাও নেই। সমকালীন দেশীয় অথবা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনাকে কতটা আন্দোলিত করতে পারে সে বিষয়টি ভাবা নিশ্চয় জরুরি । ‘তোমার পূজার ছলে তোমায়’ যেন ভুলে না থাকি এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।
সহায়ক গ্রন্থ:
১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষোড়শ ও বিংশ খণ্ড।
২. রবীন্দ্রজীবনী— তৃতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩. শিশুতর্থি ঞযব পযরষফ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি।
৪. দিনযাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ, হায়াৎ মামুদ।
৫. বাংলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব— আহমদ শরীফ।
৬. রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী দৃষ্টিকোন থেকে— হায়দার আকবর খান রনো।
৭. আমার রবীন্দ্র অবলোকন— যতীন সরকার।
৮. সত্য যে কঠিন— যতীন সরকার।
১০. রবীন্দ্রনাট্যধারার প্রথমপর্যায়— ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য।
১১. রবীন্দ্রনাথ: অভিন্ন ভাবনার ভিন্ন উপস্থাপন— শাশ্বত ভটাচার্য

পেশায় শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে গবেষণা করে পি এইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। লেখেন প্রবন্ধ গল্প কবিতা। অনুবাদ করেছেন ভিয়েতনাম সহ বিভিন্ন দেশের কবিতা। সম্পাদনা করেন সাহিত্য ওয়েবজিন উত্তরকথা ডট কম এবং নিউজ পোর্টাল উত্তরবাংলা ডট কম। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাট্যধারার প্রথম পর্যায়, রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন ভাবনার ভিন্ন উপস্থাপন, সমাবিষ্ট স্বপ্নের সমুহ প্রপাত, কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের জীবনী।