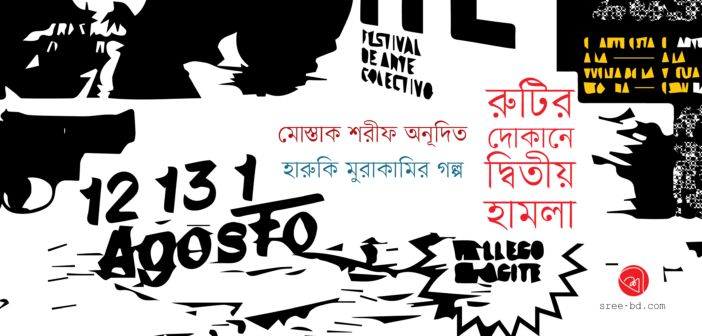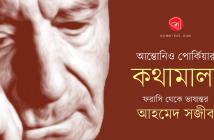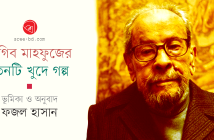আমি এখনও নিশ্চিত নই আমার বউকে রুটির দোকানে হানা দেওয়ার কথা বলাটা ঠিক হয়েছিল কিনা। অবশ্য ঠিক বেঠিকের প্রশ্ন নাও হতে পারে এটি। বলতে চাইছি, ভুল সিদ্ধান্ত কখনো কখনো সঠিক ফল দিতে পারে, আবার ঘটতে পারে উল্টোটাও। আমার নিজের বিশ্বাস, আমরা কোনোকিছু বেছে নিই না, ঘটনা এমনিই ঘটে যায়। অথবা ঘটে না।
ব্যাপারটাকে যদি এভাবে চিন্তা করেন তাহলে রুটির দোকানে আক্রমণের কথা আমার বউকে বলাটা স্রেফ ঘটে গেছে। নিজে ওটার কথা তুলিনি, বস্তুত বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। যদিও ‘তুমি যেহেতু কথাটা তুললেই’ ধরনের ব্যাপারও ছিল না এটা। রুটির দোকানে হানা দেওয়ার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিল অসহ্য এক ক্ষুধা। আঘাত হানল রাত দুটোয়। রাতের খাবার সেরেছি ছটার দিকে, হালকা কিছু দিয়ে। বিছানায় গিয়েছি সাড়ে নটায় এবং ঘুমিয়ে পড়েছি। কে জানে কেন, ঠিক একই সময় জেগে উঠলাম দুজন। খানিক পরই ‘ওজের জাদুকর’ বইয়ের সেই টর্নেডোর মতোই হামলে পড়ল সে ভয়ংকর, শক্তিশালী এক ক্ষুধার ছোবল।
ফ্রিজে একটাও জিনিস ছিল না প্রকৃতপ্রস্তাবে যাকে খাদ্য বলা যায়। ফরাসি সসের একটা বোতল, ছয় ক্যান বিয়ার, চিমসে হয়ে যাওয়া এক জোড়া পেঁয়াজ, খানিকটা মাখন আর একবাক্স দুর্গন্ধনাশক। দুজনের বিয়ের বয়স মাত্র দু হপ্তা, খাবার দাবারের ব্যাপারে দাম্পত্য বোঝাপড়া তৈরির জন্য সময়টা যথেষ্ট নয়, অন্য কিছুর কথা বাদই দিলাম। একটা আইনী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম তখন, বউ কাজ করত ডিজাইন শেখানোর স্কুলে। আমার বয়স তখন আটাশ কি উনত্রিশ-বিয়েটা কোন বছর হয়েছিল কেন যে ছাই মনে পড়ছে না! বউ ছিল আমার দু বছর আট মাসের ছোটো। মুদিমাল বা আনাজপাতি নিয়ে ভাবনার ফুরসতই ছিল না।
পেটে এত ক্ষুধা নিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়াটা সহজ ছিল না, সম্ভব ছিল না শুয়ে থাকাও। ক্ষুধার জ্বালায় কাজের কাজ কিছু যে করব সে উপায়ও ছিল না। বিছানা ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম, টেবিলের দুপাশে বসলাম দুজন। পেটটা কেন খাই খাই করছে এমন? মনে আশা নিয়ে পালা করে ফ্রিজের দরজা খুলতে লাগলাম দুজন, তবে যতবারই খুলি ভেতরের জিনিস সেই একই থাকল। বিয়ার, পেঁয়াজ, মাখন, সস আর দুর্গন্ধনাশক। মাখনে পেঁয়াজ ভেজে খাওয়া যেত। তবে শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাওয়া দুটো পেঁয়াজে দুজনের খালি পেট ভরার সম্ভাবনা নেই। পেঁয়াজ অন্য কিছুর সঙ্গে খাওয়ার জিনিস, ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়।
‘ম্যাডাম কি দুর্গন্ধনাশকে ভাজা খানিকটা ফ্রেঞ্চ সস খাবেন?’ জানতাম আমার রসিকতার চেষ্টাকে আমলে নেবে না সে, ঘটলও তাই। ‘সারা রাত খোলা থাকে এমন রেস্তোরাঁর খোঁজে যাই চলো,’ বললাম আমি। ‘বড়ো রাস্তায় ওরকম একটা না একটা থাকবেই।’
প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল সে। ‘সম্ভব না। মাঝরাতের পর খাওয়ার জন্য বাইরে যাওয়ার দস্তুর নেই।’ এসব ব্যাপারে সে মোটামুটি সেকেলে।
ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বললাম, ‘আসলেই নেই।’
সে সময় বউ যখনই এরকম কোনো মত (বা তত্ত্ব) প্রকাশ করত, দৈববাণীর মতোই আমার কানে প্রতিধ্বনি তুলত সেটি। কে জানে হয়তো সব নববিবাহিতের ক্ষেত্রেই এটি ঘটে। তবে তার মুখ থেকে কথাটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হতে লাগল, হয়তো বিশেষ কোনো ক্ষুধা এটি, এমন কিছু, বড়ো রাস্তায় সারা রাত খোলা থাকে এমন রেস্তোরাঁয় গিয়ে যেটা মেটানো সম্ভব নয়।
বিশেষ এক ধরনের ক্ষুধা। কী হতে পারে সেটা?
সিনেমার কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করতে পারি এখানে।
এক, ছোট্ট একটা নৌকায় আছি আমি, ভাসছি শান্ত সাগরে। দুই, নিচের দিকে তাকালাম, দেখলাম সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরের দিকে ছুটে আসছে আগ্নেয়গিরির একটি চূড়া। তিন, চূড়াটি পানির পৃষ্ঠদেশের খুব কাছে চলে এসেছে, কত কাছে বলতে পারছি না। চার, কারণ হচ্ছে, পানির অতিমাত্রায় স্বচ্ছতার কারণে দূরত্বের আন্দাজটি ঠিকমতো করা যাচ্ছে না।
সারারাত খোলা থাকে এমন রেস্তোরাঁয় যেতে আমার স্ত্রীর অস্বীকৃতি জানানো আর ‘আসলেই তাই’ বলে আমার সম্মতি জানানোর ঘটনাটি ঘটতে যে দু থেকে তিন সেকেন্ড লাগল। সে সময় আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠা দৃশ্যগুলোর মোটামুটি নিখুঁত বর্ণনা বলা যায় এটিকে। যেহেতু সিগমুন্ড ফ্রয়েড নই সেহেতু দৃশ্যগুলোর মাজেজা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব না। এ কারণেই-ক্ষুধার বিকট তীব্রতা সত্ত্বেও বউয়ের ইচ্ছার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একমত হলাম।
সিনাই উপদ্বীপের মতো আমাদের বিশাল আর অন্তহীন ক্ষুধার মধ্যে বিস্কুট আর বিয়ার কোনো চিহ্ন না রেখেই গায়েব হয়ে গেল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছিল সময়, মাছের পেটের মধ্যে জমা ভারি সীসার মতো।
একমাত্র যে কাজটি করা সম্ভব ছিল তাই করলাম, বিয়ারের ক্যান খুললাম। পেঁয়াজগুলো খাওয়ার চেয়ে ঢের ভালো ওটা। বিয়ার খুব একটা পছন্দ না বউয়ের, ভাগাভাগি করে নিলাম এজন্য— ও দুটো, আমি চারটা। প্রথম বিয়ারটি যখন গলায় ঢালছিলাম, নভেম্বর মাসে কাঠবিড়ালীরা যেমন করে, সেভাবে রান্নাঘরের তাকগুলোতে অনুসন্ধান চালাল সে। একটা প্যাকেট পেল শেষমেষ যার তলার দিকে চারটা মাখন-বিস্কুট ছিল। আগে কখনো খাওয়ার সময় উচ্ছিষ্ট থেকে গিয়েছিল হয়তো, নরম আর নেতানো। ওগুলোই খেলাম তারিয়ে তারিয়ে, দুজন দুটো করে। লাভ হলো না অবশ্য। সিনাই উপদ্বীপের মতো আমাদের বিশাল আর অন্তহীন ক্ষুধার মধ্যে বিস্কুট আর বিয়ার কোনো চিহ্ন না রেখেই গায়েব হয়ে গেল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছিল সময়, মাছের পেটের মধ্যে জমা ভারি সীসার মতো। বিয়ারের অ্যালুমিনিয়ামের ক্যানের লেখাগুলো পড়লাম। তাকালাম ঘড়ির দিকে। ফের ঢুঁ মারলাম ফ্রিজে। কালকের পত্রিকার পাতাগুলো ওল্টালাম। একটা পোস্টকার্ডের কানা দিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োগুলো ছেঁচে তুললাম টেবিল থেকে।
‘জীবনে কখনও এত ক্ষুধা লাগেনি,’ বউ বলল। ‘বুঝতে পারছি না বিয়ে হওয়ার সাথে সম্পর্ক আছে কি না এটার।’
‘হতে পারে,’ আমি বললাম, ‘আবার নাও হতে পারে।’
খাবারের টুকরোটাকরার খোঁজে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল সে, আমি সেই নৌকাটির কানায় গিয়ে উঁকি মারলাম ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির চূড়ার দিকে। নৌকার চারপাশে সমুদ্রের পানির স্বচ্ছতা অস্থিরতা জাগাল মনে, যেন আমার পেটের ঠিক মধ্যিখানে মুখ ব্যাদান করা ফাঁপা একটা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে, বায়ুশূন্য একটা গহ্বর, যাতে ঢোকা ও বেরোনোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এই না থাকাটা বিদঘুটে একটা অনুপস্থিতির বোধ তৈরি করল মনে। খুব উঁচু আর সরু কিছু বেয়ে চূড়ায় ওঠার সময় শরীর অবশ করা যে ভয়টা হানা দেয় তার সঙ্গে মিল আছে অনস্তিত্বের অস্তিত্বসম্পর্কিত বাস্তবতার এ উপলব্ধিটির। ক্ষুধা আর উচ্চতাভীতির মধ্যে এ সম্পর্কটাও নতুন এক আবিষ্কার আমার জন্য। তখনই মনে পড়ল, এর আগেও একবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। পেটটাকে একইরকম ফাঁকা মনে হয়েছিল তখনও…কখন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ওটা ছিল–
‘রুটির দোকানে হানা দেবার সময়,’ নিজেকে বলতে শুনলাম।
‘রুটির দোকানে হানা? কী বলছ এসব?’
কাজেই গল্প শুরু হলো।
‘একবার একটা রুটির দোকানে হামলা করেছিলাম। বহুদিন আগের কথা। খুব বড়ো দোকান ছিল না, বিখ্যাতও নয়। তাদের রুটি যে বিশেষ কিছু তাও না। অবশ্য খারাপও বলা যাবে না। গাদাগাদি করা অনেকগুলো দোকানের মধ্যে সেঁদিয়ে থাকা একটা পাড়ার দোকান। বুড়ো একটা লোক চালাত ওটা, সব কাজই একাই করত। সকালে রুটি সেঁকত, রুটি শেষ হয়ে গেলে সেদিনের মতো ঝাঁপ ফেলে দিত।
‘হানা যদি দিতেই হয় ওটাতে কেন?’
‘বড়ো দোকানে আক্রমণ করে ফায়দা নেই। টাকাপয়সা না, রুটিই চেয়েছিলাম আমরা। হামলাকারী ছিলাম, ডাকাত না।’
‘আমরা? আমরাটা কে?’
‘আমি আর আমার জিগরি এক দোস্ত। বছর দশেক আগের কথা। পকেট এমনই গড়ের মাঠ যে টুথপেস্ট কেনার পয়সাও ছিল না। খেতে পেতাম না ঠিকমতো। খাবারের জন্য আজেবাজে কয়েকটা কাজও করতে হয়েছিল। রুটির দোকানে আক্রমণ তার মধ্যে একটা।’
‘বুঝতে পারছি না,’ খর চোখে আমার দিকে তাকাল বউ। মনে হচ্ছিল ভোরের আকাশে টিমটিম করে জ্বলা কোনো তারা খুঁজছে। ‘কাজ জুটিয়ে নাওনি কেন একটা? ক্লাস শেষে কাজ করতে পারতে। রুটির দোকানে হামলা করার চেয়ে ঢের সহজ ছিল ওটা।’
‘কাজ করার ইচ্ছে ছিল না। দুজনেই একমত ছিলাম এ ব্যাপারে।’
‘এখন তো কাজ করছ, নাকি?’
মাথা ঝাঁকিয়ে বিয়ার গিললাম আরেকটু। চোখ ডললাম। বিয়ারে চুপচুপে এক ধরনের কাদা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে ক্ষুধার যন্ত্রণার সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করছে।
‘সময় পাল্টায়। মানুষও,’ আমি বললাম। ‘চলো বিছানায় যাই, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে কাল।’
‘ঘুম আসছে না আমার। রুটির দোকানে হামলার ঘটনাটা শুনতে চাই।’
‘বলার মতো কিছু নেই আসলে। ঘটনার ঘনঘটা নেই, উত্তেজনা নেই।’
‘সফল হয়েছিলে কাজটায়?’
ঘুমের চিন্তা বাদ দিয়ে বিয়ারের ক্যান খুললাম আরেকটা। একবার কোনো গল্পের ব্যাপারে আগ্রহ জাগলে পুরোটা শোনা চাই-ই তার। ধাতটাই এরকম। ‘বলতে পারো খানিকটা সফল হয়েছিলাম, আবার হইওনি। যা চেয়েছি তা পেয়েছি, তবে ওটাকে যদি ডাকাতি বল তাহলে সফল হইনি। কেড়ে নেওয়ার আগে আপসেই রুটি দিয়ে দিয়েছিল দোকানি।’
‘বিনে পয়সায়?’
‘ঠিক তাও না। গেরোটা ওখানেই,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। ‘দোকানি ছিল ধ্রুপদী গানের পাগল। আমরা যখন গেলাম, ভাগনারের ওভারচারের একটা অ্যালবাম শুনছিল। আমাদের সঙ্গে একটা রফায় আসে সে। যদি আমরা রেকর্ডটা আগাগোড়া শুনি তাহলে যত খুশি রুটি নিতে পারব। পরামর্শ করলাম দুজনে। মনে হলো, এটাকে হয়তো কাজ বলা যায় না, তবে ক্ষতিওতো নেই কোনো। কাজেই ছুরিগুলো থলেতে ভরলাম, দুটো চেয়ার টেনে বসে টানহয়জার আর ফ্লায়িং ডাচম্যান ওভারচার শুনলাম।’
‘এবং বিনিময়ে পেলে রুটি?’
‘হুম। দোকানে যা ছিল প্রায় সবটাই। থলেতে ভরে বাড়ি নিয়ে এলাম। চার থেকে পাঁচদিন চলেছিল আমাদের।’ আরেকটা চুমুক দিলাম বিয়ারে। সমুদ্রতলে ভূমিকম্পের শব্দহীন তরঙ্গের মতো ঘুম ঘুম ভাব আমার নৌকাটাকে ধীরে, লম্বা একটা ঝাঁকুনি দিল।
‘উদ্দেশ্য ভালোভাবেই হাসিল হয়েছিল। রুটি চেয়েছিলাম, পেয়েছি। কেউ বলতেও পারবে না কোনো অপরাধ করেছি। ব্যাপারটাকে বিনিময় বলা যায়। লোকটার সঙ্গে বসে ভাগনারের বাজনা শুনেছি, বিনিময়ে রুটি দিয়েছে সে। আইনের ভাষায় বলতে গেলে একটা বাণিজ্যিক লেনদেন।’
‘কিন্তু ভাগনারের বাজনা শোনাকে কাজ বলা যাবে না,’ সে বলল।
‘অবশ্যই না। দোকানি যদি বলত বাসন মাজতে বা জানালা পরিষ্কার করতে হবে, মানতাম না আমরা। ওটা বলেনি সে। স্রেফ ভাগনারের একটা রেকর্ড শুরু থেকে শেষ অব্দি শোনাতে চেয়েছিল। কার মাথায় আসবে এরকম একটা কথা? ভাবো একবার– ভাগনার! যেন একটা অভিশাপ ছুঁড়ে দিয়েছে লোকটা আমাদের দিকে। এখন অবশ্য মনে হয়, প্রস্তাবটা মানা উচিত হয়নি। ছুরি উঁচিয়ে হুমকি দেওয়া দরকার ছিল লোকটাকে, কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল রুটিগুলো। তাহলেই সমস্যা হতো না কোনো।’
‘সমস্যা হয়েছিল?’
ফের চোখ ডললাম। ‘বলা যায়। তবে সমস্যাটা কী জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। যেটা ঘটেছিল তা হলো, এরপর থেকে বদলে যেতে শুরু করল সব। একটা সন্ধিক্ষণ বলতে পারো ঘটনাটাকে। যেমন ধরো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় ফিরে গেলাম, স্নাতক শেষ করলাম, একটা কোম্পানিতে কাজ নিলাম, ওকালতি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলো, বিয়ে করলাম। ওরকম আর কিছু কখনও ঘটাইনি। রুটির দোকানে আর কোনো হামলা নয়।’
‘এই-ইতো সব?’
‘হ্যাঁ, এ-ই।’
শেষ বিয়ারটাও পেটে চালান দিলাম। ছ’টা বিয়ারের সব ক’টা শেষ। বিয়ারের ক্যানের ছ’টা ঢাকনা ছাইদানিতে পড়ে আছে মৎস্যকন্যার শরীর থেকে ছাড়ানো আঁশের মতো। রুটির দোকানে হানা দেওয়ার কারণে কিছু ঘটেনি এটা ঠিক নয়। নির্দিষ্ট করে বলা যাবে এমন অনেক কিছু আছে, কিন্তু বউয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না।
‘তোমার ঐ বন্ধু, কী করছে সে এখন?’
‘জানি না। কিছু একটা ঘটেছিল দুজনের মধ্যে, তুচ্ছ কিছু একটা, যে কারণে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। জানি না কী করছে এখন।’
খানিকক্ষণ চুপ মেরে রইল বউ। হয়তো বুঝতে পারছিল গোটা কাহিনিটা তাকে বলিনি। তবে চাপাচাপি করার জন্য সম্ভবত তখনও প্রস্তুত ছিল না। ‘তবু,’ সে বলল, ‘ঐ ঘটনার কারণেই তোমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই না? রুটির দোকানে হানা দেওয়ার কারণেই।’
রুটির সঙ্গে ভাগনারের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে পরের কয়েকটা দিন অনেক কথা বলেছি দুজন। কাজটি কি ঠিক করেছিলাম, বারবার জিজ্ঞেস করেছি নিজেদের। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি কোনো। যদি যৌক্তিকভাবে চিন্তা করো, সিদ্ধান্তটা অবশ্যই ঠিক ছিল। কারো ক্ষতি হয়নি। সবাই তা পেয়েছিল যে যা চেয়েছিল। দোকানির কথা যদি বলো, কেন সে ওরকম করেছিল আজও ভেবে পাই না।
‘হতে পারে। হয়তো আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে গভীর ছিল ব্যাপারটি। রুটির সঙ্গে ভাগনারের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে পরের কয়েকটা দিন অনেক কথা বলেছি দুজন। কাজটি কি ঠিক করেছিলাম, বারবার জিজ্ঞেস করেছি নিজেদের। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি কোনো। যদি যৌক্তিকভাবে চিন্তা করো, সিদ্ধান্তটা অবশ্যই ঠিক ছিল। কারো ক্ষতি হয়নি। সবাই তা পেয়েছিল যে যা চেয়েছিল। দোকানির কথা যদি বলো, কেন সে ওরকম করেছিল আজও ভেবে পাই না। ঘটনা যাই হোক, ভাগনারের প্রচারণায় সে সফল, আর আমরা সফল গণ্ডেপিণ্ডে রুটি গেলায়। তারপরও, কেন যেন মনে হয়েছিল বড়ো একটা ভুল করেছি। এই মনে হওয়াটা রয়েই গিয়েছিল, মীমাংসা হয়নি কোনো। একটা কালো ছায়া ফেলেছিল ওটা আমাদের জীবনে। এ কারণেই ‘অভিশাপ’ শব্দটা ব্যবহার করেছি। সত্যিই তাই, অভিশাপের মতোই ছিল ওটা।’
‘তোমার কি মনে হয় অভিশাপটা এখনও আছে তোমার সঙ্গে?’
ছাইদানি থেকে ক্যানের ছ’টা ঢাকনা তুলে নিলাম, সেগুলো দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বৃত্ত বানালাম টেবিলে, আকার হলো অনেকটা চুড়ির মতো।
‘কে জানে! বলতে পারি না। দুনিয়াটাই অভিশাপে ভরা। কোন অভিশাপ যে কোন কাজে ভজঘট পাকিয়ে দেয় কে জানে!’
‘কথাটা ঠিক না।’ আমার চোখাচোখি তাকাল সে। ‘ঠান্ডা মাথায় ভাবলে ঠিকই বলতে পারবে। নিজে যদি অভিশাপটা না ভাঙো দাঁতের ব্যথার মতো লেগে থাকবে পেছনে। মরার আগ পর্যন্ত জ্বালাবে। কেবল তোমাকেই নয়, আমাকেও।’
‘তোমাকেও?’
‘হুম। এখন কে তোমার সেরা বন্ধু, আমি না? তোমার কী মনে হয়, দুজনেই এত ক্ষুধার্ত কেন আমরা? তোমাকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এমন ভয়ংকর ক্ষুধা জীবনে লাগেনি। অস্বাভাবিক মনে হয় না এটা তোমার কাছে? তোমার অভিশাপটা আমার ওপরও কাজ করছে।’
মাথা নাড়লাম আমি। বিয়ারের ঢাকনার আংটিটা ভেঙে দিয়ে ফের ছাইদানিতে চালান দিলাম ওগুলোকে। তার কথা ঠিক কিনা জানি না, তবে কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে, টের পেলাম।
উপোসের অনুভূতিটা আগের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ফিরে এসেছে, তীব্র একটা মাথাব্যথা অনুভব করছি ওটার কারণে। পাকস্থলীর প্রতিটি মোচড়ানি ইস্পাতের একটা তার বেয়ে চলে যাচ্ছে মগজের মাঝখানে, যেন শরীরের ভেতরকার সবকিছুর সঙ্গে জটিল সব কলকব্জা এঁটে দেওয়া হয়েছে।
সমুদ্রতলদেশের আগ্নেয়গিরিটির দিকে তাকালাম আরেক ঝলক। পানি আগের চেয়েও স্বচ্ছ, বড্ড বেশি স্বচ্ছ। বস্তুত ভালোমতো না তাকালে পানি যে আছে সেটাই ঠাহর করা কঠিন। মনে হলো শূন্যে ভাসছে নৌকাটা, কোনোকিছুর সাহায্য ছাড়াই। সমুদ্রতলের প্রতিটি নুড়ি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার কেবল বাকি।
‘মাত্র দু হপ্তা হলো একসঙ্গে আছি দুজন,’ সে বলল, ‘গোটা সময়টায় অদ্ভুত কিছু একটার উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমি।’ আমার চোখে চোখ রেখে হাতদুটো টেবিলের ওপর রাখল, দু হাতের আঙুল আঁকড়ে আছে পরস্পরকে। ‘এটা যে অভিশাপ খানিক আগেও বোঝার উপায় ছিল না। এখন বুঝতে পারছি। অভিশাপের খাঁড়া ঝুলছে তোমার ওপর।’
‘কিসের উপস্থিতির কথা বলছ?’
‘ভারি, ধুলোভরা পর্দার মতো কিছু একটা। বহুদিন ধোয়া হয়নি, ঝুলে আছে ছাদ থেকে।’
‘হয়তো অভিশাপ-টভিশাপ নয়। স্রেফ আমিই,’ বলে হাসলাম।
সে হাসল না। ‘উঁহু, তুমি না।’
‘ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমিই ঠিক। এটা একটা অভিশাপ। কী করা উচিত তাহলে আমার?’
‘আরেকটা রুটির দোকানে হানা দেবে। এখনই। এটাই একমাত্র উপায়।’
‘এখন?’
‘হ্যাঁ, এখন। যতক্ষণ ক্ষুধাটা পেটে আছে। যে কাজটা শেষ করতে পারনি সেটা শেষ করবে।’
‘কিন্তু এখন মাঝরাত। দোকানপাট খোলা আছে?’
‘খুঁজে বের করব একটা। টোকিও অনেক বড়ো শহর। সারারাত খোলা থাকা রুটির দোকান একটা হলেও আছে কোথাও না কোথাও।’
আমার পুরনো করোলাটায় চেপে রুটির দোকানের খোঁজে টোকিওর রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলাম রাত আড়াইটায়। আমার হাত স্টিয়ারিং হুইলে, বউ নাবিকের আসনে, ক্ষুধার্ত ঈগল যেভাবে শিকার খোঁজে সেভাবে রাস্তা জরিপ করছি দুজন। একটা রেমিংটন অটোমেটিক শটগান পড়ে আছে পেছনের আসনে, মরা মাছের মতো লম্বা আর শক্ত। বউয়ের গলাবন্ধ জ্যাকেটের পকেট থেকে ভেসে আসছে শটগানের কার্তুজের ঝুনঝুন শব্দ। কালো রঙের দুটো স্কি খেলোয়াড়ের মুখোশ আছে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে। বউ কী কারণে শটগান রাখে জানা নেই আমার। মুখোশগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। কখনও স্কি খেলিনি দুজনের কেউই। এগুলো রাখার কারণ সে ব্যাখ্যা করেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। বিবাহিত জীবন বড়ো অদ্ভুত, মনে হলো আমার।
কালো রঙের দুটো স্কি খেলোয়াড়ের মুখোশ আছে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে। বউ কী কারণে শটগান রাখে জানা নেই আমার। মুখোশগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। কখনও স্কি খেলিনি দুজনের কেউই। এগুলো রাখার কারণ সে ব্যাখ্যা করেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। বিবাহিত জীবন বড়ো অদ্ভুত, মনে হলো আমার।
অস্ত্রশস্ত্রে যতই সজ্জিত হই, সারারাত খোলা থাকে এমন একটা রুটির দোকানও পেলাম না। ইয়োইয়োগি থেকে শিনজুকু, সেখান থেকে ইয়োতসুভা ও আকাসাকা, আয়োয়ামা, হিরু, রপোঙ্গি, দাইকানিয়ামা, শিবুইয়া— একের পর এক ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। গভীর রাতের টোকিও ভর্তি হরেক রকমের মানুষ আর দোকান, যার একটাও রুটির দোকান নয়।
পুলিশের টহলগাড়ির সামনে পড়লাম দু’বার। রাস্তার পাশে ঘাপটি মেরে ছিল একটা, সহজে যাতে চোখে না পড়ে। অন্যটা ধীরে পাশ কাটাল আমাদের, তারপর আস্তে হারিয়ে গেল দূরে। দু’বারই ঘামে বগল ভিজল আমার, কিন্তু আমার বউয়ের মনোযোগ একবিন্দুও টলল না। শ্যেনচোখে রুটির দোকান খুঁজছে সে। যতবারই বসার ভঙ্গি বদলাল, পকেটের মধ্যে শটগানের কার্তুজগুলো সেকেলে ঢঙে বানানো বালিশের মধ্যে ভরা বাজরার খোসার মতো মটমট করতে লাগল।
‘বাদ দাও,’ আমি বললাম। ‘এত রাতে কোনো রুটির দোকান খোলা থাকে না। আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতে হয় এসব ব্যাপারে, নইলে—’
‘গাড়ি থামাও!’
ব্রেক দাবালাম আমি।
‘এই যে, এখানে,’ সে বলল।
রাস্তার পাশে সব দোকানের শাটার নামানো, ফলে অন্ধকার, নিঃশব্দ দেয়াল তৈরি হয়েছে দু’পাশে। একটা নাপিতের দোকানের সাইনবোর্ডকে ঝুলতে দেখলাম বিকৃত, বুকে ভয় ধরালো কাচের চোখের মতো। দুশো গজ দূরে একটা ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গারের সাইনবোর্ড, আর কিছু নেই।
‘রুটির দোকানতো দেখতে পাচ্ছি না,’ বললাম আমি।
কোনো কথা না বলে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে আঠাযুক্ত টেপের একটা বান্ডিল বের করল সে। ওটা হাতে নিয়ে নামল গাড়ি থেকে। আমিও নামলাম। গাড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে খানিকটা টেপ ছিঁড়ল, ঢেকে দিল গাড়ির লাইসেন্স প্লেট। একই কাজ করল গাড়ির পেছনে গিয়েও। নড়াচড়ায় দক্ষতার ছাপ, যেন আগেও করেছে এসব। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।
‘ম্যাকডোনাল্ডে হানা দেব আমরা,’ এমন ঠান্ডাগলায় কথাটা বলল যেন রাতে কী খাব সেটা জানাচ্ছে।
‘ম্যাকডোনাল্ড রুটির দোকান না,’ আমি বললাম।
‘রুটির দোকানের মতো,’ সে বলল। ‘মাঝেমাঝে একটু এদিক সেদিক করতে হয়। চলো।’
ম্যাকডোনাল্ডের কাছে গিয়ে পার্কিং লটে দাঁড় করালাম গাড়ি। কম্বলে মোড়ানো শটগানটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে।
‘জীবনে গুলি ছুঁড়িনি আমি,’ বললাম।
‘গুলি ছুঁড়তে হবে না। স্রেফ ধরে রাখ, ঠিক আছে? আমি যেভাবে বলব সেভাবে করবে। হেঁটে ভেতরে ঢুকব, যেই ওরা বলবে, ম্যাকডোনাল্ডে স্বাগতম, মুখে মুখোশ এঁটে নেবে। বুঝেছ?’
‘হ্যাঁ, কিন্তু…’
‘তারপর বন্দুকটা ওদের মুখের ওপর ধরবে, দোকানের কর্মচারি আর ক্রেতাদের একসঙ্গে জড়ো করবে। দ্রুত। বাকিটা আমি করব।’
‘কিন্তু…’
‘ক’টা হ্যামবার্গার লাগতে পারে আমাদের? ত্রিশটা?’
‘হয়তো।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে শটগানটা হাতে নিলাম, কম্বল সরিয়ে মাথাটা বের করলাম ওটার। বালুভর্তি থলের মতো ভারি জিনিসটা, নিশুতি রাতের মতো কালো।
‘কাজটা কি করতেই হবে?’ জিজ্ঞেস করলাম, কিছুটা বউয়ের উদ্দেশে বাকিটা নিজের উদ্দেশে।
‘অবশ্যই।’
কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটা ম্যাকডোনাল্ডের টুপি পরে ম্যাকডোনাল্ড মার্কা একটা হাসি ছুঁড়ল আমার দিকে। ‘ম্যাকডোনাল্ডে স্বাগতম।’
রাতের বেলা মেয়েরা ম্যাকডোনাল্ডে কাজ করে ধারণায় ছিল না, ফলে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে মুখোশ পরে নিলাম। আচমকা দুই মুখোশধারীকে দেখে হা করে তাকিয়ে রইল মেয়েটা।
বোঝাই যাচ্ছে, ম্যাকডোনাল্ডের আতিথেয়তা বিষয়ক পুস্তিকায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা বলা হয়নি। ‘ম্যাকডোনাল্ডে স্বাগতম’-এর পরের বাক্যটি তৈরি করতে শুরু করেছিল সে, কিন্তু মুখটা শক্ত হয়ে গেল, কথা বের হচ্ছে না আর মুখ দিয়ে। তারপরও, ভোরের আকাশে এক চিলতে চাঁদের মতো পেশাদার একটুখানি হাসি ঠোঁটের কোনায় লটকে রইল তার। যত দ্রুত পারি কম্বলের আবরণ সরিয়ে বের করলাম শটগানটা, তাক করলাম টেবিলসারির দিকে, কিন্তু দোকানের একমাত্র ক্রেতা এক তরুণ আর তরুণী, সম্ভবত ছাত্র, দুজনেই টেবিলে মুখ গুঁজে ঘুমে কাঁদা হয়ে আছে। তাদের মাথা এবং স্ট্রবেরি মিল্কশেকের দুটো কাপ নিরীক্ষামূলক ভাস্কর্যের মতো সাজানো আছে টেবিলে। মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে দুজন, মনে হয় না আমাদের অভিযানে বাধা দেওয়ার মতো অবস্থায় আছে, কাজেই ফের কাউন্টারের দিকে ঘোরালাম শটগান।
দোকানে কর্মচারি সাকুল্যে তিনজন। কাউন্টারের মেয়েটা, ফ্যাকাসে, ডিম আকৃতির মুখাবয়ব আর ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের ম্যানেজার, আর রান্নাঘরে ছাত্রগোছের চেহারার আরেকজন। তালপাতার সেপাইর মতো হালকাপাতলা, পুরোপুরি অভিব্যক্তিশূন্য চেহারা। এ মুহূর্তে ক্যাশ রেজিস্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, তাকিয়ে আছে শটগানের নলের দিকে, ইনকা দেয়ালের দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে পর্যটকেরা। চেঁচাল না কেউ, আক্রমণাত্মক কোনো ভঙ্গিও করল না। বন্দুকটা এত ভারি যে ক্যাশ রেজিস্টারের ওপর রাখতে হলো সেটার নল, আঙ্গুল পেঁচিয়ে রেখেছি ট্রিগার।
‘টাকা দিয়ে দেব,’ ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল ম্যানেজার। ‘এগারোটায় চালান নিয়ে গেছে, টাকা খুব একটা নেই, চাইলে দিয়ে দেব সব। বীমা করা আছে আমাদের।’
‘সামনের শাটার বন্ধ করো, সাইনবাতি নেভাও,’ আমার বউ বলল।
‘দাঁড়াও দাঁড়াও,’ ম্যানেজার বলল, ‘এটা করতে পারব না, অনুমতি ছাড়া বন্ধ করলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপবে।’
হুকুমটা ফের করল বউ, এবার ধীরে ধীরে। লোকটাকে দেখে মনে হলো দ্বিধায় ভুগছে।
‘ও যা বলছে করো,’ সতর্ক করে বললাম।
কাউন্টারে রাখা বন্দুকের নলের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর আমার বউয়ের দিকে এবং আবার বন্দুকের দিকে। অবশেষে ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করল।
কাউন্টারে রাখা বন্দুকের নলের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর আমার বউয়ের দিকে এবং আবার বন্দুকের দিকে। অবশেষে ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করল। সাইনবাতি নেভাল, বৈদ্যুতিক বোর্ডে একটা সুইচ বন্ধ করল এবং শাটার নামাল। চোখ সরালাম না ওর ওপর থেকে। ভয় পাচ্ছিলাম কোথাও চোরঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডে সে জিনিস নেই বলেই মনে হলো। হতে পারে কখনো ম্যাকডোনাল্ডে হানা দেওয়ার কথা ভাবেনি কেউ। সামনের শাটারটা বন্ধ করার সময় পিলে চমকানো শব্দ হলো, যেন খালি বালতিকে বেসবল ব্যাট দিয়ে পেটাচ্ছে কেউ। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমানো যুগলের হেলদোল নেই তবু। গভীর ঘুম আর কাকে বলে! এমন কিছু দেখিনি আগে কখনো।
‘ত্রিশটা বিগ ম্যাক, বাড়ি নেওয়ার জন্য,’ আমার বউ বলল।
‘বরং টাকাটাই দিয়ে দিই,’ অনুনয়ের সুর ম্যানেজারের গলায়। ‘যা দরকার তার চেয়ে বেশিই পাবে। অন্য কোথাও গিয়ে খাবার কিনতে পারবে। আমার হিসাবের বারোটা বেজে যাবে, তাছাড়া—’
‘ও যা বলছে সেটা করো,’ ফের বললাম আমি।
একসঙ্গে রান্নাঘরে গেল তিনজন, ত্রিশটা বিগ ম্যাক বানাতে শুরু করল। ছাত্রগোছের ছেলেটা বার্গার বানাল, ম্যানেজার সেগুলোকে বনরুটিতে ঢোকাল আর মেয়েটা মোড়কে ঢোকাল। টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করল না কেউ। বড়ো একটা রেফ্রিজারেটরে হেলান দিলাম আমি, তাওয়ার দিকে তাক করলাম শটগানটা। মাংসের চপগুলো তাওয়ার ওপর সার দেওয়া আছে গোল গোল বাদামি নকশার মতো, ভাজা চলছে। মাংস ভাজার মনকাড়া গন্ধ ছোটো ছোটো পোকার মতো শরীরের রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করছে, মিশে যাচ্ছে রক্তের সঙ্গে, চলে যাচ্ছে শরীরের প্রতিটি প্রান্তে, তারপর গিয়ে জড়ো হচ্ছে ক্ষুধাভর্তি বায়ুশূন্য গূহাটাতে, লটকে থাকছে তার গোলাপি দেয়ালে।
সাদা কাগজে মোড়া বার্গারের একটা স্তূপ জমা হচ্ছিল অদূরে। ইচ্ছে হচ্ছিল ধরে ধরে মুখে পুরি, তবে আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কাজেই অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রান্নাঘরের পাশে ভীষণ গরম, স্কি মুখোশের নিচে ঘামতে শুরু করলাম আমি।
ম্যাকডোনাল্ডের লোকগুলো আমার শটগানের নলের দিকে চোরাচোখে চাইছিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে কান চুলকালাম, স্নায়ুচাপে ভুগলে কান চুলকায় আমার। মুখোশের ওপর দিয়ে কান খোঁচাখুঁচি করার কারণে বন্দুকের নলটা উপর-নিচ করছিল, তাদের অস্থিরতার কারণ ছিল সেটাই। শটগানের সেফটি ক্যাচ যেহেতু খোলা, দুর্ঘটনাক্রমে গুলি ছুটে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাদের অবশ্য সেটি জানার কথা নয়, আমারও দায় পড়েনি আগ বাড়িয়ে বলার।
হ্যামবার্গার বানানো শেষ হলে গুনে গুনে সেগুলোকে ছোটো দুটো থলেতে ভরল বউ। একেক ব্যাগে পনেরটি করে।
‘এটা কেন করছ?’ দোকানের মেয়েটা জিজ্ঞেস করল আমাকে। ‘টাকাটা নিয়ে এরকম কিছু কিনে নিলেই তো হতো। ত্রিশটা বিগ ম্যাক খেয়ে কী লাভ?’
মাথা নাড়লাম আমি।
‘আসলেই দুঃখিত। তবে কিনা, রুটির কোনো দোকান খোলা নেই। থাকলে রুটির দোকানেই হানা দিতাম,’ ব্যাখ্যা দিল আমার বউ।
মনে হলো উত্তরটা সন্তুষ্ট করেছে তাদের। আর কোনো প্রশ্ন করল না অন্তত। মেয়েটাকে দুটো বড়ো কোক দিতে বলল বউ, পয়সা মিটিয়ে দিল সেগুলোর। ‘কেবল রুটি চুরি করছি আমরা, আর কিছু না,’ বলল সে। মাথার জটিল একটা ভঙ্গি করে জবাব দিল মেয়েটা। কিছুটা মাথা দোলানো আর কিছুটা ঝাঁকানোর মতো দেখাল। হতে পারে দুটোই একসঙ্গে করার চেষ্টা করেছিল। তার কেমন লাগছে খানিকটা বুঝতে পারছিলাম।
পকেট থেকে পাকানো দড়ির একটা বল বের করল বউ, দরকারি সবকিছুই নিয়ে এসেছে। একটা খুঁটির সঙ্গে এমন দারুণভাবে বাঁধল তিনজনকে যেন বোতাম সেলাই করছে। দড়ির কারণে ব্যথা লাগছে কি না বা কেউ টয়লেটে যেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করল, মুখে কুলুপ এঁটে রইল তিনজনই। বন্দুকটাকে ফের কম্বলে মুড়লাম, থলেগুলো তুলে নিল বউ, বেরিয়ে এলাম দুজন। দুই ক্রেতা তখনও ঘুমিয়ে, যেন গভীর সমুদ্রের দুই মাছ। কী ঘটলে এমন মরণঘুম থেকে তারা জাগবে কে জানে।
আধঘণ্টার মতো গাড়ি চালালাম, একটা ভবনের ধারে পার্কিং করার ফাঁকা একটু জায়গা দেখে থামালাম। হ্যামবার্গার আর কোক খেলাম সেখানে বসেই। মোট ছ’টা বিগ ম্যাক পাঠালাম পেটের গহ্বরে, বউ খেল চারটা। গাড়ির পেছনের আসনে রয়ে গেল বিশটা। আমাদের ক্ষুধা, যেটি অনন্তকাল ধরে চলবে বলে মনে হয়েছিল, ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সূর্যের প্রথম আলো ভবনের নোংরা দেয়ালকে রাঙাচ্ছিল বেগুনি রঙে, ‘সনি বেটা’-র বিশাল এক বিজ্ঞাপনি টাওয়ার জ্বলজ্বল করছিল বেদনার প্রখরতায়। মহাসড়কের ট্রাকগুলোর টায়ারের ক্যাঁচক্যাচানির সঙ্গে যোগ হচ্ছিল পাখির কিচিরমিচির। মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর রেডিওতে কাউবয়দের গান বাজছিল। ভাগাভাগি করে সিগারেট খেলাম একটা। আমার কাঁধে মাথা রাখল সে।
‘আসলেই কি দরকার ছিল এটা করার?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।
‘অবশ্যই দরকার ছিল!’ লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মুরগির ছানার মতো নরম আর হালকা মনে হলো তাকে।
যেহেতু একা, নিজের নৌকার কানায় ঝুঁকে সমুদ্রতলের দিকে তাকালাম। আগ্নেয়গিরিটা নেই। পানির শান্ত বুকে প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে আকাশের নীলের। হালকা বাতাসে দোলা রেশমি পাজামার মতো ছোটো ছোটো সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে নৌকার গায়ে। কিছু নেই আর কোথাও।
নৌকার পাটাতনে শরীরটা লম্বা করে দিয়ে চোখ বুঁজলাম, অপেক্ষায় থাকলাম ভরা জোয়ার কখন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে, যেখানে আমার থাকার কথা।

জন্ম ফেনীতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বর্তমানে একই বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। লেখালেখির শুরু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, পত্রপত্রিকায়। গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি ইতিহাস, তথ্যপ্রযুক্তি, ছোটোদের জন্য রূপকথা নানা বিষয়ে লিখেছেন। বিশেষ আগ্রহ অনুবাদে। সিলভিয়া প্লাথের ‘দি বেল জার’ ছাড়াও ইতিহাসভিত্তিক কয়েকটি বই অনুবাদ করেছেন। মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বাইশ।